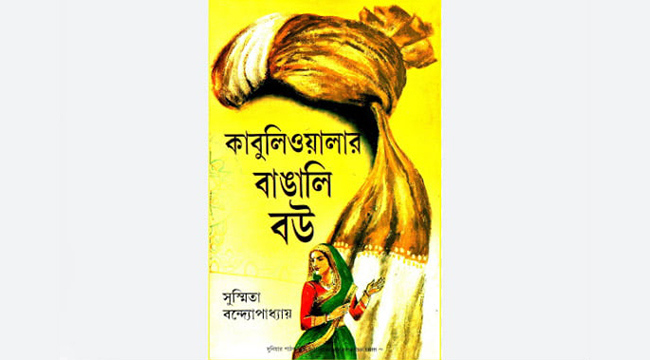প্রথম অধ্যায়
অন্য সব দিনের চেয়ে আজ যেন শীতটা একটু বেশিই। রাত কত কে জানে। অন্ধকারে দেওয়াল ঘড়িটা দেখাই যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি রাতটা শেষ হলে যেন বাঁচা যায়। জানালা ভিতর থেকে মোটা কাগজ দেওয়া। বাইরের দিক থেকেও প্লাস্টিক দিয়ে পুরো জানালাটা ঢাকা। ঘরের দরজায় মোটা কম্বল ঝোলানো। এত কিছু সত্ত্বেও একটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া কোথা থেকে যে আসছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। মোটা একটা লেপ গায়ে দিয়েছি। তার ওপর ভেড়ার লোমের গরম কথা চাপিয়েছি। তবুও শীত আজ চেপে ধরেছে। যত ঠাণ্ডাই লাগুক, মাঝরাতে তো আর উঠে বসে থাকা যায় না! তাই আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছি। বাইরে বরফ জমেছে। গতকাল থেকে টানা তুষারপাত। কখনো থামছে, আবার কখনো ঝিরঝিরে বৃষ্টির মতো তুষার পড়ছে।
ছবছর হয়ে গেল, আমি আফগানিস্তানে। এখানে আমার শ্বশুরবাড়ি। দেশে ফেরার ইচ্ছেটাকে মনের ভেতর দমিয়ে রেখে পড়ে আছি এই অচেনা, রুক্ষ পাহাড়ি দেশে। কারণ এরা আমাকে বন্দী করেছে। তবে, বন্দী করার যে আভিধানিক অর্থ, ঠিক সেই অর্থে এখানে কাউকে বন্দী করার দরকারই হয় না। এদেশে মহিলারা একা এক পা-ও, যেতে পারে না। সব জায়গাতেই তালিবান প্রহরীদের কড়া নজর। তাছাড়া, গাড়ি পাবো কোথায়? আর কাবুলে সব অ্যামব্যাসিই তত বন্ধ। কিংবা যদি খোলাও থাকে যুদ্ধের তাণ্ডব থেকে বেঁচে বর্তে অ্যামব্যাসি পর্যন্ত পৌঁছানো, আর দুর্গম হিমালয় পেরনো-দুটো একই ব্যাপার। সত্যি কথা বলতে কি, কোনও মহিলা চেষ্টা করলে হয়ত হিমালয়ও পেরোতে পারবে; কিন্তু এই দেশে কোনও মহিলার পক্ষে বাড়ির চৌকাঠ পেরোনও অসম্ভব।
কাবুল শহর থেকে আমার শ্বশুরবাড়ি, পুরো আঠারো ঘণ্টার রাস্তা। ১৯৮৮ এর জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে, আমি আমার স্বামী জাম্বাজ খানের সঙ্গে কলকাতা থেকে কাবুলের মাটিতে প্রথম পা রাখি। শ্বশুরবাড়ির সকলকে দেখার প্রবল ইচ্ছেই আমাকে বাধ্য করেছিল পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটাতে আসতে-যেখানে মধ্যযুগীয় গোঁড়ামির অন্ধকার এখনও ঘোচেনি। তখন তো জানতাম না যে, এটা এমনই একটা দেশ, যে দেশে ঢোকার রাস্তা আছে, কিন্তু বেরোবার পথ নেই। আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন গোটা কাবুল শহর জুড়ে সদর্পে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে রাশিয়ার সৈন্য। আর শুনেছি সেই সময়, আঠারো থেকে আটত্রিশ বছর বয়সের দাড়িওয়ালা কোনও অচেনা যুবকই নাকি গ্রাম থেকে শহরে যেতে পারত না। কারণ, রাশিয়ানরা তাদের ধরে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দিত। পরে, সময় বুঝে তাদের সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করত। ইচ্ছেয় হোক বা অনিচ্ছেয় হোক, সোভিয়েত সৈন্যদলে তাদের যোগ দিতেই হবে। তা না হলে তাদের দাঁড়াতে হত ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। অন্যদিকে সোভিয়েত বাহিনীতে যোগ দেওয়ার ফলে তাদের গ্রামে, নিজেদের বাড়ি ফেরার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যেত। আর গ্রামে আছে মুজাহিদরা ১৯৭৯ থেকে সোভিয়েত সেনাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চলেছে। মুজাহিদরা সোভিয়েত সরকারকে ও তাদের হাতের পুতুল ডঃ নাজিবুল্লাকে দেশের চরম শত্রু বলে ভাবে। তাই ওরা সবাই খালকি অর্থাৎ দেশদ্রোহী। নাজিব নাকি দেশের মন্ত্রীর আসনে বসে দেশকে সোভিয়েতের কাছে তুলে দিচ্ছে। তাই নাজিব পন্থীরা দেশের শত্রু। অন্যদিকে, মুজাহিদরা দেশে ইসলামি শাসন কায়েম করতে চাইছে। তাই মুজাহিদ ভক্তরা হল দেশভক্ত।
যে সময় কাবুল শহরে লোকে যেতে ভয় পেত, ঠিক সেই সময় আমি জাম্বাজের হাত ধরে এ দেশের একেবারে ভিতরে পৌঁছে গেছি। আশ্চর্যের কথা বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরোর মতো মুসাফিররা সে সময় শহরে অবাধে চলাফেরা করতে পারত। জাম্বাজের এক কাকা নাজিবপন্থী খালকি ছিলেন। তিনি কাবুলেই তার পরিবার নিয়ে বাস করতেন। এই কাকা খোদ নাজিবের একেবারে কাছের লোক। তাই নাজিব সরকারের ট্রেডমার্ক স্টার লাগানো একটা গাড়ি সব সময়ই কাকার কাছে থাকত। কাবুলে এসে এই কাকার বাড়িতেই, আমি প্রথম রাত কাটিয়েছি।
একে আমি সম্পূর্ণ নতুন। তার উপর সর্বত্র বিপদ উঁকি মারছে। দেশের ভেতরে যে এত জটিল ব্যাপার তার কিছুই আমি আগে আঁচ করতে পারিনি। এখানে এসে সব জেনেছি। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা যে আমাকে করতে হবে তা কি আমি কোনদিন ভাবতে পেরেছিলাম? যখন সব জানতে পারলাম তখন আমার সমস্ত শরীরটা যেন থরথর করে কাঁপতে লাগল। মনে হল, পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। চোখে সব কিছু অন্ধকার দেখতে লাগলাম। জীবনে প্রথম, এই প্রথম ভয়ে, বিস্ময়ে আতঙ্কে আমি নির্বাক। কিন্তু একটু পরেই যেন শত সমুদ্রের অসংখ্য ঢেউ এসে আমার মনকে, শরীরকে নাড়া দিয়ে যেতে লাগল, কারণ আমি যখন শুনলাম শহর ছেড়ে গেলেই, যুদ্ধের রেশ আর থাকবে না। যুদ্ধের ভয়াবহতা মন থেকে যাওয়ার পর আর একটা অচেনা ভাবনা মনের কোণে এসে, আমাকে সজাগ করে দিয়ে চুপিচুপি, কানে কানে বলল–সুমি, এবার আর এক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে তৈরি হও। তুমি কি একবারও ভেবেছো যে তুমি সম্পূর্ণ ভিনদেশি, তায় বাঙালি হিন্দু নারী। তোমাকে কেমন ভাবে গ্রহণ করবে তারা? আর, তুমিই বা কেমন ভাবে স্বীকার করবে তাদের? যাদের দেখার অদম্য ইচ্ছায় তুমি এখানে এসেছো?
আশ্চর্য। কয়েক হাজার মাইল দূরে দাঁড়িয়ে এখন আমি যে কথাটা চিন্তা করছি আগে তো তা ভাবিনি। অথচ সবচাইতে জরুরি চিন্তা তো এটাই ছিল। আসলে, অঘটনের বিষয় ভাবতে ভাবতে একটা দুর্ঘটনার বৃত্তের মধ্যেই আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। তাই এই স্বাভাবিক চিন্তাটা মনের কোণে স্থান করে নিতে পারিনি। মনে মনে ভাবলাম যা এতক্ষণ করিনি তা এখন করার কোনও মানেই হয় না।
আমরা ভোর পাঁচটায় রওনা দিয়েছি জাম্বাজের কাকার বাড়ি থেকে। ওর কাকাই একটা গাড়ি ঠিক করে দিয়েছিলেন। গাড়ির ড্রাইভার রাশিয়ান। গজনি শহরে সে আমাদের পৌঁছে দেবে। সেখান থেকে অন্য গাড়ি নিতে হবে। রাশিয়ানরা গজনির বেশি যেতে পারে না। কারণ গজনি থেকে শুরু হয়ে যায় মুজাহিদদের এলাকা। গাড়ি আমাদের নিয়ে ছুটে চলল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া জানলার ফাঁক দিয়ে এসে গায়ে লাগল। বাইরের দিকে চোখ মেলে দেখলাম সুন্দর চওড়া রাস্তা। রাস্তার দুধারে সারি সারি দোকান। সেগুলি এখন বন্ধ। রাশিয়ান সৈন্যরা বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম কাবুলের সৌন্দর্য, আর সেই সঙ্গে রাশিয়ান লালমুখো সৈন্যদের।
লম্বা কোট পরা সোভিয়েত সৈন্যরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে সবাইকে খুঁটিয়ে দেখছে। কয়েক মিনিট পরে, দুজন সৈনিক খটাস্ করে বন্দুক ঘাড়ে তুলল। তারপর বুটের গর্জন তুলে তালে তালে কদম ফেলে স্তব্ধ শহরে অদৃশ্য হল। এই সময় কাছাকাছি এক ঝাক গুলির শব্দ। শুরু হল ছোটাছুটি। রাস্তায় যে কজন মানুষ ছিল তারা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে লাগল। প্রচণ্ড হৈ-চৈ। দলে দলে সৈন্য ছুটে এসে বন্দুক উঁচিয়ে চিৎকার করে ধমকাতে লাগল। একটা ট্যাঙ্ক বিকট ঘড়ঘড়ে আওয়াজ তুলে এগিয়ে আসছে দেখে আমাদের ড্রাইভার স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে অন্য রাস্তা ধরল এবং ওদের ভাষাতে জাম্বাজকে কী যেন বলল। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম ড্রাইভার কী বলল? জাম্বাজ আমাকে জানাল যে ড্রাইভার বলছে শিগগিরই কামান চলবে। রকেট চলবে। গুলি চলবে। তাই ও রাস্তা বদলাল। কারণ আমরা যেদিকে মোড় নিয়েছি সেদিকটা এখন শান্ত। জাম্বাজের কথা শুনে ভয়ে আমার হাত পা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।
দিনের আলোয় ঝকঝক করছে শহর। যুদ্ধের পরোয়ানা না থাকলে, শহরটা আরো ভাল লাগত। হঠাৎ একদল সৈন্য আমাদের গাড়ির সামনে রাস্তা আটকে দাঁড়াল। গাড়ির পাশ দিয়ে একটা মিলিটারি ট্যাঙ্ক কর্কশ আওয়াজ করে বেরিয়ে গেলো। আমাদের ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে সৈন্যদের সামনে গিয়ে কী যেন বলল। তখন ওরা আমাদের ছাড়পত্র দেখাতে বলল। জাম্বাজ তাড়াতাড়ি একটা কাগজ বার করে সৈন্যদের হাতে দিল। সৈন্যরা ধীরে ধীরে বানান করে কাগজটা পড়ল। তারপর আমাদের আপাদমস্তক দেখল। এবং দেখার পর ছেড়ে দিল। গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। একটু দূরে যাওয়ার পর নজরে পড়ল ডানদিকে রাস্তার ধারে চার পাঁচটা ট্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে; খবর পেলেই স্টার্ট দেবে। একটা বেপরোয়া। আবহাওয়া চারিদিকে। তার সঙ্গে মৃত্যুর হাতছানি। এখন আমরা শহর ছেড়ে অনেক ভেতরে ঢুকে পড়েছি। এইবার রাস্তা মাঝে মাঝে ভাঙা, এবড়ো-খেবড়ো। সৈন্যদের চোখ-রাঙানি আর তর্জন গর্জন পেছনে ফেলে রেখে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। চোখে পড়ছে রাস্তার দুধারে অনেকটা ব্যবধানে একটা করে গাছ। আরও খানিকটা যাবার পর গাড়ি পাহাড়ি রাস্তা ধরল কখনো সোজা, কখনো আঁকাবাঁকা, কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। মাঝে মাঝে দু-একটা বাড়িও চোখে পড়ছে। অবশ্য, বলে না দিলে বুঝতেই পারতাম না ওগুলো বাড়ি। চারদিকে বিশাল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। উঁচুতে তিনতলা বাড়ির সমান। চওড়াটা দূর থেকে ঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না। ওর মাঝখানে যে ঘর আছে আর তাতে যে মানুষ বসবাস করে তা আমি বিশ্বাসও করতে পারছিলাম না। আমরা যখন গজনি শহরে পৌঁছলাম ঘড়ির কাঁটায় তখন বেলা বারোটা।
.
সাহেব-কামাল, সাহেব কামাল, ওঠো। সকাল হয়েছে। আচমকা ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শোওয়ার ফলে কখন যে সকাল হয়েছে বুঝতেও পারিনি। এখানে আসার পর জাজের এক কাকা আমার নতুন নামকরণ করেছেন-সাহেবকামাল। এই নামের অর্থ আমি জানি না। তবে আন্দাজে বলতে পারি সাহেব কা মাল–অর্থাৎ সাহেবের মাল গোছের আর কি। এখানে সবাই আমাকে এই নামেই ডাকে, আমার সত্যিকারের নামটাও আজ অতীতের অ্যালবামে। ছবছরের অতীত। সেদিনের কথা বড্ড মনে পড়ে। কলকাতার জনস্রোতে গা ভাসিয়ে পথ চলা, কার্জন পার্কে ফুচকা খাওয়া, বর্ষায় শরীর ভিজিয়ে ঝোড়ো কাক হয়ে বাড়ি ফেরা, মনখারাপ করা বিকেলে কিংবা উদাসী দুপুরে স্বপ্নের জাল বোনা, পার্ক স্ট্রিটে কিংবা গ্র্যান্ডের আর্কেডে শপিং করা–এই রকম অজস্র স্মৃতির টুকরো মনের মধ্যে উথাল-পাথাল করে।
নানান অনুভূতিতে ভরা কয়েক বছর আগের ফেলে আসা দিনগুলি থেকে এবার আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম আমার তিন দেওর বরফ পরিষ্কার করছে। শুরু হয়েছে নিত্যদিনের মতো আরও একটি আফগানি দিন। সেই একঘেয়ে জীবন। কোনও বৈচিত্র্য নেই এখানকার দৈনন্দিন জীবনধারায়। তবুও চলছি, চলতে হচ্ছে। জীবনধারণের জন্য খেতে হচ্ছে, কথাবার্তা বলতে হচ্ছে, নইলে সময় কাটাবো কী। করে?
আফগানিস্তানে পুরো তিন তিনটে বছর কেটে গেল। জাম্বাজ হিন্দুস্থানে গিয়েছে আসাম চাচার সঙ্গে। নরমে গরমে ঝগড়ায় ভালবাসায় ভালই কাটছিল। সব বেদনা, যন্ত্রণা ভুলেছিলাম জাম্বাজের মুখ চেয়ে। কিন্তু জাম্বাজের সঙ্গসুখের সৌভাগ্যটুকুও আমার কপালে বেশিদিন সইল না। একদিন ওর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। মাঝ রাতে হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। এর আগেও অনেক রাত গিয়েছে জাম্বাজ সারা রাত বাড়িতে ফেরেনি। কিন্তু আমার মন এত চঞ্চল হয়নি। মনে হল আজও সে বোধহয় রাতে বাড়িতে আসবে না। সকালে এসে এক মুখ হাসি নিয়ে আমার সামনে কপট ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াবে। কৈফিয়ত দেবে রাতে না ফেরার জন্যে। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠতে লাগলো। ওর বাড়িতে না ফিরে আসাটা কেন জানি
আমার মনে একটা ভয়ের সংকেত দিচ্ছে। আসাম চাচাও তো বাড়িতে নেই। আমার এই একটা দোষ আসামকে আমি কখনো কাকা বলি তো কখনো চাচা বলি। গতকাল তার দুই বিবি ও অন্যান্য সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হিন্দুস্থানের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে জাম্বাজের এইভাবে রাতে বাড়ি না ফেরাটা, আমার যেন স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। গতকাল রাতে বিছানায় ওর ব্যবহারটা অন্যান্য দিনের মতো ছিল না। এই কথাটা সারাদিন আমার মনে পড়েনি তো! তাছাড়া এই কথা মনে না পড়বারই তো কথা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রাতের অন্ধকারে বিছানার নির্জনতায় অনেক বাস্তব ও অবাস্তব ঘটনাই ঘটে, যা সকালের কর্মব্যস্ততায় কেউই বিশেষ করে মনে রাখে না। কিন্তু এখন আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে, রাতে ওর ভালবাসার রংটা একটু অস্বাভাবিক ছিল, রোজকার মতো ছিল না। যেন ও আমার থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। হয়তো বা কোনদিন আর মিলন হবে না, নতুবা বহুদিন বাদে মিলন হবে। চাপা একটা বেদনা যেন ওর ব্যবহারে ছিল বলেই আমার মনে হচ্ছে এখন। কিন্তু কী সেই বেদনা? তবে কি সে আমাকে এখানে রেখে হিন্দুস্থানে চলে গেল? কিন্তু তাও কি কখনো সম্ভব? সে যে আমাকে ভালবাসে। আমি তার স্ত্রী। কোনও স্বামীই স্ত্রীকে মিথ্যে বলে না। স্বামীর গোপন যত কিছু আছে তা আর কেউ না জানলেও স্ত্রী জানবেই। নানা। এমন অমানবিক নিষ্ঠুরের মতো কাজ জাম্বাজ কিছুতেই করবে না। সে আমাকে প্রাণাধিক ভালবাসে। কোনও মুজাহিদ ওকে গুলি করে দেইনি তো ভুলবশত? হ্যারিকেনের আলোটা টিমটিম করে জ্বলছে। সমস্ত ঘরটায় আলো আঁধারির এক বৈচিত্র্যময় বাহারি খেলা। মনে মনে ভাবলাম কাল সকালে জাম্বাজ বাড়ি এলে একটু কড়াভাবে বলতে হবে আর যেন এভাবে আমাকে না জানিয়ে রাতে কোথাও না থাকে। এতে আমার কষ্ট, আবোল তাবোল চিন্তা হয়। এ কি অসভ্যতা? রাতে বাড়ির বাইরে থাকা? রাগের মধ্যেই এপাশ থেকে ওপাশ ফিরে শুলাম।
পরদিন বেলা প্রায় বারোটা। জাম্বাজের দেখা নেই। মন দিয়ে রুগী দেখতেও পারছি না। এমন দেরি তো ও কোনদিন করে না! এই তো সেদিন আমাকে না বলে ওর পিসির বাড়িতে গিয়েছিল। রাতে বাড়ি ফেরেনি, কিন্তু ভোরে বাড়িতে এসে হাজির। সব কিছু বোধহয় ঠিক আছে কিন্তু তবুও আমার মন অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠছে বার বার। কেবলই থেকে থেকে মনে হচ্ছে জাম্বাজ যেন অনেক দূরে কোথাও চলে গেছে। আমার ডাক সে আর শুনতে পাচ্ছে না। বাড়ির পরিবেশটাও যেন কেমন কেমন। একটা যেন বেপরোয়া ভাব সবার মধ্যেই লক্ষ করছি। কেবল গুলগুটি ছাড়া। গুলগুটির চোখ দুটো লাল। যেন অনেক কেঁদেছে সে। যদিও প্রায়ই ও কাঁদে ওর ভাগ্যের পরিণতির জন্য। দেওররা অন্যদিনের মতো শান্ত নয়। একটু বেশিই সাহসী মনে হচ্ছে। সাদগি অন্যদিন বাড়ির দাওয়ায় পা মেলে বসে না। আজ দাওয়ায় পা মেলে বসে কিসমিস দিয়ে চা খাচ্ছে আর বেশ জোরে জোরে স্বামী কালাখানের সঙ্গে কথা বলছে। যা একেবারেই সম্ভব নয়। কারণ জাম্বাজের উপস্থিতিতে কেউ এই ভাবে তার বৌয়ের সঙ্গে বসে কথা বলবে না। একটা বাজে। উদ্বিগ্ন নয়নে বাড়ির বড় দরজার সামনে একটা থামের ওপর বসে আছি। হঠাৎ দেখলাম, আসাম চাচার দুই বিবি, আর আবু ও সেরিনা চাচি, আদ্রামান ভাইয়ার বিবি, সবাই আমাদের বাড়ির দিকে আসছে। মনটা চমকে উঠল। শেষ, আমার সব শেষ হয়ে গেল। নেই, জাম্বাজ আর কোনখানেই নেই। আমি চিৎকার করেও আর তাকে ফিরে পাবো না। আমি উঠে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগলাম। কান্নায় ভেঙে পড়লাম। একটু পরেই জাম্বাজের দেহটা হয়তো আমার বাড়ির উঠোনে এনে হাজির করবে। শেষ হয়ে গেল সব। আমি উন্মাদের মতো গিয়ে আবুকে জড়িয়ে ধরলাম। আগত সবাই আমার মাথায় হাত রাখল। আমি কাঁদতে কাঁদতেই বললাম–কে? কে করল এমন কাজ? আমার প্রাণ থাকতে আমি তাকে ছাড়বো না। তার বংশের কেউ বাঁচবে না। আমি সবাইকে হত্যা করব। হঠাৎ আসাম চাচার বড় বৌ বলল –সেয়িদা, জেবুম গোরম। অর্থাৎ আমিও দেখব যে তুমি কী কর? আমি পাবলু চাচির কথা শুনে রাগে, দুঃখে সজোরে এক ঘুষি মারলাম তার মুখে। পাবলুচাচি উই, উই আওয়াজ করে মাটিতে বসে পড়ল।
আবু তখন আমাকে ধরে মাটিতেই বসিয়ে, বলল—দাগাসায়কে?–এটা কি? দেতা অইলি বিনা কে? মানে ওকে কেন মারছে? তা মেরো আপলে উরাল। অর্থাৎ তোমার স্বামী নিজেই চলে গেছে।
কতক্ষণ সময় যে অতিবাহিত হয়েছে জানি না। অবসন্ন শরীরে টলতে টলতে নিজের ঘরে চলে এলাম। কান্না অনেকক্ষণ থেমে গিয়েছে। বিলাপ আর নেই। শুধু একটা কিছু থেমে গেছে বলে মনে হচ্ছে। দিনের আলোকে পরাস্ত করে রাতের অন্ধকার পৃথিবীতে ছেয়ে যাচ্ছে। একটা শুষ্ক মরুর হাওয়া শন্ শন্ বয়ে চলেছে। পাতকুয়ার সামনে গরুগুলো একটানা হাম্বা হাম্বা চিৎকার করছে। মুরগিগুলো ডানার ঝাঁপট দিতে দিতে ওদের গন্তব্যে চলেছে। একটা মুরগিকে অন্য একটা মোরগ তাড়া করেছে ঠিক তখন বড় একটা মোরগ কেশর তুলে বেগে ধেয়ে এসে অন্য মোরগটাকে সরিয়ে দিল। আমি ঘরের জানালার সামনে বসে শূন্য দৃষ্টিতে দেখছি। চোখের পলক যেন পড়তে ভুলে গেছে। বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না। নিজের মাথার দোপাট্টা দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে শুয়ে পরলাম। যারা এসেছিল আমাকে একটু উপদেশ দিয়ে চলে গেল। আমিও বুঝে নিলাম যে মৃত্যু নয় মুজাহিদদের গুলি নয়। সে পালিয়েছে। সে জীবিত। সুতরাং দেখা তার সঙ্গে একদিন হবেই। মিথ্যে মিথ্যে, সব মিথ্যে। সমস্ত ভালবাসা মিথ্যে। সব প্রতিশ্রুতিই মিথ্যে। আমি তো বেশ ছিলাম। কোনও পুরুষকেই জীবনসঙ্গী করব না বলেই তো প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। তবে কেন করলাম বিয়ে? আর বিয়ে করলামই যখন তখন নিজের দেশের ছেলেকে কেন করলাম না? কে যেন আমার নিজের মনের ভেতর থেকেই বলে উঠল-এর জন্যে দায়ী তুমি নিজে।
-না না, এই পরিণতির জন্যে দায়ী রুমা। নিজেকেই কৈফিয়ত দিতে চাইলাম আমি। আবার মন প্রশ্ন করল তুমি সত্যি করে বলো তো, তোমার এই পরিণতির জন্যে রুমাই কি দায়ী?
-হ্যাঁ, রুমাই তো দায়ী। ওই তো জাম্বাজের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিয়েছিল।
-মিথ্যে কথা। রুমা পরিচয় করে দিয়েছিলো, কিন্তু বিয়ে করতে বলেনি।
-আসলে জাম্বাজের মধ্যে আমি একটা প্রকৃত পুরুষকে দেখতে পেয়েছিলাম। তাই আস্তে আস্তে ওকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম। আবার মনকে কৈফিয়ত দিলাম।
–তবে আজ রুমাকে দায়ী করছ কেন? আর তাছাড়া এই কি তোমার প্রকৃত মানুষ? সৌরভকে মনে পরে? তাকে কি তুমি ফেরাতে পারতে না? না, তুমি তাকে ফেরাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করনি। সুতরাং তুমি মরো।
জাম্বাজ চলে গেছে। অনেক চিন্তা করেও ওকে আর আমার মনে পড়ে না।
ঠিক মনে পড়ে না এ কথা বলতে পারব না। পড়ে, আবার ঘেন্নার আচ্ছাদন দিয়ে সব ভালমন্দ ভালবাসা ঢেকে ফেলি। মনের কোনও খানেই আর উত্তাল তরঙ্গের ঢেউ নেই। কেবল বালির ওপর আছড়ে পরা ঢেউ। ক্লান্ত, অবসন্ন মন। একটা হিংসা আমার মনে অপ্রত্যক্ষ জায়গা করে নেয়। কাউকে যখন দেখি সে তার স্বামীর সঙ্গে বসে আছে, তখন আমার মনের ভিতরটা সপ্ততন্ত্রীর বীণার ঝঙ্কারের মতো বেজে ওঠে। ভাবি ও কত সুখী। স্বামী ওর সঙ্গেই আছে। আমার নেই। একটা কষ্ট তখন আমার বুকের ভেতরটা একেবারে ঝাঁঝরা করে দেয়। এমনকি পশুপাখির ক্ষেত্রেও আমার একই হিংসা বা ওই প্রকার বীণা ঝংকৃত হতে থাকে। সবই আছে, অথচ কিছুই নেই। আমি আছি। আমার কেউ নেই। হৃদয় আছে তবে তা উদ্দীপ্ত হয় না। চাওয়া আছে, পাওয়া নেই। উন্মাদনা অনেক কিন্তু তা প্রশমিত হয় না। আমি আছি। আমার কেউ নেই। আমি এক হারিয়ে যাওয়া নারী। কেবল দুচোখ ভরে নীড়ের স্বপ্ন আঁকি। কোথায় ছিলাম, আজ কোথায় এলাম। কী চেয়ে হায় কী যে পেলাম। স্বপ্ন দিল শুধুই ফাঁকি।
এও কি বাস্তব? কিন্তু এই অসম্ভব বাস্তব আমার জীবনে ঘটল। জাম্বাজ আজ তিন বছর হল হিন্দুস্থানে চলে গিয়েছে। এখানে সে মাত্র দুবছর সাত মাস আমার সঙ্গে কাটিয়েছে। অনেক সুখ আর অবিশ্রান্ত ভালবাসার স্রোতে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। যা কোনোদিন কোনো পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো না। দুর্লভ। দুষ্প্রাপ্য সব স্মৃতি আমাকে দিক থেকে দিগন্তরে কেবলই ছুটে যেতে বাধ্য করে। আজ তিনবছর ধরে ছুটতে ছুটতে আমি ক্লান্ত। অবসন্ন। ভালবাসা আজ পশ্চিমাঞ্চল। আমার জীবনে যখন যা কিছু ঘটেছে তা অতি অপ্রতাশিত ভাবেই ঘটেছে। আর আমি বিক্ষিপ্ত, বিকীর্ণ, উন্মুক্ত হয়ে লোকসংসর্গে অনুচিত কর্ম ভুলে গিয়েছি। সংকীর্ণ চিত্তের মানুষের কাছে উপহাস্যতার খোরাক হয়ে বিচরণ করেছি। জাম্বাজ চলে যাওয়ার পর শুরু হয়েছে আমার প্রতি ওর ভাইদের অত্যাচার। অনাহার, অনিদ্রা, আর সেই সঙ্গে আছে মারধোর। বলেও তো কোনো লাভ নেই, এরা অমানুষদের দলেই পরে। বর্তমানে আমি এখানে অলিখিত বন্দী। কারণ দেশটাই একটা কয়েদখানা।
জীবনের শুরুতে আদৌ ভাবিনি যে একটা অমোঘ দুর্যোগ এবং অধঃপতনের মতো বীভৎস ভয়ঙ্কর অন্ধকার আমাকে সুস্থ জীবনের থেকে এইভাবে তাড়া করে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আর হয়তো কোনোদিন আমি নতুন দিগন্তের নব আলোয় উদ্ভাসিত হব না। জাম্বাজের কথা ভর্তি ক্যাসেট, এখন আমার নতুন দিগন্তের নব আলো। দুতিন মাস বাদেই এখন ওর ক্যাসেট আসে। সেই ক্যাসেটে ও বলে, রাস্তা ঠিক হলে, যুদ্ধ থামলে তুমি আসবে। জাম্বাজ খুব ভালো করেই জানে যে, বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত খবর থেকে আমি বঞ্চিত। সুতরাং ওর কথা সহজেই বিশ্বাস করে নেব। এই ভাবেই প্রহসন-মাখানো ক্যাসেট বন্দী একগুচ্ছ কথাই হল আমার এই কয়েদী জীবনের সঙ্গী। বিয়ের আগে জাম্বাজকে ভালো করে জানার বোঝার সুযোগ বা সময় কোনোটাই ছিল না। সপ্তাহে একবার হয়তো আমরা দেখা করতাম। একটা বাঁধাধরা টাইমের মধ্যে। তিনটে থেকে চারটে। নিউ মার্কেটের ভেতরে ফুরিজের রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমরা বসতাম। এক কাপ কফি বা একটা পেস্ট্রি খেতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকুই ছিল দুজন দুজনকে বোঝার সময়। এইটুকু সময়ের পরিধির মধ্যে ও আমাকে কতটুকুই বা চিনতে পেরেছে? আর, আমিই বা ওকে কতটা জানতে পেরেছি। তবে আজ এসব প্রশ্ন তুলে যে কোনও লাভ নেই, সেটুকু অন্তত বুঝেছি।
দ্বিতীয় অধ্যায়
কম করেও একশ রুগীর স্লিপ জমা পরেছে। গাড়ির লাইন দেখে বুঝেছি যে, আজ আর তিনটের আগে কপালে খাওয়া জুটবে না। সমগ্র আফগানিস্তানে একটাও মেয়ে ডাক্তার নেই। দুএকজন যা আছে, তা ওই শহরে। তবে স্পেশালিস্ট কেউই নয়। যে দাঁত দেখে, সেই আবার ওভারিয়ান সিস্ট, অথবা এন্ডোমেট্রিওসিস এর চিকিৎসা করে। মেট্রোরেজিয়া এবং ডিমেনোরিয়ার একই রকম ওষুধ দেয়। যদিও আমি কোনও পাশ করা ডাক্তার নই, তবুও ডাঃ এস, এন পাণ্ডের প্র্যাকটিস অব মেডিসিন এবং, সি. এস দা-এর টেক্সট বুক অব গাইনোকলজি বই দুটো পড়ে যেটুকু শিখেছি, তাতেই অন্তত কিছু মেয়ের উপকার হয়েছে। আমার দেওয়া ওষুধ খেয়ে রুগী তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে দেখে, এখানে প্রায় সব গ্রামেই ভালো ডাক্তার হিসেবে আমার নাম ছড়িয়েছে।
সেদিন বেলা শেষের মুখে। সবে আমি সবকিছু গুছিয়ে রেখে চেম্বারের দরজা বন্ধ করতে যাবো, এমন সময় এক বয়স্কা মহিলা, আর তার সঙ্গে একটু কম বয়সী একজন মেয়ে এলো। ওই কম বয়সী মেয়েটি আমাকে অবাক করে দিয়ে পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল,-আমি আপনার সঙ্গে পস্তু বলব নাকি বাংলাতে কথা বলব?
তুমি বাংলা জানো? তুমি কি হিন্দুস্থান থেকে এসেছো?–আমিও তো বাঙালি। হিন্দুস্থান থেকে এসেছি। এই বাঙালি-বর্জিত দেশে, নিজের ভাষার ও দেশের একজনকে পেয়ে, কেন জানি না একটু বেশিই নিজেকে প্রকাশ করে ফেললাম।
-আমি জানি, আপনি বাঙালি। তাই তো দশ মাইল রাস্তা হেঁটে, বাড়িতে মিথ্যে বলে, আপনার কাছে এসেছি।
-কেন? আমার কাছে কেন? কোনও রোগে ভুগছো?
-না। আমার কোনও রোগ নেই। আমি শুনেছি যে কাবুলের রাস্তা ঠিক হলে, আপনি আবার নিজের দেশে ফিরে যাবেন। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।
এতক্ষণ আমি খেয়াল করিনি যে আমরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। এবার আমি ওদের দুজনকে ঘরের ভেতরে আসতে বললাম। চা খাবে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। ওরা খাবে না বলে মাথা নাড়ল। ওদের দুজনকে বসতে বলে আমি ওদের সামনে বসলাম। মেয়েটি বলল-আমার নাম কাকলি রায়। উত্তর কলকাতার সিঁথিতে আমার বাড়ি ছিল। আমি মেয়েটির কথাবার্তায় এতটাই মগ্ন হয়েছিলাম যে কত সময় হল ঠাহর করতে পারেনি। মেয়েটিকে কী বলব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।
ঘোমটা দেওয়া থাকলেও ওর মাথায় যে একরাশ ঘন কালো চুল আছে, তা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম। চোখ দুটো টানা টানা। টিকালো নাক। যদিও মুখে তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য নেই কিন্তু অজন্তার সামান্য তুলির টান নিশ্চয়ই আছে। মাইকেল এঞ্জেলো অথবা পাবলো পিকাসো তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে কাকলিকে সৃষ্টি করেননি। তবুও এক কথায় বলতে পারি যে, কোনও পুরুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত রূপের জোয়ার তার সর্বাঙ্গে। নেই যেটা, সেটা হল মেয়েদের আসল সৌন্দর্য ব্যক্তিত্ব।
সৌন্দর্য দর্শনের চর্চা শেষ করে এবার আমি বাস্তব জগতে ফিরে এলাম। মেয়েটিকে বললাম-বলল, তুমি কী আশা নিয়ে আমার কাছে এসেছো? আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?
-আপনি যখন কলকাতায় যাবেন, তখন যদি আমার বাড়ি সিঁথিতে গিয়ে, বাবাকে একটু অনুরোধ করেন যে, আমার স্বামীর ভাইকে যদি বাবা কোনরকমে পুলিসের হাতে তুলে দিতে পারে, তবে ওরা ভয় পেয়ে আমাকে আমার দেশে পাঠাতে বাধ্য হবে।
-কোথায় থাকে তোমার দেওর? আর কী করে তাকে পুলিসে হ্যান্ডওভার করবে?
–সিঁথিতেই থাকে। আমার বাবা চেনে। ওর নাম ইব্রাহিম খান। যেভাবে হোক ওকে ধরে পুলিসে দিতে বলবেন। বলবেন তো? বিশ্বাস করুন এই মানসিক যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না।
-কেন? তোমার স্বামী কি বাড়িতে নেই? আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রশ্নটা করলাম। হঠাৎ কাকলি কেঁদে ফেলল। তারপর বলল-ম্যাডাম, আপনার স্বামী দেবতুল্য। তাই অন্তত মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে হয়নি আপনাকে। উনি ঠকাননি আপনাকে।
আমি মনে মনে ভাবলাম ঠকায়নি? যন্ত্রণা দেয়নি?
কাকলি বলল- একটা মানুষ তার স্ত্রীর কাছে, মিথ্যের পথ ধরে এগোচ্ছে। দাম্পত্য জীবনের আগাগোড়াটাই তার মিথ্যে দিয়ে ভরা। এর থেকে যন্ত্রণা আর কী হতে পারে? বলতে বলতে হঠাই স্তব্ধ হয়ে গেল কাকলি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বলতে লাগলো–আমাদের বাড়ির রাস্তার বাঁদিকে ছিল নবাব খানের বাড়ি। জনা পাঁচেক পাঠান একই বাড়িতে থাকতো। নবাবকে দেখতে খুব সুন্দর ছিল। একটা মেয়ের মনের কোণে যখন কামনা, বাসনা জাগে তখন তার মনের মানুষটির সম্পর্কে কল্পনায় রং মিশিয়ে, বহুরকম অবাস্তব স্বপ্ন দেখে তাকে ঘিরে। যে সময় ভালবাসার কারেক্ট ডেফিনেশান সম্পর্কে মেয়েরা কিছুই জানে না, ঠিক এমনি একটা সময়ে আমি নবাবের সঙ্গে ভালবাসার স্রোতে ভেসে যেতে লাগলাম। সন্ধে হলেই কিসের একটা টানে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতাম।
কী যে সেই টান কিসের যে এত প্রবল আকর্ষণ, তা আমি বুঝে উঠতে পারতাম। এক সময়ে বাড়িতে জানাজানি হল। আমার বাবা ছিল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। বাবা, মাদাদা আমাকে অনেক বোঝালেন। পরে মারধর শুরু করলেন। কিন্তু কিছুতেই আমাকে বাগ মানাতে পারছিলেন না। আমি তখন নবাবের জন্য উন্মাদ। আমার মনের মানুষ নবাব। আমার চেতনার গভীরে তখন একমাত্র নবাব।
ইতিমধ্যে বাবা আমার বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। ছেলের বাড়ি দিল্লিতে। বাবার একমাত্র সন্তান। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। আমি তখন সবে ইংলিশে অনার্স গ্র্যাজুয়েট। যখন জানতে পারলাম যে, বাবা বিয়ের সব ব্যবস্থা করে
ফেলেছেন আমি তখন নবাবকে গিয়ে সব বললাম। নবাবই তখন আমার কাছে। সমগ্র পৃথিবীর একমাত্র বন্ধু। নবাব আমাকে বলল-কোনও চিন্তা করো না। আমি পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে তোমাকে নিয়ে আমার দেশে চলে যাবো।
আমি তখন আনন্দে বিভোর হয়ে গেলাম। আমার ভালবাসা সত্যিকারের সার্থকতার রূপ পাবে। নবাব সারা জীবনের জন্যে আমার একান্ত আমার হয়ে যাবে। পৃথিবীর কেউ আর নবাবকে পাবে না। নবাবের ভালোবাসার রাজ্যে আমি এক ও অদ্বিতীয় সম্রাজ্ঞী।
তারপর থেকে প্রায় এক সপ্তাহ আমি নবাবের দেখা পেলাম না। তখন আমার যে কী অবস্থা তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তবে কি সব মিথ্যে? সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন খালি হয়ে গিয়েছে। খাওয়া, ঘুম, বিদায় নিল। একটা অসম্ভব যন্ত্রণা
আমাকে দিনরাত কষ্ট দিতে লাগল। এমন একটা যন্ত্রণার মধ্যেই নবাব ফিরে এল।
নবাবকে যখন আমি না বলে কয়ে হঠাৎ উধাও হওয়ার জন্যে বকাবকি করছি তখন নবাব বলল যে, আমাকে নিয়ে ওর দেশে পালাবার সব ব্যবস্থা করতে গিয়েছিল। এরপর আমি নবাবের সঙ্গে ১৯৮৬-এর মার্চ মাসে এই দেশে চলে এসেছি। এই পর্যন্ত বলে কাকলি কাঁদতে লাগলো।
আমি বুঝতে পারলাম না, কাকলিকে ঠিক কী বলে সান্ত্বনা দেওয়া যায়। ভাবলাম, কিছু বলার চাইতে চুপ করে থাকাটাই বোধহয় ভালো। এসব ক্ষেত্রে কিছু কমেন্ট করা ঠিক নয়। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাতের অন্ধকার দিনের আলোকে গ্রাস করেছে। কাকলিদের ওঠার কোনও তাড়া না দেখে বুঝে নিলাম ওরা রাতে আমার মেহমান। সুতরাং খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই আমি ওদের বসতে বলে রান্নাঘরের দিকে চললাম। আমার মেজো জা তখন রান্নাঘরে রুটি করছে। এদেশে কেউ ভাত খায় না, রুটি খায়। ভাত পোশকি খাবার।
আমি জা সাগি-কে বললাম-মেহমান আছে দুজন।
ও বলল–আমি জানি। দুবার গিয়ে দেখে এসেছি। সন্ধের পরেও ওরা বসে আছে দেখেই বুঝেছি, যে ওরা রাতে থাকবে। তাই রান্নাও করেছি ওদের জন্যে।
-বাঃ! তোর বেশ বুদ্ধি আছে তো?– তা কী রান্না করেছিস?
–মাংসের কোরমা। আর দই আছে। হবে না?
–হবে, হবে। এর থেকে বেশি কিই বা করবি? আছেটাই বা কি?
–আকিইকে বলো তোমাদের ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে আসবে।
আমাদের এক খুড়তুতো জাকে সাগি আইি বলে ডাকে।
এদিকের কাজ সেরে আমি আবার, কাকলিদের কাছে গেলাম।
ওকে বললাম–কাকলি। তোমার জীবনের কাহিনী শুনে মনটা বেশ ভারী ভারী লাগছে।
-দিদি এখনো তো কিছুই শোনেননি। এই যে আমার সঙ্গে ইনি এসেছেন? ইনি সব জানেন।
–সত্যিই তো? এতক্ষণ আমরা নিজেরাই কথা বলে চলেছি। ওঁর কথা তো কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি। ও তোমার কে?
-ইনি, আমার ননদের বড় ননদ। আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। এঁর সঙ্গেপরামর্শ করে এঁর বাড়িতে যাওয়ার নাম করে, তবেই আপনার বাড়িতে আসতে পেরেছি।
-কাউকে বলে দেবেন না তো যে তুমি আমার কাছে এসেছে?
-না, তা বলবেন না। কারণ, আমি তো রাস্তাঘাট কিছুই চিনি না। উনিই তো আমাকে নিয়ে এসেছেন রাস্তা দেখিয়ে। বলে দিলে নিজেই তো ফেঁসে যাবেন।
-তারপর কী হল? তুমি তো নবাবকে বিয়ে করে এখানে চলে এলে? তারপর?
-তারপর? প্রথমেই আমরা চলে এলাম কাবুলে। কাবুলের অবস্থা তখন, আরো খারাপ। যুদ্ধ তখন চরমে। সবদিকেই মিসাইল আর রকেটের হানাহানি। সারা রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে কেবল মৃত মানুষের ছিন্ন-বিছিন্ন দেহ। তাদের তাজা রক্তে লাল হয়ে উঠেছিলো পথঘাট। তার মধ্যেই আমরা একটা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। প্রধান রাস্তা ধরে কেউ আসতে যেতে পারত না। তাই মেঠো পথের একটা রাস্তা ধরল গাড়ি। গাড়ির চাকার সঙ্গে মেঠো রাস্তার ধুলো উড়ে, আমাদের চোখ-মুখ ভর্তি হয়ে যেতে লাগল। রাস্তা যখন শেষ হল, তখন সন্ধে হয়েছে। তারপর আরো এক ঘণ্টার পথ পেরোনোর পর নবাবের বাড়ি এসে গেল। নবাবের বাড়ির লোকেরা একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল আমাকে। কিছু লোক আমার সামনে এসে বসে আমাকে দেখতে লাগল।
-তোমার গায়ে চিনি ছড়ায়নি? এখানে তো নতুন বৌ ঘরে এলে তার গায়ে চিনি ছড়াবার প্রথা? আকাশে বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে আনন্দ করার রেওয়াজ? আমার বেলায় তো তাই করেছে।
-না, আমার বেলা এসব কিছুই ওরা করেনি। অবশ্য তার কারণও আছে। রাত বারোটা নাগাদ নবাবের দাদা ঘরে এল। সঙ্গে এক মহিলা। বয়স প্রায় চল্লিশের কোঠায়। এতক্ষণ ঘরে যারা বসেছিল, তাদের সবাই এবার একে একে উঠে চলে গেল। শুধুনবাব, আমি, দাদা আর ওই মহিলা চুপ করে বসে রইলাম। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে ওই মহিলা চেঁচিয়ে উঠে, চোখ লাল করে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে একবার নবাবকে আর একবার দাদাকে কী যেন বলতে লাগল। নবাব হাত নেড়ে নেড়ে তাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি কিছু না বুঝে নবাবের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ভাবলাম উনি হয়তো নবাবের মা। আমাকে বিয়ে করেছে বলে নবাবকে বকছেন। সত্যিই তো। মায়ের হয়ত অনেক আশা ছিল ছেলেকে নিয়ে। ভালো বিয়ে দেবেন; নিজের হাতে বরণ করে ঘরে বউ আনবেন। তা তো আর হল না? তাই এত চিৎকার চেঁচামেচি।
আমি যখন এই সব ভাবছি, তখন দাদা হিন্দিতে বলল, শোন কালি। আমরা কেউ তৈরি ছিলাম না যে, নবাব এই ভাবে একটা ভিনদেশী মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনবে। কথাগুলো এমন ঘেন্নার সঙ্গে বলল যে, আমার খুব খারাপ লাগল। কেন, ভিনদেশী মেয়েরা কি মেয়ে নয়? দাদা সঙ্গের মহিলাটিকে দেখিয়ে আরও বলল-এই যে একে দেখছ? এর সঙ্গে তোমার পরিচয় হওয়া দরকার। কারণ সারা জীবন তোমাকে এর সাথেই ঘর করতে হবে। আমি মনে মনে ভাবলাম, সে তো করতেই হবে। পৃথিবীর সব বউ-ই তো শাশুরির সঙ্গে ঘর করে। আমাকেও তা করতে হবে। সেটা আবার নতুন করে বলার কী আছে?
এবার আমার চমকের পালা। দাদা আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, এ হচ্ছে নবাবের বিবি।
বিবি? নবাবের বিবি? ঘরের সব আলো মুহূর্তে নিভে গেল। আমার নিশ্বাসটাও যেন থেমে গেল। রক্ত চলাচলও বোধহয় বন্ধ হয়ে গেল। চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে এল। কী বলব আমি? ঠিক শুনলাম তত? ওই বিভীষিকাময় দাদা আমাকে চুপ থাকতে দেখে আবার বলল- কেন? নবাব তোমাকে বলেনি কিছু? প্রায় দশ বছর আগে নবাবের বিয়ে হয়েছে।
না, আর কোনও সংশয় রইল না। আমি ঠিকই শুনেছি। এই মহিলা সত্যিই নবাবের বিবি। তবে আমি কে? এখানে কী পরিচয় আমার? যাকে ভরসা করে ভালবেসে, দেশ ছেড়ে, সবাইকে ছেড়ে, হাজার হাজার মাইল দূরে এসেছি, সে আমার সঙ্গে কেন এত বড় ছলনা করল? আমার সরল সুন্দর বিশ্বাসের এত বড় অমর্যাদা করল?
দাদার কথার আমি কোনও উত্তর দিতে পারলাম না। নবাবের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। গলা বুজে এল। দুচোখ ঝাপসা হয়ে এল। আমি মুখ নিচু করে বসে রইলাম।
কাকলির জীবনকাহিনীর মধ্যে, এত বড় একটা বিস্ময় আমার জন্যে যে অপেক্ষা করছে, তা আমি আগে টের পাইনি। মনে পড়ল, আমার বাবার একটা কথা। বাবা বলত–বিয়েটা হচ্ছে জীবনের একটা অঙ্গ। কিন্তু সেটাকে যদি সঙ্গ করে নাও, তবে তোমার পতন অনিবার্য। কাকলির জীবনেও ঘটল সেই অনিবার্য দুর্ঘটনা। আমার জীবনেও কি ঘটেনি তেমন কোনও ট্র্যাজেডি? ব্যর্থ হয়নি কি জীবনের চাওয়া পাওয়া? কাকলি আমার কাছে মুক্তির সন্ধানে এসেছে।
হায়রে হতভাগ্য মেয়ে, তুমি কার কাছে এসেছ মুক্তির খোঁজে? যে নিজেই জানে না তার মুক্তির পথ কোথায়। অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস।
আফগানিস্তান সম্পর্কে এবং এখানকার মানুষের সম্পর্কে, ভালোলাগার বোধ গড়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালার রহমতের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু আজ সেই রহমত খানের দেশটা একটা আতঙ্কের মতো লাগে। মনে হয় এটা কিরহমতের দেশ? এই দেশেই কি থাকত রহমতের মেয়ে? কী ভীষণ অসহায়তা গ্রাস করেছে, এখানকার প্রতিটি মানুষকে। পাহাড়ের গায়ে, পাথুরে জমিতে, খোলা আকাশে সর্বত্রই যেন শুনতে পাই, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্তনাদ, শিশুদের কান্না। আরও অবাক হয়ে যাই রহমত খানের মতো মানুষের লেশমাত্র যখন কারো মধ্যে খুঁজে পাই না। তখন ভাবি-রবি ঠাকুর সত্যিই কি খুঁজে পেয়েছিলেন রহমত বলে কাউকে? নাকি সবটাই তার কল্পনা? আবার ভাবি। রহমত যে একেবারেই নেই তাও তত নয়? আমরা তার সন্ধান পাইনি। আমি হয়তো সন্ধান পেয়েছি জাম্বাজের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু কাকলি? সে কী পেয়েছে? নবাবের মধ্যে দিয়ে অন্তত রহমত খানকে পাওয়া যাবে না। ভাগ্য আজ আমাদের কোথায় এনে ফেলেছে? দুজনের বিড়ম্বনার ক্ষেত্রটা শুধু আলাদা কিন্তু কেন্দ্রবিন্দু তো ওই একটাই?
কাকলি বলেছিল–আমি বুঝতে পারিনি, আরও অনেক যন্ত্রণা অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে।
নবাবের দাদা আমাকে বলল- শুধু আজকের রাতটা, তুমি একা শোবে। একা ঠিক নয়। নবাবের বোনেরাও শোবে তোমার সঙ্গে। কাল থেকে, তুমি, নবাব ও আরানা এক সঙ্গে।
আরানা, নবাবের বিবির নাম।
আমি কোনও উত্তর দিলাম না। কী উত্তর দেবো আমি? আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা করছিল না, ওই দাদাটার সঙ্গে কথা বলতে। এরপর নবাব ও আরানা ঘর থেকে চলে গেল লজ্জায় ঘৃণায় সমস্ত হৃদয় রি রি করছে। দিল্লিতে মাত্র দুটো রাত কেটেছে আমার বিবাহিত জীবনের। মাত্র দুটো দিন নবাব আমার স্বামী হয়েছে। আমি ওই দুটো দিন তাকে আপন করে পেয়েছি। তার পরেই সব শেষ হয়ে গেল। আজ আমার শ্বশুরবাড়িতে প্রথম রাত। পৃথিবীর সব কিছু ঠিক আছে। আকাশে রাতের অন্ধকার আছে। উজ্জ্বল তারাদের দীপান্বিতা আছে। আর আছে একফালি চাঁদ। আমিও বেঁচে আছি। আমার নাড়ি গতিময়। চিন্তাধারা চলমান। শুধু সে আজ আমার পাশে নেই, যার জন্যে ঘরের নিরাপদ জীবন ছেড়ে পা বাড়িয়েছিলাম অজানা অচেনা পথে। ভোরের দিকে একটু ঘুম এসেছিল। হঠাৎ ঘরে কিসের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম সামনে দাঁড়িয়ে আরানা আর তার স্বামী নবাব। নবাব আমাকে বলল, কাকলি ওঠো। আরানা তোমাকে জল এনে দিচ্ছে। তুমি স্নান করে ড্রেস করে বসো। এখুনি সবাই তোমাকে দেখতে আসবে। আর হ্যাঁ, তোমার কাছে যে টাকা আমি রেখেছি, সেই টাকাটা আরানার কাছে দাও। ও রেখে দেবে।
-কেন? আমি কি টাকা রাখতে পারি না? নাকি ও আমার থেকে ভালো হিসেব জানে! আর তাছাড়া আমার যখন টাকার দরকার পড়বে–তখন কি তোমার বিবির কাছে চাইতে যাব? ভীষণ শ্লেষ মিশিয়ে কথাগুলো বললাম আমি। আফগানিস্তানের মাটিতে এই আমার প্রথম প্রতিবাদ। নবাব কী বুঝল কে জানে। আর কিছু বলল না। তারপর সারাদিন ধরে বহু লোকজন আমাকে দেখতে আসতে লাগল। আমি যেন সিনেমার ছবি বা ওই ধরনের কিছু। রাত নটা বাজে। ঘর এতক্ষণে খালি হল। তারপর দেখলাম আরানা বিছানা করছে। বেশ চওড়া বিছানা। তাতে পর পর তিনটে মাথার বালিশ রেখেছে। খানিক বাদে নবাব আমাকে শুতে ডাকল। সে বিছানায় গিয়ে ঠিক মাঝখানে শুয়ে পড়েছে। আরানাকেও ডাকল।
আমি প্রশ্ন করলাম–ও আমি আর তুমি একসঙ্গে শোবো?
–হ্যাঁ! নিশ্চয়ই। আরানাও তত আমার বিবি! এখানে না শুলে সে আর কোথায় যাবে?
–নবাব, তুমি কী বলছ? আমি কিছুতেই পারব না এইভাবে একসঙ্গে শুতে। এই সব নোংরামোতে তোমরা অভ্যস্ত। কিন্তু আমার শিক্ষা, আমার কালচার এসবের সঙ্গে পরিচিত নয়। আমি প্রাণ থাকতেও আমার লজ্জা আর এক জনের সামনে বেআবরু করতে পারব না। স্বামী-স্ত্রীর একান্ত গোপনীয়তার মাঝে অন্য কেউ আসতে পারে না। সেই রাতে নবাব ও আরানা একসঙ্গে শুয়ে পড়ল। আমি একটু দুরে। গিয়ে ওদের দিকে পিছন করে শুয়ে পড়লাম। ঘুম কি আসে? আমার একান্ত মানুষটা পাশেই শুয়ে আছে অন্য জনের বাহুতে। অসম্ভব। অশালীন। কল্পনারও অতীত। জীবনে এমন পরিস্থিতির কথা কি কখনো স্বপ্নেও ভেবেছি? তারপর কাকলি কাঁদতে কাঁদতে, অস্ফুটে বলল–সেই রাতে নবাব আমার সামনেই আরানার সঙ্গে…… কথাটা শেষ করতে পারে না কাকলি। ভেঙে পড়ল কান্নায়।
সকালে কাকলি বিদায় নিল। কিন্তু সারাদিনের সব কাজের মধ্যেও কাকলি একবারও আমার মনের থেকে বিদায় নিতে পারেনি। অবসাদ ও ক্লান্তির মধ্যে দিয়ে দিনটা শেষ। আমার মেজো জা বলল, খাবার দেবো? আমার জা আমাকে, আগলনাওয়ে বলে ডাকে। আমার স্বামীকে ওরা আগল বলে। আগল অর্থাৎ দাদা, আর নাওয়ে মানে নতুন বউ। আগলের নতুন বউ বলে আমি ওদের আগলনাওয়ে।
তৃতীয় অধ্যায়
জীবনে বহু জায়গায় আমি ঘুরেছি। কিন্তু এই দেশটার সবই যেন কেমন অচেনা। যেদিন প্রথম আমি এখানকার ঘরবাড়ি দেখলাম সেদিন ভাবতে পারিনি বাড়ি এমন হয়। প্রথম যখন গজনীতে জাম্বাজের এক ভাগ্নে রফিক খুরিয়ের বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম খুরিয়ে মানে ভাগ্নে, সেদিন তাদের বাড়ি দেখে অবাক হলাম। বাড়ির সদরে একটা বিশাল লোহার গেট। এত বড় গেট একটা বাস অথবা লরি অনায়াসে সেই গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। বাড়ির দেওয়াল, ঘর, মেঝে, সব মাটির। কাবুল শহর ছাড়া সর্বত্র মাটির বাড়ি। পঞ্চাশ বা ষাট ইঞ্চি চওড়া দেওয়াল। দেওয়ালের কোল ঘেঁসে সারি সারি ঘর। গুনে দেখলাম। মোট আটখানা ঘর আছে। আর তার সঙ্গে লাগোয়া লম্বা বারান্দা। বারান্দা থেকে নেমে অনেকটা গেলে ঠিক উঠোনের মাঝখানে একটা ঘর। আর উঠোনের বাঁদিকে একদম কোনার দিকে চারটে গরু দাঁড়িয়ে আছে। রান্নাঘরের ডানদিকের কোনায় একটা পাতকুয়ো। একজন অতি সুন্দরী বয়স্কা মহিলার ডাকে আমি ফিরে তাকালাম। মহিলার পরনে ঘাগরা চোলির মতো পোশাক। মাথায় কালো রংয়ের খুব বড় দোপাট্টা ঘোমটার মতো করে দেওয়া। মহিলাটি প্রথমে আমার সঙ্গে হ্যান্ডসেক করলেন। পরে আমাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে দুগালে দুটো চুমো দিলেন। তারপর আমার হাত ধরে মনের আনন্দ প্রকাশ করলেন। একটি বারো তেরো বছর বয়সের মেয়ে খানিকটা চিনি নিয়ে এসে আমার ওপর ছড়িয়ে দিল। সিদিক হচ্ছে রফিক খুরিয়ের ছেলে। সে আমাকে আপ্যায়ন করে বলল–কি খেতে চাও বলো?
–এখন আমি কিছু খাব না। কথা বলতে বলতেই পরপর আরো চারজন মহিলা এলেন। দুজন আমার বয়সী, আর দুজন আমার থেকে ছোট বলে মনে হল। আর এল একটা বছর বারো তেরোর মেয়ে। সবাই ওই, প্রথম মহিলার মতো করে চুমো দিয়ে আমাকে স্বাগত জানাল। তারপর ওরা আমাকে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসতে বলল।
দরজা দিয়ে ঢুকে মনে হল, ঘরেই ঢুকলাম। কিন্তু না! ওই ঘরটার দিকের কোণ দিয়ে একটা দরজা আর ডান দিকের কোনা দিয়ে একই রকম আর একটা দরজা। আমাকে বাঁদিকের দরজা দিয়ে ঢুকতে বলল। ভিতরে ঢুকে দেখলাম, ঘরের আসবাব বলতে আছে–এক বিশাল তোশক। আর তার ওপর সারি সারি তাকিয়া। সেগুলো পাতা দামি কার্পেটের ওপর। সমস্ত ঘর জুড়েই আছে দামি ফরাসি কার্পেট। উত্তর দিকের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে, পশ্চিম দিকের দেওয়ালে পিঠ করে বসলে ঠিক তার নাক বরাবর একটা জানালা আছে। চওড়ায় ও লম্বায় প্রায় আড়াই মিটার। আমি সেই জানালার কাছে গিয়ে বসলাম। জানালা দিয়ে রান্নাঘরটা দেখা যাচ্ছে। ওই ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেই আন্দাজ করলাম ওটাই রান্নাঘর। আমি বুঝতে পারলাম, ওরা আমার জন্যেই কিছু খাবার করছে। এখানে বৌ আর আইবুড়ো মেয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই। তবু কিছু বৌ আছে, যারা একদম চাপা পায়জামা পরে এবং পা অব্দি কামিজ পরে। এসব আগেই জাম্বাজের কাছে শুনেছি। এখন চাক্ষুস দেখছি। সত্যিই বোঝা দায় কোনটা মেয়ে আর কোনটা বৌ। চাপা পায়জামা পরা কাউকেই এখানে দেখতে পাচ্ছি না। সবাই ঢোলা পায়জামা ও হাঁটু অব্দি কামিজ পরেছে। ওদেরই মধ্যে একজন একটা কানা উঁচু কাঁচের প্লেটে; আমার জন্যে চারটে ডিম পোচের মতো রান্না করে এনেছে। পোচগুলো ঘিয়ের মধ্যে ডুবে আছে। সেই ঘি আর পোচ ভর্তি প্লেটটা আমার সামনে রাখল। আর একটা কাঁচের জামবাটিতে রাখল লস্যির মতো কিছু। দেখে প্রথমে সেটা লস্যি বলে মনে হলেও খেতে গিয়ে বুঝলাম ওটা আদৌ লস্যি নয়; মাখন ভোলা দইয়ের জল মাত্র। এবার আরও অবাক হলাম, ওদের রুটি এবং রুটি রাখার পাত্র দেখে। একটা বড় প্লাস্টিকে মোড়া, বিশাল বড় বড় গোল রুটি। সবাই হাত নেড়ে আমাকে খেতে বলল। আমি বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম সেই রুটির দিকে। খাওয়া তো দূরের কথা, কস্মিনকালে কোনোদিন এমন অদ্ভুত রুটি দেখেছি বলেও আমার মনে হয় না। আমি নিজেকেই নিজে বিদ্রূপ করলাম। আমার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল। হায়রে হতভাগ্য মেয়ে! নিজের অজান্তে নিজেকে, এ তুমি কোন জীবনের সঙ্গে জড়ালে? এই জীবনই যদি তোমার কাম্য ছিল তবে সভ্যতার আলোয়, নিজেকে কেন তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলে? কেন নিঃশ্বাসে টেনে নিয়েছিলে সেই সংস্কৃতির হাওয়া? বেশিক্ষণ ডুবে থাকতে পারলাম না। আমার ডাক পড়ল বাইরে থেকে। গাড়ি তৈরি। কেবল আমার যাওয়ার অপেক্ষা। আমি সবার সাথে একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিলাম। বারান্দা দিয়ে হেঁটে সামনের সেই বিশাল গেটটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এক নতুন অভিজ্ঞতা সঙ্গী করে আবার এগিয়ে চললাম। গাড়ি এবার পাকা রাস্তা নয়, সম্পূর্ণ কাঁচা রাস্তা ধরে ছুটে চলল। রাস্তার দুধারে, একটু তফাতে তফাতে সারি সারি বাড়ি। রাস্তার পাশেই লাগোয়া জমিতে আলু, পেঁয়াজ গাজরের চাষ, কয়েকটা তামাকের ক্ষেতও দেখলাম। তরমুজ, শশা, কুমড়ো এসব তত সর্বত্র। আর দেখলাম, সারি সারি আঙুরের ক্ষেত। আর তারই সঙ্গে হাত দশেকের মতো তফাতে তফাতে আপেল গাছ। গেরুয়া মাটির পথ ধরে গাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। কখনো অনেকটা উপরে উঠছে আবার কখনো নিচের দিকে নামছে। এই ভাবে এক ঘণ্টা চলার পরে, চোখে পড়ল একটা বিশাল ড্যাম। চওড়ায় ড্যামটা গঙ্গার মতো হবে। লম্বায় কতটা বলতে পারব না। এখান থেকে আরো এক ঘণ্টা পথ পেরোলে তবেই আসবে, জাম্বাজদের গ্রাম।
জাম্বাজদের দেশে একমাত্র রাজধানী কাবুলের সঙ্গেই বিদ্যুতের দোস্তি আছে। রাজধানী পেরিয়ে দশমাইল দূরে যখন এসেছি তখন দেখলাম, লাইট পোস্ট আছে বটে, তবে লাইন ও লাইট কোনোটাই নেই। পোস্টগুলো যেন জানান দেয়, ভুল বুঝো না? একসময় আমি, এই গ্রামে গ্রামেও ঘুরে বেড়াতাম। কিন্তু আজ আর আমি এসব গ্রামে আসি না। এদের সঙ্গে বর্তমানে আমার কোনও দোস্তি নেই।
হঠাৎ, কী একটা চিৎকারে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সবাই কি যেন বলতে বলতে আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে দৌড়ে আসছে। শুধু এইটুকুই বুঝলাম ওরা জাম্বাজ জাম্বাজ বলে দৌড়ে আসছে।
গাড়ি আবার আর একটা সেইরকম বিশাল লোহার গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। দাঁড়ানোর পরেই জাম্বাজ নিচে নেমে গেল। এবার আমাকে নিয়ে ওই গেট দিয়ে গাড়ি ভিতরে ঢুকল। এতক্ষণ যে গাড়ি চালাচ্ছিল এবার সেও নেমে গেল। গাড়িতে তখন আমি একা। দেখতে দেখতে বাড়ির উঠোন লোকে লোকারণ্য। তার মধ্যে থেকে এক মহিলা আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। গাড়িতে উঠেই, সে আমার ওপর কিছু চিনি ছড়িয়ে দিল, তারপর আমার হাত ধরে নিচে নামলো। এবং ভিড় ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল।
একটু পরেই শুনতে পেলাম মেসিনগানের আওয়াজ। আমি ভয়ে চমকে উঠলাম। আমি যে ভয় পেয়েছি, সেটা ওই মহিলা বুঝতে পারলেন, এবং বাইরে গিয়ে এক ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে এলেন। এক মুখ ভর্তি দাড়ি নিয়ে একজন চোখ কানা ভদ্রলোক আমার সামনে এসে বললেন-বেটি ভয় পেয়ো না। বাড়িতে বৌ হয়ে এসেছ বলে সবাই আনন্দে আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ছে। আমাদের এখানে বাজি পাওয়া যায় না। তাই সবাই বন্দুকের গুলি চালিয়েই আনন্দ প্রকাশ করে। ওদের ওই বন্দুকের একটা গুলি যদি সেদিন আমার হৃৎপিণ্ডটাকে ভেদ করে বেরিয়ে যেত, তবে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মোকাবিলা আমাকে করতে হয়েছে; অন্তত তার থেকে মুক্তি পেতাম। এরপর শুরু হল আমার শ্বশুরবাড়ির ঘর করা। আমার শ্বশুররা তিন ভাই। বড় এবং মেজো মারা গিয়েছেন। ছোট ভাই বেঁচে আছেন। আমার শ্বশুর ছিলেন মেজো। তিনি কলকাতাতেই দেহ রেখেছেন। শুনেছি গোবরাতে তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। ছোটভাই আসাম খান। তার দুই বিবি। পাবলু বড়। ছোট নাসিরা। দুই সতীনে একই সঙ্গে একই বাড়িতে থাকে। স্বামী পালা করে বৌদের ঘরে যায় দুদিন করে পালা পরে। বড় বৌয়ের দুই মেয়ে, ফৌজি ও গুলাপি, এক ছেলে সুলতান। ছোট বৌয়ের পাঁচ ছেলে, দিনার, আলিখেল, কুলিই, গুড়াই ও ইসলাম। আর পাঁচ মেয়ে। কাফুই, সায়েস্তু, গোল পরী, অন্যদের নাম মনে পড়ছে না। জ্যাঠা শ্বশুরের প্রথম পক্ষের বৌ মারা গেছে। তার এক মেয়ে সামালা, এক ছেলে আদ্রামান। দ্বিতীয় পক্ষের বৌ বর্তমান। তার দুই ছেলে, আদম ও জারখান। আমার শ্বশুরের চার ছেলে, জাম্মাজ, কালা, মুশা ও শাওয়ালি। এক মেয়ে গুনচা। বিয়ে হয়ে গিয়েছে।
অবশ্য, আমরাও চার ভাই বোন। আমি আমার বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান। আমার পর তিন ভাই। আমার বাবারাও তিন ভাই। বোন দুজন। আমার শ্বশুরের বোন একটা। আমার বাবা ডিফেন্সে সার্ভিস করেন। আমার শ্বশুরবাড়ির কেউই চাকরি বারি করে না।
যে সময়, একবার চলে যায় তা আর ফিরে আসে না। দিন যায়, রাত আসে। এই দিন-রাতের আসা যাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমার নিত্যদিনের জীবন কেটে যায়। এখন আমি আর শ্বশুরবাড়িতে নতুন নই। আমার একুত্রিশ বছর বয়সের সঙ্গে আরো ছমাস যোগ হয়েছে। আর ছমাস গেলে, আমার বত্রিশ বছর পূর্ণ হবে। আস্তে আস্তে আমি ওদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। তাই সবার আগে দরকার হল ওদের ভাষাটাকে আয়ত্তে আনার। আমি যখন ওদের ভাষাকে আয়ত্তে এনে সবাইকে আপন করে নিতে চলেছি ঠিক এইরকম একটা সময়ে, আমাকে বিয়ে করার অপরাধে জাম্বাজকে পরিবার থেকে আলাদা করে দিল। ওর ছোট চাচা, আসাম-খান মানুষটা ভারী অদ্ভুত। টাকা খরচের ভয়ে তিনি তার মৃত ভাইয়ের ছেলেদেরও অবিবাহিত জীবন যাপনে অভ্যস করিয়েছেন। মেপে মেপে খাবার দিতেন। বছরে একবার জামা প্যান্ট দিতেন, তাও আবার চাচার পরা পুরনোগুলো। এমন অবস্থায় আলাদা হয়ে বরং ভালোই হয়েছে।
আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ওদের এই পরিবেশের মধ্যে থেকে আমিও একটু একটু করে ওদের মতো হয়ে যাচ্ছি। এক সভ্য জগতের শিক্ষিতা মেয়ে আমি ধীরে ধীরে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছি। একে একে আমার স্ট্যাটাস, আমার অহং, আমার আভিজাত্য, সমস্ত বিসর্জন দিতে লাগলাম। মিশে যেতে লাগলাম ওদের মধ্যে। সাল, মাস, বার, তারিখ–এসব আস্তে আস্তে মুছে যেতে লাগল মন থেকে। খবরের কাগজ, টিভি, রেডিও কিছুই তো এখানে নেই। তাই কিছু জানার উপায়ও নেই। এখানে বারকে বলে, এক সাম্বা, দু সাম্বা, ছ সাম্বা। এরা কেউই রান্নার পদ্ধতি জানে না। আলু-পেঁয়াজ, টমেটো ছাড়া অন্য তরিতরকারি কেউই চেনে না। মাংসের স্টুয়ের মতো বানিয়ে তাতে রুটি ছিঁড়ে দিয়ে দুধ রুটির মতো করে ভিজিয়ে তারপর খায়। স্টুকে এখানে সুরুয়া বলে। পানীয় বলতে আছে ব্ল্যাক ও গ্রিন টি, কিসমিস ও লজেন্স মুখে রেখে চায়ের সিপ করে। শিক্ষা ও সভ্যতার আলো থেকে আফগানিস্তানের অধিকাংশ মানুষ আজ বঞ্চিত। প্রায় সতেরো বছর ধরে এদেশে যুদ্ধ হচ্ছে। সাধারণ মানুষ স্পষ্টতই ভীত ও সন্ত্রস্ত। প্রত্যেকটি দিন বিভীষিকাময়। আমাদের দেশের শিশুরা সরস্বতীর কাছে হাতেখড়ি দিয়ে কলম ধরে। আর এদেশের শিশুরা শপথ করে বন্দুক হাতে তুলে নেয়। দেশের অবস্থা খুবই শোচনীয়। ডঃ নাজিবুল্লার সৈন্যরা রাশিয়ানদের নিয়ে হেলিকপ্টারে করে এসে একের পর এক গ্রামে বোমা ফেলে যাচ্ছে। কারো বাড়িতে আলো জ্বেলে রাখতে পারে না। কোনও বাড়িতে অনুষ্ঠান হলে, অন্ধকারেই তা সমাধা করতে হয়। দেশের সর্বত্র মাইন পোঁতা আছে। যেখানেই পা দেবে, সেখানেই মৃত্যুর পরোয়ানা। রাতের নির্জনতায় বারান্দায় এসে দাঁড়ালে অনবরত শোনা যায় কামানের আওয়াজ। বাতাসে বারুদের গন্ধ। অন্ধকার, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও আতঙ্কের রাত পোহাতেই দেখা দেয় আর একটা দিনের সূর্য। এখানে যুদ্ধ সমাপ্তি বোধহয় কোনদিনও হবে না। গণতন্ত্র জিন্দাবাদ প্রতিধ্বনিত হবে না। পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছড়িয়ে থাকা মানুষগুলির মুখে কেউ দেখবে না শিশুর মতো সরল হাসি। আনন্দে উদ্ভাসিত হবে না কারুর মুখ। ১৯৮৯-এর শেষে জাম্বাজের এক চাচা গফর খান তার ছেলেকে নিয়ে চোরাপথে নিজের লিরি নিয়ে মাল আনতে যাচ্ছিল আঙ্গুরহাটা বলে একটা শহরে। আঙ্গুরহাটা পাকিস্তানের বর্ডার। এই আঙুরহাটা যাওয়ার রাস্তা আগে রাশিয়ান তথা নজিবুল্লার কজায় ছিল। পরে মুজাহিদরা ওদের হঠিয়ে দিয়ে এই রাস্তাগুলো দখল করেছে। এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় গফর খানের লরির চাকা পড়ল মাটিতে পুঁতে রাখা মাইনের ওপর।
বাড়িতে খবর এল। আমরাও শুনলাম। গ্রামের লোক কেঁদে আকুল। আমিও তো মানুষ! তাই সবার কান্নার সঙ্গে আমিও কেঁদেছি। সবাই তখন গাড়ি নিয়ে গফরের উদ্দেশে রওনা দিল। পরের দিন সকালে সবাই ফিরে এল হাসি মুখে। সঙ্গে গফর ও আম্মাজান। তাদের যে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাওয়া যাবে এ কথা কেউ ভাবেনি। এদেশে পদে পদে এরকম মৃত্যু ফাঁদ পাতা। কোথাও রাশিয়ান ও নাজিবের দাপট, আবার কোথাও বা মুজাহিদদের। সব মিলিয়ে এক অদ্ভূত পরিস্থিতি এ দেশটায়। যে কোনও সভ্য দেশের সাধারণ লোকজন নিরস্ত্র। আর এদেশে সবার ঘরেই অস্ত্র মজুত। সর্বত্র পোঁতা আছে ভয়ঙ্কর মাইন। গফর খানের গাড়ি পড়েছিল সেই মাইন পাতা এক প্রান্তরে। শেষ পর্যন্ত আল্লাই তাকে রক্ষা করেছেন। নবজন্ম হল গফর খান ও আম্মাজানের। শুধু সাধের গাড়িটি রইল না। এই ঘটনা যখন ঘটেছে ঠিক সেই সময় আমি খুব অসুস্থ। আমাকে ডাক্তার দেখানো খুব জরুরি। কিন্তু কাছেপিঠে কোথাও ডাক্তার নেই। ডাক্তার দেখাতে গেলে যেতে হবে, মুশখেল বলে একটা শহরে। তবে সেখানে পাশ করা কোনও ডাক্তার নেই। বই দেখে ওষুধ দেয়। এই ঘটনার অনেক পরে আমি ওষুধের দোকান করেছি। ঠিক হল, সেই ডাক্তারের কাছেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু সবাই ভয় পাচ্ছে মুশখেলে যেতে। কারণ মুশখেল ও আমাদের গ্রাম শেরাকালার মাঝখানে পড়ে একটা প্রকাণ্ড মাঠ। কম করেও চারটে গড়ের মাঠের সমান। সেই ময়দান পেরিয়ে যাওয়া মানে, মৃত্যুর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া। কারণ হেলিকপ্টারে সবসময় রাশিয়ান সৈন্যরা গ্রাম পাহারা দেয়। কোনও গাড়ি দেখলেই, হেলিকপ্টার তখনি নিচে নেমে আসবে। এবং সন্দেহজনক মনে হলেই গুলি করে মেরে ফেলবে। কোনও অজুহাতই চলবে না। যাত্রীদের কারুর কাছে যদি মেশিনগান থাকে তাহলে আর রক্ষে নেই। এদিকে মেসিনগান না নিয়ে গেলেও বিপদ। যদি বাঘ বা অন্য জন্তু আসে? চোর পিছু নেয়?
ভয়ে সবাই যখন পিছু হটে গেল, তখন জাম্বাজ বলল,-তোমাদের কারুর যাওয়ার দরকার নেই, আমি নিজেই নিয়ে যাব। মস্ত একটা ট্রাকটর ইঞ্জিনের শব্দ তুলে যখন থরথর করে কাঁপছিল, আমি তখন সালোয়ার কামিজ পরে বাইরে বেরোলাম। কনকনে শীতের দাপটে গায়ে একটা শালও জড়ালাম। দরজা খুলে বাইরে আসতেই, এক ঝলক কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস আমার মুখে এসে যেন সজোরে ধাক্কা মারল। হাসিমুখে মাথার ফ্যাকাশে খয়েরি চুল ঠিক করতে করতে আবু আমার সামনে এসে বলল, আমিও যাবো। আবু, জাম্বাজের জেঠিমা আর এলো জাম্বাজের জ্যাঠতুতো বৌদি। উঠে বসলাম আমরা। একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে এগোল ট্রাক্টর। আবু আর বৌদির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম আমি। গাড়ি চলল ফটকের মস্ত গেট পেরিয়ে। আঁকুনি দিয়ে, এপাশে, ওপাশে হেলে গাড়ি এবার চারদা গ্রামের পথ ধরল। মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখা যাচ্ছিল সশস্ত্র মুজাহিদ সৈন্যদের। বন্দুক তুলে চিৎকার করে বলছিল-মুসলমান? নাকি কাফের? কিন্তু জাম্বাজ অতি দক্ষতার সাথে, দুর্বোধ্য কী সব বলে গাড়ি হাঁকিয়েই চলল। চারদা গ্রাম পেরিয়ে আরও পশ্চিমে বাঁহাতের কোনার দিকের কটুয়াল গ্রাম ছাড়িয়ে আমরা ময়দানে ঢুকলাম।
জনহীন, সুনসান রাস্তা বা ময়দান। তীব্র উত্তেজনা সত্ত্বেও নিপুণভাবে গাড়ি নিয়ে ছুটে চলেছে জাম্বাজ। এক ভয়ঙ্কর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। যেন এক অতল গহ্বর আমাদের গ্রাস করতে ধেয়ে আসছে। মাইল পাঁচেক এগিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ ট্রাক্টরের গর্জন ছাপিয়ে একটা হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আবু ও বউদি মেসিনগানটা রেখে তার ওপর আমাকে চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়তে বলল। জাম্বাজ ফুল স্পিডে গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে চলল। তবুও হেলিকপ্টারের সঙ্গে পারবে কেন? হঠাৎ একটা কপ্টার আমাদের গাড়ির রাস্তা রুখে দাঁড়াল। আমার পালস রেট দ্রুত থেকে দ্রুততর হল। দেশের যুদ্ধের সামগ্রিক অবনতির একটা মানচিত্র আমার চোখের সামনে। বউদি কেঁদেই চলেছে। আবু হঠাৎ চুপ হয়ে আশঙ্কায় সময় শুনছে। জাম্বাজ পিছন ফিরে আমাদের দিকে তাকাল আমি উঠে বসে ওকে দেখছি। ওর দুচোখ জল টসটস করছে। বুকফাটা আর্তনাদের সঙ্গে একটাই কথা বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে–আবু, আমাকে যদি ওরা মেরে ফেলে, তবে পাগলিকে তোমরা অবশ্যই তার দেশে পাঠিয়ে দেবে।
এবার আমি কান্নায় ফোঁপাতে লাগলাম। গলাটা বুজে এল। কিছুই আমি জাম্বাজকে বলতে পারলাম না। আবু ও বউদি চুপ করে কেবল দেখতে লাগল আমাকে। এগিয়ে আসতে লাগল রাশিয়ান সৈন্যরা। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর হঠাৎ দৌড়ে ধেয়ে এল। ওদের মুখগুলো নিষ্ঠুরতা আর আক্রোশে ভরা। একজন সৈন্য চিৎকার করে জাম্বাজকে বলল–কোথায় যাচ্ছো।
জাম্বাজ উত্তর দিল, মুশাখেলে যাচ্ছি। আমার বিবি ভীষণ অসুস্থ। তাই ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছি। ততক্ষণে আমি ফের শুয়ে পড়েছি। গোটা চারেক সৈন্য ঘিরে ধরল আমাদের। আমার বুকের ভিতর ভয়ানক কাঁপুনি। এবার ওরা নিশ্চয়ই জাম্বাজকে মেরে ফেলবে। শেষ হয়ে যাবে আমার জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া, সুখ, ভালবাসা। এই রাশিয়ান সৈন্যদের হামলার মুহূর্তে বুঝলাম, জাম্বাজকে আমি কতখানি ভালবাসি। ওর পরিবর্তে যদি আমাকে মেরে ফেলে, তবেই আমি শান্তি পাব। সৈন্যদের আর একজন রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করল- তুই কি মুজাহিদ?
না আমি মুজাহিদ নই। আমি হিন্দুস্থানে থাকি। আমার বিবি হিন্দুস্থানি। মাস দুয়েক হল বিবিকে আমাদের দেশ দেখাতে এনেছি। আর পনেরো দিন বাদেই চলে যাব।
সৈন্যগুলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। কিছুক্ষণের জন্যে আমরা সবাই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছি। সৈন্যরা খুঁটিয়ে আমাদের আপাদমস্তক দেখে বলল-আমস আছে সঙ্গে?
-না, আমরা মুজাহিদ নই। আর্মস কোথায় পাব?
–সত্যি নাকি মিথ্যে?
–না মিথ্যে না। আপনারা সার্চ করতে পারেন।
না। সেদিন তারা জাম্বাজের ওপর গুলি চালায়নি। একটা বিজয়ের হাসি হেসে জাম্বাজ আবার গাড়ি স্টার্ট দিল। এবার আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবলাম এই রক্তক্ষয়ী দিন কবে শেষ হবে? নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষগুলো কি শান্তির সন্ধান কোনোদিনও পাবে? যুদ্ধ-শান্তির প্রতিশ্রুতি কি কেউ তাদের দেবে? আমাদের গাড়ি ততক্ষণে একটা ডাক্তারখানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালাম। সামনেই দেখতে পেলাম একটা ছোট ওষুধের দোকান।
জাম্বাজ আমাদের নিয়ে ডাক্তারখানার কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ডাক্তার সোৎসাহে অভিনন্দন জানালেন। ভেতরে গিয়ে বসতে বললেন। মেয়েদের বসার জায়গা ভেতরেই। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ডাক্তার এলেন। একটু ভারী চেহারা। মুখ ভর্তি দাড়ি। মাথার চুল কাধ পর্যন্ত নেমেছে। চোখ দুটো বেশ বড় বড়। পরনে একটা সাদা খান ড্রেস। গায়ে একটা কালো রংয়ের বড় শাল। বয়স হবে আটত্রিশ কি চল্লিশ। কোনও ডাক্তারসুলভ অঙ্গভঙ্গি নেই। অতি সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার। সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন-কী হয়েছে? তার দৃষ্টি জাম্বাজের মুখের ওপর।
জাম্বাজ বলল, ডাক্তারসাব আমার বিবি হিন্দুস্থানি। মনে হয় এখানকার জল হাওয়া ওর সহ্য হচ্ছে না। তাই কিছু খেতে পারে না। বমি হয়। মাথা ঘোরে।
ডাক্তার একটা স্টেথিসকোপ আমার পেটে লাগিয়েই তুলে নিলেন এবং বললেন–বুঝেছি, জন্ডিস হয়েছে। আমি ওষুধ দিচ্ছি। সব সেরে যাবে। কথা শেষ করে তিনি বাইরে চলে গেলেন।
আবু বলল-দেখলে তো কত বড় ডাক্তার? দূরবীন লাগিয়েই বুঝতে পারল তোমার কী হয়েছে। এখানে স্টেথিসকোপকে দুরবীন বলে।
আমি হতবাক। এ কোন দেশে এসেছি আমি? বমি ও মাথা ঘোরা বা খেতে পারি না বলে পেটে স্টেথো? জীবনে শুনিনি পেটে স্টেথো দিয়ে দেখে।
জাম্বাজ ইতিমধ্যে ওষুধ নিয়ে ভেতরে এল। একটা সরু তিন ইঞ্চি কৌটোয়, খান দশেক গোল চাকার মতো বড় বড় বড়ি। নাম ক্যালসিয়াম স্যান্ডোজ উইথ ভিটামিন সি আর এক শিশি ব্লড বিল্ডার ভিটামিন বি, বি, বি, ট্যাবলেট পাঁচশো এমজি। আরো দু একটা প্যাকেটও আছে।
আমি ওষুধ দেখে আঁতকে উঠলাম। এ করেছে কি? আমি জানি আমার জন্ডিস হয়নি। আর হলেও এই কি তার ওষুধ? এ তো মানুষ মারার ফাঁদ! সবাইকে তা হলে এই ধরনের ওষুধই দেয়? কোনও রোগ যদি তাদের নাও থাকে; তবে এই ধরনের ওষুধ খেলেই তো রোগ হতে বাধ্য। এই রকমই সৃষ্টি করা রোগ হয়েছিল গুলগুটির ছেলের। মাত্র তিন বছর বয়স, এই বয়সেই তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়েছিল। দিন দিন তার পেট ফুলে উঠতে লাগল। কোটরাগত চোখ দুটো আরও কোটরাগত হল। হাত ও পা রোগা লিকলিকে। মুখটা ফ্যাকাশে। কিন্তু ডাক্তার যা ওষুধ দেয় তাতে রোগ সারে না। বরং বেড়ে যায়। গুলগুটির স্বামী তখন কুয়েতে। ছেলেকে ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে কে? আসাম চাচার হাতে তখন সমস্ত সংসারের ভার। সুতরাং ডাক্তার দেখাবার জন্যে তার কাছেই হাত পেতে দাঁড়াতে হবে। চাচার বড় বৌ পাবলু তখন সংসারের প্রথম মহিলার স্থানে। হিন্দুস্থান থেকে যে সব টাকা সংসারের জন্যে আসে, তার বেশির ভাগ টাকাই চলে যায় পাবলুর বাপের বাড়ি। তায় এ সব উটকো ঝামেলা। সংসারে বাড়তি খরচা হওয়াটা তার কাছে ঝঞ্ঝাট বলে মনে হয়। অসুখ-সুখ না হয়ে বরং মরে গেলেই পাবলুর শান্তি। অন্তত বাড়তি খরচার হাত থেকে সে বেঁচে যায়। তবুও লোক লজ্জার ভয়ে একদিন কিছু ওষুধ এনে দিয়েছিল। অবশ্যই ওই মুশখেলের ডাক্তারের থেকে। সকাল থেকে রাত অব্দি এগারো দাগ ওষুধ খাইয়েছিল ওই তিন বছরের বাচ্চাটাকে। পরের দিন বিকেলে সূর্য যখন ঢলে পড়েছে পশ্চিমে, দিনের শেষ আলোটুকু ছুঁয়ে আছে পাহাড়ের মাথায়, মাঠের গরুগুলো গোয়ালে ফিরে আসছে, পাখিরা কিচির-মিচির ধ্বনি তুলে বাসার দিকে ডানা মেলেছে। ঠিক এমনি একটা সময়ে গুলগুটির ছেলে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। মা তখন তাকে নিজের বুকের দুধ পান করাচ্ছিল। ছেলের মাথায় মায়ের স্নেহের অতি আদরের একটা হাত চলাফেরা করছিল।
ঠিক সেই সময় জ্যাঠ শাশুড়ি আবু এসে বলল–কাকে দুধ খাওয়াচ্ছ?
গুলগুটি বুঝল তার ছেলে তাকে, মা বলে কোনোদিন আর জড়িয়ে ধরবে না। তখন সে ছেলেকে কোল থেকে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর স্থিরভাবে নিস্তব্ধ পায়ে ঘর থেকে বাইরে চলে গেল।
আসাম খান সেই মৃত বাচ্চাটাকে নিয়ে গিয়ে কবর দিয়ে দিল। পরের দিন সকালে, আসামের ছোট বৌ নাসিরা এসে বলল-তোমার ছেলে তো মরে গেছে ওই ওষুধগুলো তুমি আর কি করবে? ওগুলো আমাকে দাও। আমি আমার ছেলেকে খাওয়াব। ওষুধগুলো নিয়ে এসে নাকসিরার সদ্যোজাত শিশুকে খাওয়াতে লাগল। ওই ওষুধের প্রতিক্রিয়া সদ্যোজাত শিশুটি সহ্য করতে পারল না। একটা পা তার পুরোটাই বেঁকে গেল। খোঁড়া হয়ে গেল সে চিরদিনের মতে, ডোজ কম ছিল বলে প্রাণে বেঁচে রইল। মাসখানেক পরে, পাবলুর বড় ছেলে সোলেমান অসুখে পড়ল। বারো বছর তার বয়স। সোলেমানের রোজ জ্বর হয়। কিছু খেতে পারে না। বমি হয়। বমির সঙ্গে রক্ত পড়ে। পাবলু কেঁদে কেটে বাড়ি মাথায় করল। এবার কিন্তু মুশখেলের ডাক্তারের ওপর নির্ভর করল না। সোজা পাকিস্তানে নিয়ে গেল। সোলেমানের বাবা তো বাড়িতেই আছে ভাবনা কি। মাও তো, সংসারের সবাইকে বঞ্চিত করে বেশ পয়সা জমিয়েছে। কিন্তু আল্লার মার দুনিয়ার বার। বাবা ও মায়ের পাপের ফল ভোগ করল ছেলে। পাকিস্তানের ডাক্তার সোলেমানকে ফেরত পাঠাল। তার ক্যানসার হয়েছে। মাত্র একমাস মেয়াদ আছে তার, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার। পাবলু কেঁদে ভাসালো। এও বুঝল, আল্লা পাপের শাস্তি এই দুনিয়াতেই দেন। গুলগুটির বুক ফাটা আর্তনাদ, খোদার আসনকেও টলিয়ে দিয়েছিল।
আমরা জানি যে, শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ। কিন্তু যে দেশে শিশুদের ভবিষ্যত নিয়ে আনাড়ি স্বার্থপর লোকেরা ছিনিমিনি খেলে সেই দেশের ভবিষ্যত কী?
এ দেশে মানুষের জীবনের কোনও দাম নেই। শিশুদের কথাও কেউ ভাবে না। তাই ভবিষ্যতের মানুষরা এভাবেই বিনা চিকিৎসায় আর কুচিকিৎসায় শেষ হয়ে যায়। আমার মনে হল গোটা আফগানিস্তান যেন বীভৎস অন্ধকারের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। এই যাওয়া কি কোনও ভাবেই রোধ করা যায় না? কিন্তু কোনও পথ পাই না। তাই ভাবনা থেমে থাকে। মনে হওয়া–মনেই থাকে। ডাক্তার দেখিয়ে বাড়িতে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। চাই না আমি সুস্থ হতে। এখানে এভাবে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়া অনেক ভালো। এদেশে কোনও বৌ যদি মারা যায় তবে এদের আফশোসের সীমা থাকে না। কারণ প্রচুর টাকা দিয়ে বৌ কিনতে হয়। সুতরাং কিনে আনা দামি বৌ যদি মারা যায়, তবে আবার তো কিনতে হবে! তা হলে তো অনেক লোকন?
এখানে মেয়েদের পরিচয় শুধু শয্যাসঙ্গিনী, রাঁধুনি আর সন্তান উৎপাদনের মেসিন। মানে থ্রি ইন ওয়ান। সংসারের সবাইকে সেবাযত্ন করার পর প্রতি বছরে একটা করে নতুন কিছু সৃষ্টি তাকে করতেই হবে। অর্থাৎ সন্তানের জন্ম দিতে হবে। যদি কোনও কারণে বৌ সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম হয়, তবে তার ঘরে সতীন আসবেই। এই নিয়ম শিথিল হবার নয়।
না, তা বলে তালাক দেবে না। অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মতো বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের মতো। এদেশের মুসলিমরা তত কঠোর নয়। অন্ধ, কালা, খোঁড়া, কুরূপা যাই হোক না কেন তাকে নিয়েই ঘর করতে হবে। স্বামী যখন দ্বিতীয় বিবাহ করে, তখন প্রথম বৌ সবার কাছে আরো বেশি প্রাধান্য পায়। সবাইকার সিমপ্যাথি নিয়েই তাকে সারা জীবন বেঁচে থাকতে হবে। এখানকার সব কিছুই কেমন যেন অদ্ভুত। আমি আসার পর যখন দেখলাম যে আমার দেওরদের একজনেরও বিয়ে হয়নি, অথচ সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক তখন আমি মেয়ে খুঁজতে শুরু করলাম। কাটয়াজে মেয়ে দেখতে গিয়ে একটা বাঙালি মেয়ের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু মেয়ে পছন্দ হয়নি। তারপর খবর পেলাম, আন্দার বলে একটা গ্রামে ভালো মেয়ে আছে। সেই আন্দার গ্রামের মেয়েই এখন আমার মেজো জা সাদগি। সাদগির দাদা কুড়ি লক্ষ টাকার বিনিময়ে সাদগিকে আমাদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলো। এদেশের অনেক অদ্ভুত নিয়মের মধ্যে আর একটা নিয়ম হল, বিয়ের সব ঠিক হবার পরও মেয়ে তার বাপের বাড়ি থাকবে এক বছর। তারপর হবে বিয়ে। আর বিয়ের আগে জামাই আসবে মেয়ের কাছে। অবিবাহিত মেয়েজামাই একঘরে শোবে। কিন্তু যদি মেয়ে গর্ভবতী হয় তবে সর্বনাশ। জামাইয়ের বাড়ি থেকে আরো বিশ লক্ষ টাকা দাবি করবে। এবং এই এক বছর মেয়ে যে বাপের বাড়ি থাকবে, তার যাবতীয় খরচা ছেলের বাড়ির লোককে বহন করতে হবে। পণপ্রথা আমাদের দেশেও আছে। শুধু তফাত এই যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত বাবা ও মায়েরা মেয়ের বাড়ি থেকে পণ নিয়ে ছেলেকে বিক্রি করে। আর কাবুলে অশিক্ষিত বাবা ও মায়েরা, ছেলের বাড়ি থেকে পণ নিয়ে মেয়েকে বিক্রি করে। জানি না, শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের পার্থক্যটা কোথায়! আমি তার হিসাব মেলাতে পারি না।
আরও একটা ব্যাপার হল, হিন্দুস্থানের বাবা ও মায়েরা পণ দিয়ে বর কিনেও মেয়ের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। একটা ভয় থেকেই যায়, এই বুঝি খবর এল তাদের আদরের মেয়েকে পুড়িয়ে না হয় কুপিয়ে মেরেছে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। নতুবা দুশ্চরিত্রা বলে ঘরে ফেরত পাঠিয়েছে। টাকা পয়সা তো গেলই সেই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার।
কাবুলের বাবা ও মায়েরা নিশ্চিন্ত তাদের মেয়েকে বিক্রি করার পরও। চরম খারাপ যদি হয় তো হবে। জামাই না হয় আবার একটা বিয়ে করবে। কিন্তু তাদের মেয়েকে তার নিজের অধিকার থেকে মৃত্যু ছাড়া কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। পৃথিবীর সব দেশেই ভালো আর মন্দ দুই-ই আছে। কোনও দেশের মানুষ বলতে পারবে না আমি সর্বাঙ্গ সুন্দর আমাদের দেশে হত্যাকাণ্ড, লুটতরাজ, গুণ্ডাবাজি কিংবা নাগরিকদের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয় না।
চতুর্থ অধ্যায়
বরাবরই আমি একটু অন্যরকম। যে কোনও অমানবিক বিষয় বা ঘটনা আমাকে নাড়া দেয়, যন্ত্রণা দেয়। তাই প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করি। কোথাও সফল হই, কোথাও হই না। এই রকমই একটা ব্যাপারে আমি একবার প্রতিবাদ করেছিলাম এখানে। আমাদের একটা বিশাল আঙুরের বাগান আছে। আঙুর পেকে গেলে, সেই আঙুর বাড়ির ছাদে এনে ঢেলে দেবে। তারপর ঠিক ধান রোদে দেবার মতো করে ছড়িয়ে মেলে দেবে। দশ বারো দিনে আঙুর শুকিয়ে কিসমিস হবে। তারপর সেগুলো পরিষ্কার করে ভাগ হবে। আমি দেখলাম, যখন কিসমিস ভাগ করছে তখন আসাম খানের বড় বৌ সেই ভাগের বিচারিকা। আসামের দুই বৌ, দুটো ভাগ নিয়েছে। জ্যেঠ-শ্বশুরের নিজের বৌয়ের একটা ভাগ, ও ছেলে আদ্রামানের বৌয়ের একটা ভাগ। আর আমার শাশুড়ির একটা ভাগ। আমি ভাবলাম, এটা কেমন হল? দুই শ্বশুরের ঘরে দুটো করে ভাগ যাচ্ছে। আর আমার শাশুড়ি প্রতিবাদ করে না বলে, তার একটা ভাগ? আমি তখন পাবলু চাচিকে বললাম, চাচি, এটা কেমন ভাগ হল? তোমরা সবাই দুটো করে ভাগ নিলে, আর আমাদের একটা ভাগ? তোমরা সবাই খেতে পারো, আর আমার দেওররা খাবে না?
পাবলু চাচি বললে–সারা জীবন তো এই ভাবেই ভাগ হচ্ছে। আমার আর আমার সতীনের আলাদা, আবু আর ছেলের বৌয়ের আলাদা।
-তুমি আর তোমার সতীন কি আলাদা থাকে? তোমাদের হাঁড়ি কি আলাদা?
-বালাই ষাট। আমরা আলাদা হতে যাব কেন? আর কার সঙ্গেই বা আলাদা হব? স্বামী তো একটাই সুতরাং স্বামীকে কী করে ভাগ করব?
-আলাদাই যখন নয় তখন কিসমিসের ভাগ আলাদা হবে কেন?
-তোমার শাশুড়ি এক মহিলা। আর আমরা দুজন করে গৃহিনী। তাই আমরা দুটো করে ভাগ নিই।
-না। তা হবে না। গৃহিনীর হিসাবে ভাগ হবে না। বাড়ির ছেলেদের হিসাবে ভাগ হবে। আমার শ্বশুররা তিন ভাই। সুতরাং তিনটে ভাগ হবে। পাবলু আমার কথা শুনে রেগে মেগে, কিসমিস রেখে উঠে গেল। কিসমিস পড়ে রইল। আমার শাশুড়ি ও দেওররা প্রমাদ গুণতে লাগল। আসাম চাচা বাড়ি এসে সব শুনে এমন রেগে যাবে যে আমাকে নাকি মেরেই ফেলবে। দেওররা ও শাশুড়ি খাওয়া-দাওয়া ফেলে ঘরের কোণে আশঙ্কায় চুপ করে বসে রইল। জাম্বাজ বাড়িতে ছিল না। গজনীতে মায়ের জন্য ওষুধ কিনতে গিয়েছিল। কিন্তু যাকে নিয়ে তাদের এত ভয় সেই আমি নির্বিকার। নিরুত্তাপ। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধেই আমি আমার মত প্রকাশ করেছি। অবিশ্বাস্য রকম ভয় আমার দেওররা পেলেও আমি চুপ। বরং চা বানিয়ে বারান্দায় বসে চা খেতে লাগলাম। প্রায় আধঘণ্টা পর, সব্বার আতঙ্কিত মুহূর্ত এল। আসাম চাচা ঘরে ঢুকল। আমি তখন বারান্দায় বসে আমেরিকার ফার্স্ট লেডি বইটা পড়ছি। আর শীতটাকে দূরে সরানোর জন্য রোদের তাপ নিচ্ছি। ভাবছিলাম, চাচা কি খুব খারাপ লোক? আসলে বৌ দুটোই শয়তান। তাদের প্ররোচনাতেই হয়তো চাচা সবার প্রতি এত উদাসীন।
চাচা ঘরে ঢোকার পর অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। কেমন যেন একটা চাপা উৎকণ্ঠায় সময় কাটাচ্ছি। চাচা যদি বৌদের কথায় বেরিয়ে আসে ঘর থেকে? আমায় প্রশ্ন করে কেন আমি এমন কথা তার বৌদের বলেছি? কী উত্তর দেবো আমি? হাজার হলেও শ্বশুর বলে কথা। তার সঙ্গে তর্ক কি করতে পারব?
হঠাৎ একটা বিকট চিৎকার শুনলাম। কনকনে শীতের সন্ধ্যায় জনশূন্য এলাকায় এমন বিকট চিৎকার কতদুর যে যেতে পারে তা বোধহয় আসাম খান জানে না। আর সে জন্যেই এমন কুৎসিত গর্জন করতে পারল। অসীম আক্রোশে ঘর থেকে বেরিয়ে এল আসাম খান। চিৎকার তখনও তার থামেনি। এটা আমি সইতে পারলাম না। পাশবিক হিংস্রতা যদি তার মধ্যে থাকতে পারে, তবে মীমাংসার খাতিরে শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণ কি শুধু আমারই জন্যে? ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় শুধু কি তারই একচেটিয়া অধিকার? না, এ অন্যায় অবিচার আমি সইতে পারব না। আমার মুখ কঠিন হল। বাহু দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হল। চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা। আসাম খান ভয়ঙ্কর ঢেউয়ের মতো ফুঁসে উঠে, অশ্রাব্য ভাষায় আমাকে গালি দিতে দিতে এগিয়ে আসতে লাগল। আমার বাবা-মার সম্পর্কেও ছেড়ে কথা কইল না। পারলাম না। আমি কিছুতেই আর সহ্য করতে পারলাম না। আসাম খানের আচরণ আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। আমাকে যা বলার বল। বাবা-মা কি দোষ করেছে?
আসাম খান এবার উঠোন থেকে একটা লাঠি তুলে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। চাচা যে স্কেলে চিৎকার করছিল আমি তার চাইতেও উঁচু পর্দায় চেঁচিয়ে বললাম-খবরদার। আর এক পাও যদি আপনি আমার দিকে এগিয়েছেন, তবে আপনার পা দুটো আজ আমি ভেঙে চুরমার করে দেব। আমি আফগানিস্তানের মেয়ে নই। পরাজয়ের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে শিখিনি। অন্যায়, অত্যচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো শিক্ষা আমি পেয়েছি।
আসাম খান মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর লাঠি ফেলে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। আমি কতক্ষণ যে একভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। জাম্বাজের ডাকে আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। বাড়ির সবাই আমার সাহস ও কাঠিন্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক।
জাম্বাজ বলল, এতদিনে এমন একজনকে পেয়েছি যে, আসামের বিরুদ্ধে লড়বার মতো ক্ষমতা রাখে। আমার এই এক অদ্ভুত চরিত্র। একবার যেটা আমি অন্যায় বা অবিচার বলে মনে করবো জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা ন্যায়ে পরিণত হবে না। কোনও কারণে কাউকে যদি আমি ঘৃণা করি, তবে তাকে আর কোনওদিন ভালবাসতে পারব না। তাকে আমার মনোভাব বুঝতে দেবো না। সুন্দর, সহজ ব্যবহার করব তার সঙ্গে।
এই ঘটনার মাস খানেক পরে আমরা আলাদা হলাম। আমার শাশুড়িও মারা গেলেন। তিনি বহু বছর ধরে অসুখে ভুগছিলেন। আসাম খান কোনওদিন তার চিকিৎসা করেনি। বিনা চিকিৎসাতে রোগ আরো বেড়ে গিয়েছিল। যাদের স্বামী নেই, ছেলেরা ছোট, রোজগার করে না তাদের দুঃখের সীমা নেই। আমার শাশুড়িও সেই অসহায় অবস্থার শিকার হয়েছেন।
পুরনো বাড়ি আসাম চাচা ও জ্যেঠশ্বশুরের ভাগে পড়েছে। আমাদের ভাগে কেবল জমিটুকু ও আঙুরের বাগান। আমার মেজো জা তখন নতুন। তাই বাড়ির সব ব্যাপারে আমাকেই যা করবার করতে হতো। নতুন বৌ বাইরের লোকের সামনে আসবে না। অতএব, জনমজুরদের খেতে দেওয়া থেকে শুরু করে মেহমানদের সেবাযত্ন করা- সব আমাকেই সামলাতে হতো। আমার সর্বত্র যাতায়াতের ছাড়পত্র ছিলো। এমনি একটা সময়েই খবর এসেছিলো যে আমার ননদের টিবি হয়েছে। তার বাড়ি পাকিস্তানে। তাকে দেখতে যাবো বলে আমি ও জাম্বাজ পাকিস্তানে রওনা দিলাম। পাকিস্তান যাওয়ার কথা শুনে সবাই বাধা দিয়েছে। কারণ আমি নাকি আর ফিরে আসব না। জাম্বাজের এক দূর সম্পর্কের চাচা, গুলাম চাচা বলেছিল, সাহেবকামাল যদি আবার ফিরে আসে; তবে আমি নিজের বৌকে জাম্বাজের হাতে তুলে দেব। অপূর্ব! চাচা হয়ে সে তার বৌকে ভাইপোর হাতে সম্প্রদান করবে! এর চেয়ে সুন্দর শর্ত আর কিই বা হতে পারে?
১৯৮৯-এর সপ্টেম্বরের চৌদ্দ তারিখের ভোরে আমরা কারুর কথায় কান না দিয়ে একটা জিপে করে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা সোজা যাব আঙুরহাটা। পাকিস্তানে যাওয়ার তো এই একটাই রাস্তা বর্তমানে খোলা। আঙুরহাটা থেকে যাবো দেরা। ওখান থেকে বাস ধরে করাচি। করাচিতে গিয়ে মুসার কাছে ফোন করে টাকা আনাব। তারপর পাকিস্তানি ট্রেন ধরে যাবো রাওলপিন্ডি। পিন্ডির আলিপুরেই থাকে আমার ননদ। আমাদের জিপ রুক্ষ-শুষ্ক পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছুটে চলেছে। দুধারে বড় বড় পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। সেই উদ্ধত মাথাকে মুহূর্তের জন্যেও নত করার ক্ষমতা কারুর নেই। তারা যেন স্বেচ্ছায় নিজেদের কোল ঘেঁষে এক ফালি রাস্তা করে দিয়েছে গাড়ি চলাচল করার জন্য। ওদের ভাবটা এই যেটুকু দিয়েছি তাই নাও, আর চেয়ো না। নইলে সর্বনাশ। যা দিয়েছি তাও কেড়ে নেব।
অনেকটা পথ পার হয়ে আসার পর পল একটা পাহাড়ি ঝরনা। ঝরনার জলের ওপর দিয়েই গাড়ি যাচ্ছে। জলের নিচে কাদা নেই, আছে বালি ও ছোট ছোট পাথর কুঁচি। এই জলের ওপরেই গাড়ি থামল। একে একে সবাই গাড়ি থেকে নামল। আমিও নেমে ঝরনার স্বচ্ছ জল চোখে মুখে দিলাম। আমি ছাড়া সবাই ঝরনার জল অঞ্জলি ভরে পান করল। তারপর আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। আবার সেই চলা। সীমাহীন এক ভালো লাগা। আমার মনের ভেতরটা কাপের রং-এর সব রং-এ রেঙে উঠল। রবি ঠাকুরের একটা গানের কলি মনের ভেতর গুনগুনিয়ে উঠল-হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে দে রে। যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দেরে। একবার নয় বারবার গানটা মনে মনে ভেজেছি।
একটু পরে রাস্তার থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে ভয় করতে লাগল। এতক্ষণ খেয়ালই করিনি আমরা নিচ থেকে অনেক অনেক ওপরে উঠে এসেছি। এবার গাড়ি আরো ওপরে উঠছে, পাহাড়ের কোল ছেড়ে চড়াইয়ের রাস্তা ধরল। সে কি যেমন তেমন চড়াই? কত ওপরে গাড়ি উঠেছে তা আমি ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না। এখান থেকে নিচের দিকে তাকালে, বুকের ভেতরটা শূন্য হয়ে যায়। পাহাড়ি গাছগুলোকে দেখে মনে হয় ওরা যেন পাহাড়ের অলঙ্কার। পৃথিবীর আলোয় তাদের সবে জন্ম হল। কোনও এক জ্যোত্সা-স্নাত রাতে অথবা ভোরের মিষ্টি হাওয়ায় এরা চোখ মেলেছে। আমরা প্রায় আঙুরহাটার কাছে এসে পড়েছি। দূর থেকে বিশাল একটা মসজিদের চূড়া দেখা যাচ্ছে। আফগানিস্তানে শহর ছাড়া অন্য কোথাও কোনও ভালো হোটেল নেই। জঙ্গলে বা পাহাড়ি পথের ধারে যে সব হোটেল আছে সেগুলোকে ঠিক হোটেল বলা যায় না। পান্থশালা বা ধাবা টাইপের। ভীষণ নোংরা। মেয়েদের থাকার কোনও আলাদা ব্যবস্থা নেই। একটা করে চাটাই পাতা। তার ওপর একটা তোষক দেওয়া। একটা লেপও দেয়। যখন লেপ বা বালিশ ব্যবহার করতে করতে ময়লা হয় এবং মনে হয় কাঁচা দরকার তখন তুলো বার করে খোলটা কেচে দেয়। এই সব হোটেলে যাতে রাত কাটাতে না হয়, সে জন্যে চালক এতক্ষণ প্রাণপণে গাড়ি চালিয়েছে যেন রাতের আগেই আঙুরহাটায় পৌঁছানো যায়। আঙুরহাটার হোটেল পান্থশালার থেকে একটু পদের।
গাড়ি দাঁড়াল। আঙুরে পৌঁছে গেছি। রাতে এখানেই থাকতে হবে। একটা হোটেলের ব্যবস্থা করতে গেল জাম্বাজ। একটু পরে ফিরে এসে আমাকে বলল, চল, রাতের মতো মাথা গোঁজার একটা ব্যবস্থা করেছি। হোটেল তো নয়! যেন স্টোর রুম। এক ফালি জায়গা। সেই ফালি জায়গাটুকুতে শুয়ে রাত কাটাতে হবে। লেপ ও তোষক থেকে বোটকা গন্ধ বেরুচ্ছে। যস্মিন দেশে যদাচার। অতএব, ওর মধ্যেই শুয়ে পড়লাম। সারাদিনের ক্লান্তিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। সকালে জাম্বাজ ডেকে তুলল। আবার চলা। এবার জিপ নয়, একটা টয়টো গাড়িতে চাপলাম। ড্রাইভারের পাশের দুটো সিটে আমরা বসলাম। হেলে দুলে গাড়ি চলতে শুরু করল। টয়টোর পিছনে আরো অনেক লোক বসেছে। মহিলা আমি একা।
শত সহস্র দামামা যেন আমার বুকের মধ্যে বেজে উঠল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজ আমি আবার গাড়ি চেপে বাইরের জগতে পা রেখেছি। এই মুহূর্তে মন আমার কী চাইছে, কোনটা স্পর্শ করার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে তা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আগে যে কোনটা করবো তাও ঠিক করতে পারছি না। বাবা ও মার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলব? নাকি অন্য কিছু! এক বছরের পর আরো তিন মাস পার হয়ে গিয়েছে। ওদের কাউকে আমি দেখিনি। কথা বলিনি। কারো কোনও খবরও আমি জানি না। কাবুল থেকে যদি কখনও কেউ কলকাতায় যায় তবে ক্যাসেট করে পাঠাই আমি। আর কলকাতা থেকে যদি কেউ আসে, তবে আমার বাড়ির ক্যাসেট আনে। তবে সংখ্যায় কম।
গাড়ির একটানা বিকট হর্নের শব্দে আমার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। সামনেই একটা বাঁক। সেই বাঁকে দুটো গাড়ি পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে না। তাই হর্ন দিয়ে একপক্ষ অপরপক্ষকে দাঁড় করায়। বেলা বারোটার সময় একটা শহরে পৌঁছলাম। সেখানে খাওয়া সেরে অন্য একটা গাড়িতে করে রওনা দিলাম।
আমি দুচোখ ভরে দেখতে লাগলাম পাকিস্তানের মনোরম দৃশ্য। বিরাট বিরাট পাহাড়ের কোলে অসংখ্য কুঁড়ে ঘর। সারি সারি পাথর দিয়ে তৈরি সাজানো সিঁড়ি পাহাড়ে ওঠার। মুগ্ধ নয়নে আমি ওদের জীবনযাত্রা দেখছিলাম। কোথাও একদল মেয়ে ঝর্নার জলে কাপড় কাঁচছে। কেউ বা তাদের ছাগল চরিয়ে বাড়ি ফিরছে। আসন্ন সন্ধ্যা তাদের মনে করিয়ে দিয়েছে, দিনের শেষ। রাতের অন্ধকার এবার পৃথিবীকে গ্রাস করতে আসছে। পালাও সবাই যে যার ঘরে। ঘণ্টা দুয়েক পরে আমরা পৌঁছলাম ওয়ার্না বলে একটা শহরে। এখানেই রাতে থাকতে হবে। এখানে রাতে গাড়ি পাবো না। এখন সন্ধে সাতটা বাজে।
সত্যি কথা বলতে কি, আমার কোথাও আর থামতে ইচ্ছেই করছিল না। বার বারই মনে হচ্ছিল এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো? শুধু চলা আর চলা। কিন্তু ম্যান প্রোপোজেস, গড ডিসপোজেস। তাই চলা থামল। আমরা রাত কাটাবার জন্যে, জাম্বাজের এক পিসির বাড়িতে গেলাম। বিরাট পাহাড়ের কোলে তার বাড়ি। ঠিক বাড়ি বলতে যা বোঝায় তা নয়। ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘর। এরা প্রত্যেকে আফগানিস্থান থেকে আসা শরণার্থী। রাতে এখানেই থাকতে হবে।
১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে সম্ভবত রাশিয়ান বাহিনী আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। যদিও ১৯৭৯-র আগেও এদেশে অনেক বার যুদ্ধ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে। কত গ্রাম শহর যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যুদ্ধের বিভীষিকা এবং ধ্বংসাত্মক কার্যাবলি সম্বন্ধে কাবুলের প্রত্যেক মানুষ সচেতন। কিন্তু ১৯৭৯-র যুদ্ধে দেশের মানুষ দলে দলে দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৭৯-র আগে শুধুমাত্র সৈন্যদের মধ্যেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ নাগরিক ও সুদূর পল্লীগ্রামের মানুষ যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন ছিল। পরবর্তী সময়ে জাতীয়তাবাদের হিড়িকে দেশের সমস্ত মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৯-র যুদ্ধে দেশের সমস্ত জনবল ও অর্থবল যুদ্ধের জন্যেই নিয়োজিত করা হল। আফগানিস্থানের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সম্পর্কে আমি আগে একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু আমার শাশুড়ি আমাকে দেশের খুঁটিনাটি সব ব্যাপারই খুলে বলেছেন। তার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী। তার মুখে শোনা ঘটনাকেই যতদূর সম্ভব মনে রেখেছি। জাহির শা যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন দেশে শান্তি ছিল। গঠনমূলক কর্মতৎপরতার জন্যে জনসাধারণের মধ্যে জাহির শা-র যথেষ্ট সুনাম ছিল। কিন্তু তিনিও তো সাধারণ মানুষ ছিলেন। এই সাধারণ মানুষ এক এক সময় এমন ভুলভ্রান্তি করে বসে যা শোধরানো অসম্ভব। সেই রকমই ভুলের মাসুল হিসাবে গদি ছাড়তে হয় জাহির শা-কে। তিনি চোখ অপারেশন করাতে আমেরিকা গিয়েছিলেন। কিছুদিনের জন্যে ভাইপো দাউদ খানকে গদিতে বসিয়েছিলেন। কিন্তু এখানেও সেই বিশ্বাসঘাতকতা। দাউদ আর গদি ছাড়ল না। এরপর ধীরে ধীরে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন নুর মহম্মদ তারাকি।
শুনেছি তারাকি নাকি পীর আজরাত সাহেবের বাড়ি যখন পুড়িয়ে দিয়েছিলেন তখন থেকেই দেশে বিদ্রোহের পদধ্বনি শোনা যায়। এবং আজরাত সাহেবের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার পর তারাকি তার ট্যাঙ্কের পেছনে, দাউদকে বেঁধে মাইলের পর মাইল টেনে নিয়ে যান। আর তাতেই দাউদের মৃত্যু হয়। নিয়মরক্ষার খাতিরে যৎসামান্য মাটি খুঁড়ে, তাতেই দাউদকে কবর দেওয়া হয়। এবং তার পরেই তারাকি গদিতে বসেন।নুর মহম্মদ তারাকির পরে গদিতে বসেন পিজলামিন। পিজলামিনের পরে বাবরাক কারমাল। অতঃপর গদি দখল করেন ডঃ নাজিবুল্লা। নুর মহম্মদের শাসন কালে আফগান জনগণ তাকে ধিক্কার দিত। পরে আরো পরে পারস্পরিক বিরোধিতার মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন হন পরপর আরো অনেকে। তারাকির সময়েই কাবুলে প্রবেশাধিকার পায় রাশিয়ানরা। অন্যদিকে আর এক প্রতি বিপ্লবের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল। আফগানিস্তানের একশ ভাগের নব্বই ভাগ মানুষ তাদের নতুন বিপ্লবী মুজাহিদদের কীর্তিতে মুগ্ধ মনোভাব প্রকাশ করতে লাগলো। আম জনতা ভাবল– কি বহুমুখী কর্মশক্তি? কি অপূর্ব দুঃসাহস ও বীরত্ব। নতুন বিপ্লবী মুজাহিদদের স্বার্থ ত্যাগের এবং বীরত্বের এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় বোধহয় আর নেই।
কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই জনতার ভুল ভাঙল। তারা বুঝল, শান্তি আর কোনও দিনই ফিরে আসবে না। কেউ কেউ ভাবত নাজিবুল্লা তো দেশের জন্যে ভালোই করতে চাইছেন। দেশকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোয় উদ্ভাসিত করতে চাইছেন। স্কুল, কলেজ তৈরি করে শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে চাইছেন। মেয়েদেরও অনুমতি দেওয়া হল সেই স্কুলে ও কলেজে গিয়ে শিক্ষাদীক্ষায় নিজেদের গড়ে তোলার। অফিসে, দোকানে মেয়েরা কাজ করতে শুরু করল। এমনকি এয়ার হস্টেসের চাকরি করেও অনেক মেয়ে সংসারের গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারছিল।
১৯৭৯-র পর থেকে শুরু হয়েছিল বিভীষিকার দিন–আতঙ্কের রাত। যে সব খ্রিস্টান কর্মসূত্রে আফগানিস্তানে থাকত, তাদের ওপর চলল অকথ্য অত্যাচার। মুজাহিদরা তাদের বলত–ব লা ইলাহা ইল্ললা, মহম্মদীন রসুল আল্লা। পৃথিবীর কেউই ধর্মীয় সংস্কার মুক্ত না। তাই খ্রিস্টানরা, মুসলিম কলেমা বলত না। আমার মনে হয় না, কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করলেই মুসলিম হওয়া যায়, অথবা ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেন্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি….. এই মন্ত্র বললেই হিন্দু হওয়া যায়? মনের শুচিতা, অধ্যাত্মবোধ, শালীনতা, সংযম–এগুলির কি দরকারই নেই? যাই হোক কলমা না বললে মুজাহিদরা ওদের মতে বিধর্মীদের নির্মমভাবে হত্যা করত।
সে এক নারকীয় পরিস্থিতি। আনাচে, কানাচে, খানায়, খন্দরে অসংখ্য লাশের পাহাড়। জলের খরস্রোতে ভেসে যাওয়া সেই সব লাশ, ধড়হীন, মুণ্ডুহীন মানুষের ছিন্ন দেহ, ট্রাক্টরে করে নিয়ে গিয়ে দূরে বহু দূরে, পাহাড়ের গায়ে কোথাও ফেলে দিয়ে আসত। ঘরে ঘরে কায়েম হল আতঙ্ক আর সন্ত্রাসের রাজত্ব। রাশিয়ানরা হেলিকপ্টারে করে এসে বোম ও মিসাইল হেনে যায়। দাড়িওয়ালা লোক দেখলেই মেরে ফেলে। গজনী, গড়দেশ, মুশখেল, পাতানা, সারানা, মমদকেল, কাটোয়াজ, তামির, আলেকদারি এই সব এলাকা মুজাহিদদের কবলে চলে এলো। নাজিব অনুগামীদের ধারণা আফগানিস্তানের উন্নয়ন ও বিকাশের পরিপন্থী এই সব মুজাহিদরা। ১৯৯০ অথবা ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ। নজিবের সামনে তখন দুটো রাস্তা হয় যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ। নতুবা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ। যে পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে–তাতে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়াই উচিত বলে মনে করলেন নাজিব। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সঙ্গেই, তিনি তার পরিবারের সবাইকে দিল্লিতে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। আত্মসমর্পণের শর্ত হিসাবে নিজের মুক্তির আবেদন রাখলেন। অতঃপর কাবুলের এয়ারপোর্টে প্লেনে উঠে কাবুল ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বন্দী হলেন ডঃ নাজিবুল্লা। চমকে ঘটে গেল এই অপ্রত্যাশিত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। নাজিবুন্নার আফগানিস্তান এবার এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করল। যার আশু পরিণাম আর যাই হোক না কেন, ইতিহাসের পাতায় নৈরাজ্যের আর একটা নতুন দৃষ্টান্ত যে হবে, তাতে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ রইল না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইরান, ইরাক, আরব প্রায় সমস্ত দেশেই গোটা ব্যাপারটা নিয়ে চলল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও সমীক্ষা।
মুজহিদদের হাতে ডঃ নাজিবুল্লা বন্দী হলেন। কিন্তু যুদ্ধ বিরতির কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। তাই শরণার্থীরা পাকিস্তান থেকে নিজের দেশে ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করল না। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক্ আফগান শরণার্থীদের স্বার্থে নিজের দেশে ক্যাম্প করার জন্যে অনেক জায়গা দিয়েছেন। আফগানবাসীদের কাছে জিয়াউল হক এক মহান ব্যক্তি। মানবিকতার প্রতীক। আফগান শরণার্থীরা পাকিস্তানে গিয়ে কোনও রকমে একটা করে কুঁড়েঘর বানিয়ে বাস করছে। আকুল অপেক্ষায় আছে, কবে তাদের নিজেদের দেশে শান্তি ফিরে আসবে। কবে তাদের নিজেদের স্বদেশে ফিরে যেতে পারবে। আমি ভেবে পাই না কী আছে ওদের দেশে? কীসের আকর্ষণে তারা এই সুন্দর, স্বচ্ছল দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায় নিজের দেশে? ওই কাদা মাটির পাথুরে দেশের জন্যে এরা কেন এত ব্যাকুল? বছরের ছমাস কাটে তুষারের প্রাণহীন শুভ্রতায়। হাজার খুঁজেও সবুজের বিন্দুমাত্র সন্ধান পাওয়া যায় না। আর সেও কি একটু আধটু তুষারপাত? এক এক দিন ভোরে উঠে ঘরের বাইরে পা রাখার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। পুরো চার মাস তুষারপাত হয়। আর ওই চার মাস সবাইকে ঘরে প্রকৃতপক্ষে বন্দী হয়ে থাকতে হয়। গ্রামের রাস্তায় কোনও গাড়ি চলে না। তবে কাবুল শহরের কথা বলতে পারব না। কারণ, তুষারপাতের সময় আমি শহরে যাইনি। খাদ্যশস্য সব নভেম্বরের আগেই ঘরে তুলে নিতে হবে। গম, চিনি গুড়, আলু, পেঁয়াজ। এছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। আর আছে মাংস। কেউ চারটে, কেউবা ছটা দুম্বা ভেড়ার মতো দেখতে, তবে ভেড়া নয়। তাকে ওরা দুম্বা বলে। আমাদের দেশেও কয়েকটি জায়গায়, দুম্বা পাওয়া যায় জবাই করে সরু সরু ফালি করে কেটে দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়। মাংস ঝোলাবার জন্যে সবার বাড়িতে আলাদা একটা করে ঘর আছে। তুষারের ঠাণ্ডা হাওয়ায় সেই মাংস শুকিয়ে যায়। এবার সারা শীত ধরে সেই শুকনো মাংস সবাই খাবে। এই শুকনো মাংসকে এরা লান্দাই বলে। আর আছে, দুধ, ঘি, মাখন, দই। গরু সবার বাড়িতেই দুটো-তিনটে আছে। গরু যদি কারো না থাকে তবে দুধ, ঘি থেকে তারা বঞ্চিত।
এই দেশই নাকি ওদের স্বর্গ। অবশ্য, নিজের দেশ সবার কাছেই স্বর্গ।
জাম্বাজের পিসি আমাকে স্বাগত জানাল। প্রথমে ত্যারে মাইসে, হ্যান্ড সেকের মতো তারপর কোলাকুলি করল। এরা গালে চুমা দেয় না। পার্শিবানরা চুমা দেয়। তারপর বলল। সারাইয়ে? কেমন আছো। আমি উত্তর দিলাম। ক্ষাইয়াম। ভালো আছি। জোরাইয়াম। সুস্থ আছি এসব কথাবার্তায় এখন আমি অভ্যস্ত। বরং এখন কেউ যদি আমাকে স্ক্যারেমাইসে সাংগারাইয়ে না বলে তবে আমি ভেতর থেকে কেমন যেন অপমান বোধ করি। যাই হোক, কোনও রকমে রাতটা কাটিয়ে আবার ভোরে একটা টয়টোয় চেপে রওনা দিলাম দেরার উদ্দেশে। এবার রাস্তা পাকা। রাস্তার দুধারে অসংখ্য বাড়ি। কিছু বাড়ি পাকা আর কিছু কঁচা। রাস্তাটাও বেশ চওড়া। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা চেক পোস্ট পড়ল। আমি মনে মনে একটু ভয় পাচ্ছিলাম। কারণ এটা পাকিস্তান। আমি হিন্দুস্থানি। যদি আমার পাসপোর্ট চায়? পরে বুঝলাম এখানে আমার পাসপোর্ট স্বয়ং জাম্বাজ। আকাশি রংয়ের জামা ও খাকি প্যান্ট পরা পুলিস জাম্বাজকে জিজ্ঞেস করল- হিন্দিতে
–কোথা থেকে আসছ? শহর না গ্রাম?
–গ্রাম, সারানা থেকে।
আমাকে দেখিয়ে বলল, এ কে? পুলিশটার নজর আমার দিকে।
–আমার বিবি। জাম্বাজের কথাটা বোধহয় সে বিশ্বাস করতে পারল না।
–তুমি তো পাঠান। আর এতো পাঞ্জাবি বলে মনে হচ্ছে!
-হ্যাঁ। আমার বিবি হিন্দুস্থানি।
–বিয়ের কাগজ আছে? দাও। বলে হাত বাড়াল পুলিশটা।
জাম্বাজ আমাদের বিয়ের কোর্ট পেপারটা দেখাল। তারপর ছাড়া পেলাম। এবং প্রায় এক ঘণ্টা পর আমরা দেরায় পৌঁছে গেলাম।
আমরা একটা দুরন্ত গতির গাড়িতে করে যাচ্ছি–যাকে ওরা বলে প্লাংকোচ। নামব করাচি। সেখানেই শেষ হবে ছদিনের চলা।
পঞ্চম অধ্যায়
জীবনের অনেকটা সময় আমি যেন পিছনে ফেলে এসেছি। নতুন করে যেন সব দেখছি রাস্তা-গাছপালা আর সভ্য জগতের শিক্ষিত, মার্জিত মানুষ দেখে অবাক হয়ে যেতে লাগলাম। আমি আবার পৃথিবীর নতুন আলোয় আলোকিত হলাম। সত্যি, আফগানিস্তানে মেয়েরা সব দিক থেকে কত বঞ্চিত। এই পৃথিবীতে ওদের জন্ম শুধু দাসীবৃত্তি করতে। জগতের যত কিছু সুন্দর জিনিস তা শুধু আফগান পুরুষরাই ভোগ করবে। মাঝে মাঝে আমার মনে হতো, সবার ঘরে গিয়ে প্রতিটি মেয়েকে বলি, তোমরা অন্ধকার জগতে মুখ লুকিয়ে থেকো না। বেরিয়ে এস এই দিনের ঝলমলে আলোয়। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করো। সবাইকে বুঝিয়ে দাও তোমরা শুধু নারী নও, মানুষও বটে। এও ভাবি, বলেই বা লাভ কি? যুগ-যুগান্তর ধরে, যে কুসংস্কারচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থা সমগ্র পৃথিবীতে চলে এসেছে তার কতটুকুই বা পরিবর্তন করা যায়?
জাম্বাজ অনেকক্ষণ ধরে আমাকে ডাকছে আমি খেয়াল করিনি। খেয়াল হতে দেখলাম আমরা আলিপুরে এসে গেছি। পাকিস্তানে আসার পর থেকেই আমি লক্ষ করছি মেয়েরা একা একাই যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনও পুরুষ তাদের সঙ্গে নেই। কাবুলে থাকতে থাকতে আমি ওদের রীতিনীতিতে ভুলেই গিয়েছিলাম মেয়েরাও একা একাই ঘোরাফরা করতে পারে। একমাত্র কাবুলেই দেখলাম মেয়েরা সর্বত্রই পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। এমনকি একা মেয়েকে কেউ গাড়িতেও তুলবে না। কাবুলে অনেক বাঙালি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, যারা জীবনের রঙ্গিন স্বপ্ন দেখে এখানে এসেছে। তাদের মধ্যে কাকলি তো আছেই। আর আছে জোবেদা, নুরজাহান, কমলা, যশোদা, হারানি, সবিতা, মানসী ইত্যাদি। এদের মধ্যে হারানি বুড়ি হয়ে গিয়েছে। জোবেদা তার চার মেয়েকে নিয়ে অনেক কষ্টের মধ্যে। জীবন কাটাচ্ছে। নুরজাহান ছিল খ্রিস্টান মেয়ে, লরেটোতে পড়ত। ওর বাবার নাকি সোনার দোকান ছিল। এরা জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবে কাবুলেই। এদের কেউ এখন আর স্বপ্ন দেখে না। আমার মতো এত ভাবনাও ভাবে না। দুর্জয় সাহসও ওদের নেই। এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই বাস থেকে নেবে আমরা বাঁ হাতের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছি। অপূর্ব জায়গা। রাস্তার দুধারে লাইন করা ঝাউ গাছ। যে পাকিস্তান আমার কাছে একটা ভয়ের দেশ ছিল আজ সেই পাকিস্তানের মাটিতে বিনা বাধায় আমি হেঁটে চলেছি। পাকিস্তানের প্রতি বরাবরই আমার একটা ঘৃণার ভাব ছিল। সব সময় একটা অবহেলার মনোভাব পোষণ করতাম। ভাবতাম ইয়াহিয়া খান আর ভুট্টো যে দেশের মানুষ, সে দেশ কোনওতেই ভালো হতে পারে না। ১৯৬৯ অথবা ১৯৭০ হবে। আমি তখন চিত্তরঞ্জনে, আমার কাকার বাড়িতে থাকতাম। ওখানেই সেন্ট জোসেফ কনভেন্টে আমি পড়াশুনা করতাম। তখন আমাদের পাড়ায় কালি পুজোর সময় যাত্রা হতো। সে বার একটা যাত্রা দল, যে পালা করেছিল সেই পালাতেই দেখেছিলাম, অত্যাচারী ইয়াহিয়া খানের চরিত্র আর ভুট্টোর অসভ্যতা ও অত্যাচার। কী ভয়ঙ্কর ছিল সেই চরিত্র দুটোর চেহারা। ওই যাত্রা দেখে আমি ভয়ে দাদুর কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ছিলাম। তারপর থেকেই মনে হতো, পাকিস্তান মানেই ভয়ঙ্কর। আমরা নির্জন রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি। আজ আমার মন ভীষণ ভালো। এই মুহূর্তে আমি সমস্ত ঘৃণা সংস্কার ভুলে গেলাম। পৃথিবীতে যাবতীয় আচার বিচার, ন্যায়-অন্যায় সব ভুলে আমি মিশে গেলাম প্রকৃতির মধ্যে। যতই এগিয়ে যেতে লাগলাম ততই আমি অবাক। রাস্তার ডানদিকে, বাঁ দিকে বিশাল গমের ক্ষেত। সে দিকে তাকালে মনে হয় প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য এই ক্ষেতে এসেই যেন বণবৈচিত্র্যের আসন পেতেছে। সবুজ ও বাদামি রং-এর কী অপূর্ব বাহার।
আমরা আমার ননদের বাড়ি পৌঁছে গেছি। আমাদের দেখে বাড়ির ভেতর থেকে ননদ গুনচা, বেরিয়ে এল। আমাদের অভ্যর্থনা করল। তারপর ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসাল। আর একজন বৌ আমাদের জন্যে চা নিয়ে এল। আমি গুনচার ঘরের ভেতরটা দেখছিলাম। ঘরের সর্বত্র একটা গরিবি ভাব। আমরা যার ওপর বসে আছি সেটা স্পঞ্জের নয়, তুলোর গদি। বেশ শক্ত। শুনেছি আমার নন্দাইয়ের ছোট্ট একটা মশলার দোকান আছে। আর তার দুই ভাইয়ের কাঠের কারবার। যা রোজগার হয়, তাতে কোনও মতে দিন চলে যায়। বাড়তি শখ মেটে না, শখ ওদের কাছে বিলাসিতা। আর সংসারও তো ছোট নয়। ননদের বড় জায়ের ছটা ছেলে, পাঁচটা মেয়ে। ছোটো জায়ের দুই মেয়ে এক ছেলে। আর আমার ননদের তিন মেয়ে, এক ছেলে। বড় মেয়ে আবার বিকৃত মস্তিষ্ক।
খুব ক্লান্ত লাগছিল, তাই আমি আধশোয়ার মতো করে শুয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি কে জানে। নন্দাইয়ের ডাকে উঠে পড়লাম। নন্দাইয়ের নাম রম্পাজান। তার বড় ভাইয়ের নাম জমিল। ছোটো ভাইয়ের নাম কালামন্দার। জমিলের বিবির নাম জোহরা। কালামন্দারের বিবির নাম রশীদা। কথা বলতে বলতে রাত অনেক হয়েছিল। গুনচা এবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করল। রুটি আর মাংসের কোরমা খেয়ে ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিলাম। ভোর পাঁচটায় গুনচা চা, নাস্তা নিয়ে এল। মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে ওঠে। কারণ সূর্য ওঠার আগে তারা নামাজ পড়ে। যদিও আমাদের হিন্দু জাতের, শুধু তাই বা কেন প্রায় সমস্ত ধর্মের লোকই ভোরে ওঠে। তবে মুসলিম ধর্মের একটাই বিশেষত্ব আছে তা হল ঘুম থেকে উঠে সবাই বাথরুমে যায় এবং তারপর অজু বানায়। কাবুলে অজুকে আবদ্দাস বলে। অজু মানে পবিত্র হওয়া একটা বড় মগে জল নেবে। তারপর মুখের ভিতর জল নিয়ে তিনবার কুলকুচি করবে। এই ভাবে তিনবার করে হাত পা ধুয়ে অজু বানাবে। এরপর বলবে,-খোদা আমি পবিত্র হয়ে নামাজ পড়ার জন্যে অজু বানালাম। আর যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে রাতে মিলন হয়, তবে রাত থাকতে উঠে তাদের স্নান করতেই হবে। স্নান না করে নামাজ তো দূরের কথা, কোন জিনিসেও হাত দিতে পারবে না। এই হলো তাদের বিশেষত্ব।
ভোরে নামাজ পড়ার পর মেয়েরা, রান্না ঘরে ঢোকে। শুরু হয় মেয়েদের দৈনন্দিনের জীবনযাত্রা। গুনচা আমাদের নাস্তা দিয়ে চলে গেল। আমি নন্দাইয়ের সাথে যাব ডাক্তার দেখাতে। অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম একটা ভালো গাইনোকোলজিস্ট-কে দেখাব। পাকিস্তানে যখন এসেইছি তখন একবার দেখিয়ে যাওয়াই ভালো। নন্দায়ের সাথে গেলাম ডাঃ W. E. Hassan- এর নার্সিংহোমে সেখানে নাম লিখিয়ে অপেক্ষা করছি। চার-পাঁচ জন রুগীর পর আমার ডাক পড়ল। দরজা দিয়ে ঢুকে ডানদিকে ডাঃ বসে আছেন। তার সামনে একটা টেবিল, টেবিলের উল্টোদিকে একটা চেয়ারে আমি বসলাম। ডাঃ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,
–তোমার কী অসুবিধা হচ্ছে বলল? সব হিন্দিতে কথা হচ্ছে।
–আমার একটু…অসুবিধে হচ্ছে।
ডাঃ কী বুঝলেন কী জানি? সোজা হয়ে বসে প্রশ্ন করলেন,
–বিবি, তুমি তো পাঠান নও! পাকিস্তানিও নও? কোথা থেকে আসছ?
-–আমি ইন্ডিয়ান। পাঠানকে বিয়ে করেছি। সেই সূত্রেই আজ পাকিস্তানে আসার সুযোগ পেয়েছি।
–তুমি মুসলিম না হিন্দু? ডাঃ বড় বড় চোখে আমার দিকে দেখলেন।
–হিন্দু। কেন? হিন্দু হলে কি আপনি চিকিৎসা করবেন না?
–এমন কথা আমি তো বলিনি?
উনি আমাকে পরীক্ষা করে লেপস্কপি করতে বললেন। তার আগে একটা বুকের এক্সরে করে নিতে বললেন। আমাকে প্রেসক্রিপশান দিলেন, আর একটা ঠিকানা দিলেন, যেখানে গিয়ে আমাকে এক্সরে করাতে হবে। ঠিকানাটা আমি পড়লাম। DEPARTMENT OF PATHOLOGY. ARMY MEDICAL COLLEGE, ABID MAJID ROAD. RAWALPINDI CANTT. [PAKISTAN]। সেদিনই ঠিকানাটা নিয়ে এক্সরে করার জন্যে আর্মি মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি ডিপার্টমেন্টে গেলাম। সেটা একটা চারতলা বাড়ি, কাঁচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। কাউন্টারে স্লিপটা দেখিয়ে বাঁদিকে কয়েকটা সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নামলাম। ডানদিকে ঘুরে বাঁদিকে গিয়ে, ডানদিকের একটা ঘরে ঢুকলাম। প্রেসক্রিপশান জমা দেওয়ার পর আমাকে ডাকল। একটা কাঠের ওপর উঠে আমাকে দাঁড়াতে বলল। গলার চেন, ব্যাগ, চশমা ইত্যাদি আমি একটা চেয়ারের ওপর রাখলাম। তারপর আমি নিশ্বাস টেনে ধরলাম। এক্সরে হওয়ার পর বেরিয়ে এলাম। কিছুটা যাওয়ার পর আমার খেয়াল হল গলায় চেন নেই। আমার মনে পড়ল আমি, ব্যাগ চশমা তুলেছি কিন্তু চেনটা তুলিনি। সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে গেলাম এবং ওই রুমের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাস করলাম। তিনি স্রেফ অস্বীকার করলেন। বুঝে গেলাম এরাই নিয়েছে। চেনটা কলকাতায় B.C. Sen-এর দোকান থেকে কিনেছিলাম। কলকাতা আমার দেশ। জন্মসূত্রে আমি পেয়েছি সেই দেশকে। আমার মাতৃভূমি। আমার আসল ঠিকানা। এই কঠিন বাস্তবের মধ্যে দাঁড়িয়েও আমার মনে পড়ে সেই ছোট্ট বেলার মধুর সব ঘটনা। মায়ের সেই বকুনি।
–দাঁড়া, বাবা এলে বলে দেব। এটা করিস না; ওটাতে হাত দিস না। ভাইকে মারিস না। বাবাকে বলে দেব। না পড়লে বলে দেব, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বলে দেওয়ার ভয়ে আমি যেন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। আর শুধু ভয় দেখানো নয়-মা সত্যিই বলে দিত। তখন আমার পিঠে পড়ত বেতের বাড়ি। তবুও আমি কি দমে যাওয়ার মেয়ে? বেত যত খেতাম শয়তানি তত বাড়ত। এরই মধ্যে, স্কুলের গন্ডি পেরোলাম। কিন্তু শয়তানি কমেনি। মার খাওয়াটাও বেড়েছে।
একবার আমরা চার বন্ধু মিলে চলে যাচ্ছিলাম মুম্বাই। সিনেমার নায়িকা হব। কিন্তু মুম্বাই পর্যন্ত আর যেতে হয়নি; হাওড়া থেকে পুলিশ কান ধরে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আর একবার ঠিক এমনই বিপদে পড়েছিলাম।
১৯৭২ সালের ঘটনা। এর ঠিক দুবছর আগে মোজো কাকা ও কাকিমা পুরী গিয়েছিলেন। ওদের কাছে পুরীর গল্প শুনে আমার খুব ইচ্ছা করত পুরী যেতে। কিন্তু আমাকে কেউ পাত্তাই দেয় না। এরপর ১৯৭২-এর জুলাইতে আমার কাকার ছেলে হয়। সবাই বলতে লাগল পুরীতে মানত করে তবেই ছেলে হয়েছে। পুরী সম্পর্কে এই সব কথা শুনে কার মন চায় ঘরে থাকতে? তবুও আমার যাওয়া হয় না। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। ১৯৭৩-র ফেব্রুয়ারি মাসে আমার ছোটো কাকার বিয়ে হল। আমার তখন সতেরো বছর বয়স। I.S.C.E. শেষ। আমি ভাবলাম চুরি করে না গেলে আমার আর কোনও দিন পুরী যাওয়া হবে না। অথচ তখন আমার কাছে পুরী যাওয়ার মতো টাকা নেই। সুতরাং এখানেও চুরি করার প্রশ্ন। কিন্তু চুরি করব কোথায়? বাবার পকেট থেকে টাকা নিলে নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবো। তাই ঠিক করলাম, আমার হাতে যে বালাটা আছে সেটা বেচে যাবো পুরী। সোনার দাম তখন পাঁচশো টাকা ভরি। কিন্তু সোনা যে কোথায় বেঁচতে হয় তা তো জানি না। এখানেও সেই বাধা। তবু হার না মেনে একটা লোককে জিজ্ঞেস করলাম। লোকটার একটা সজীর দোকান। আমার প্রশ্ন শুনে লোকটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখল। তারপর বলল–আলু পটলের দোকানে সোনা বেঁচতে এসেছেন? তার থেকে এক কাজ করুন–মাছের দোকানে যান। মাছওয়ালারাই আপনাকে রাস্তা বাতলে দেবে। যত্তে সব উটকো ঝামেলা। বাড়ি ফিরে এসেছি। লজ্জায় মুখ নিচু করে।
১৯৭৪। ইতিমধ্যে অনেকটা সময় চলে গিয়েছে। কিন্তু আমার পুরী যাওয়ার ইচ্ছাটা থেমে থাকেনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ইচ্ছাটা আরো জোরদার হয়েছে। কিন্তু যাওয়া হয়নি। দাদু মারা যাওয়ার পর ঠামা তখন বেশির ভাগ সময়টা চিত্তরঞ্জনে গিয়ে থাকে। ঠাম্মা আমাদের এখানে না থাকার জন্যে আর কার কী অসুবিধা হয়েছে জানি না। তবে, আমার সব থেকে বেশি কষ্ট হয়েছে। এই সময়তেই মারা গেলেন আমার ছোটো কাকিমা। ছোটো কাকিমার মারা যাওয়াটা এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি নিয়ে এল আমাদের বাড়িতে। কারণ তিনি একমাসের একটা শিশুকে রেখে চলে গিয়েছেন। এই মেয়ের দুধ গরম করতে গিয়েই সিলিন্ডার বাস্ট করে তার মৃত্যু হয়। তখন সবাইকার একটাই চিন্তা যে শিমুকে কোথায় রাখা হবে। কার কাছে রাখলে শিমুর আদরে কোনও ত্রুটি হবে না। তারপর শুনলাম যে ছোটো কাকার বিয়ে হবে। আমার মনের মধ্যে তখন একটাই চিন্তা, শুনেছি সত্য কখনো ভালো হয় না। যদি শিমুর সম্মাও ভালো না হয়? তবে? সবাইকেই ওই একই চিন্তা যেন পেয়ে বসেছে। যদি শিমুর সম্রা ভালো না হয়? তবুও ছোটো কাকার বিয়ে হল। নতুন কাকিমাও বাড়িতে এল। আমি তখন ছোটো কাকার বাড়িতেই বেশির ভাগটা থাকতাম। নতুন ছোটো কাকিমা আমাকে কতখানি ভালবাসতেন তা আমি জানি না। কিন্তু একটা ব্যবধান তার মধ্যে আমি নিশ্চয়ই খুঁজে পেয়েছিলাম। যে ব্যবধান তার কাছ থেকে আমাকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলো। এই আমার চরিত্রের ভীষণ দোষ। কারো ভালোটা আমি প্রাণ ভরে উপভোগ করতে পারি, কিন্তু মন্দটা কখনোই গ্রহণ করতে চাই না। বা পারি না। সে যেই হোক না কেন। যত বড় স্বার্থই তার সঙ্গে আমার জড়িয়ে থাক না কেন। তবুও বলি আমি–আমি–আমি কারো মতো করে বাঁচতে চাই না। তাই ছোটো কাকিমার ওপর অভিমান করে আমি বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। তারপর খুব কম যেতাম সেখানে। আমার ভীষণ আপন, ভীষণ প্রিয় ছোটো কাকাও আমাদের থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন। আগে ছোটো কাকা আমার ভালোমন্দ সব কিছুর মধ্যেই থাকতেন। বিয়ের পরে আর থাকলেন না। আগে প্রতি বছর মহালয়ার দিন আমারা পুজোর জামা কাপড় কিনতে যেতাম ছোটো কাকিমা আসার পর আর তা হয় না। জামা দেওয়া তো দূরের কথা, পুজোতে আমাদের বাড়িতে দেখাই করতে আসেন না। কিন্তু মেজো কাকিমা আমার আপন। অনেক অনেক অন্যায় করার পরও মা যেমন তার সন্তানকে কোলে তুলে নেয়? মেজো কাকিমা ঠিক তেমনি। আমাদের তার ভালোবাসার রং এ রঙিন করে রেখেছেন। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে। কিন্তু ভাসুরপো ও ভাসুরঝিতে তার ঘর ভর্তি। মেজো কাকিমা বলে তোরা ছাড়া আমার আর কে আছে বল? আমার নিজের তো মাত্র এক ছেলে মেয়ে। তোরাই আমার সব। শুধু আমরা কেন? সবাই তার ভীষণ আপন।
আসলে কিছু মেয়ে আছে, যারা একা থাকতে ভালোবাসে, কিন্তু বোঝে না একা থাকার মধ্যে কোনও মজা নেই। আনন্দ নেই। সুখ? কী জানি একা থাকার মধ্যে কোনও সুখ আছে কিনা। সব মেয়েদের এই একটা জায়গা আছে, যেখানে সে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। স্বামীকে নিজের আঁচলের তলায় রাখতে চায়। নিজের বাবা-মা-ভাই-বোন, সবাইকে ঠিক রাখবে কিন্তু স্বামীর দিকের কারো সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। স্বামীগুলোও কেমন যেন মেরুদণ্ডহীন হয়ে স্ত্রীর আঁচলের তলায় ঘুরঘুর করে। বিয়ের পরে কোনও কোনও পুরুষ নিজস্বতা হারিয়ে ফেলে। কেন পুরুষরা তার স্ত্রীকে এতটা সাহস দেয়? কোর্টের হুকুম হচ্ছে বধুরা যদি নির্যাতিত হয় তবে শাশুড়ি ও ননদের জেল হবে। বধুরা কি শাশুড়িদের নির্যাতন করে না? গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয় না? তার জন্যে কেন কোনও আইন নেই, শাশুড়ি নির্যাতিত হলে বৌদের কোনও শাস্তি হয় না কেন? যাক বধুদের কথা, থাক আমার কথা। আমার প্রাণের বন্ধু ছিল, বুড়ি-টুটুন-বিজয়, শোভন, ট্যাটন, পলি। এদের মধ্যে কেউ আমার সঙ্গে কখনো আড়ি করতে পারত না। আড়ি করলেই বিপদ। আমি সবাইকে কিছু না কিছু রোজ খাওয়াই। তাই আড়ি করলেই বলতাম, আমি তোদের যা যা খাইয়েছি আগে তা ফেরত দে, তারপর আড়ি করবি। সুতরাং আড়ি আর হতো না।
কিন্তু বুড়ি একবার আমার শয়তানি সহ্য করতে না পেরে, আড়ি করেই সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতে পাঁচ পয়সার চানাচুর ধরিয়ে দিয়েছিল। তিনদিন আগেই এই চানাচুর আমি ওকে খাইয়েছিলাম। আজকের এই বাস্তব পরিস্থিতি সেই ছোট্টবেলার স্মৃতিকে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। আমাকে নিঃস্ব, রিক্ত করেছে। রাতারাতি আমি যেন এক ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা হয়ে উঠেছি।
আমার সামনে সাফেসাল মসজিদ। জাম্বাজ বলেছে, এখানেই প্লেন ভেঙে পড়েছিল জিয়াউল হকের। কী যে তার সৌন্দর্য তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মসজিদ চত্বরে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল আমি বোধহয় স্বর্গে পৌঁছে গেছি। আমার কলমের এত জোর নেই যে, সাফেসাল মসজিদের সৌন্দর্যকে ভাষায় প্রকাশ করি। ইসলামাবাদের এই জায়গাটা দেখে আমার মনে হল আমি যেন দিল্লির সফদরজঙ রোডে দাঁড়িয়ে আছি। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। আজ পাকিস্তান থেকে চলে যেতে হবে। আবার সেই আফগানিস্তান। আবার সেই অসহ্য, অসভ্য জীবনযাত্রা। এই জীবন থেকে আমার আর মুক্তি নেই। অনন্তকাল ধরে যেন আমি কোনও অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহাতে ঘুমিয়ে ছিলাম। সেই ঘুমের মধ্যে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। স্বপ্নের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম অনেক অনেক আলোর রাজ্যে। যেখানে অন্ধকারের লেশ মাত্র নেই। সর্বত্রই আলো আর এক মধুর ভাললাগা স্বপ্ন। স্বপ্ন বিদায় নিল। চোখ মেলে দেখলাম সেই অন্ধকার গুহাতেই আমি শুয়ে আছি। ভালো লাগার মুহূর্তগুলি কেন যে এত ক্ষণস্থায়ী হয়? আমার জীবনের সব ভালো মুহূর্তগুলি ভীষণ ক্ষণস্থায়ী। পারি না আমি তাদের ধরে রাখতে।
আবার আমি ফিরে চললাম বন্দীদশার মধ্যে। না গিয়েও তো উপায় নেই। আমি কোনও কিছুর মূল্যেও নিজের দেশকে ছোট করতে পারব না। এখান থেকে এই ভাবে চলে গেলে কাবুলের আত্মীয়দের আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হবে যে জাম্বাজের বৌ আর ফিরে আসবে না। আমাকে এবং আমার দেশের সব মেয়েদের আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। আর তাছাড়া আমার একটা চরিত্র হচ্ছে; কোন কিছুর শেষ না দেখা অবধি ছাড়ার পাত্রী আমি নই।
পাতানা বলে একটা জায়গায় আমাদের নামিয়ে দিল গাড়ি। এখান থেকে আমাদের বাড়ি মাত্র দুই কিলোমিটার। এই পাতানায় অনেকের কবর আছে। জাম্বাজের দাদু ও জ্যাঠাকে এখানেই কবর দেওয়া হয়েছিল। পাতানায়, কাজে অকাজে অনেক লোক আসে। কবরের কাছে বসে কেউ কাঁদে, কেউবা তাদের দুঃখের খবর জানায়। মোট কথা পাতানা এখানকার মেয়েদের কাছে একটা তীর্থস্থান। ভালো বেড়াবার জায়গা।
বাড়িতে ফিরে এসে ওদের ব্যাপারস্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেলাম। যেন বিশাল যুদ্ধ জয় করে আমি ফিরে এসেছি। একের পর এক সবাই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। সবার মুখে একই কথাসাবাস্তি দার বান্দি। এর অর্থ তোমাকে সাবাসি জানাচ্ছি। কেউ বলল প্লার, মোর, মখ না দা তোর কারাই। এর অর্থ বাবা, মার মুখ কালো করোনি। কেউ নাকি কল্পনাও করেনি আমি ফিরে আসতে পারি। আমি কি ফিরে আসতাম? এসেছি শুধু একটা লোকের প্রতি কৃতজ্ঞতা বা ভালবাসার। খাতিরে। তা নইলে কে আর এত কষ্ট ভোগ করতে চায়? একে তো কাদামাটির। বাড়ি দেশ তার ওপর বিঘুঁটে খাওয়া। বিশাল বিশাল গোল রুটি, হয় মাখন, নয় দই, নয়ত বা মাখন ভোলা জল দিয়ে খেতে হবে। যা আমরা এ জন্মে চোখে দেখিনি, তাই কোনও রকমে গিলতে হবে। মাখন ভোলা জলকে এরা কুবে বলে। দইকে বলে মস্তিয়া। গমের খড়কে এখানে বলে পোরোরা। এই প্রোরোরা গরুর ও খোরাক অর্থাৎ শুকনো খাবার। আর শাওতালা ও রিস্কা হচ্ছে লান্দা খোরাক অর্থাৎ তাজা ও সবুজ খাবার। সেপ্টেম্বরে আঙুর পাকে। জুলাইতে তরমুজ খাওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠে। সেপ্টেম্বরের প্রায় একমাস আগে থেকেই আপেল পাকতে থাকে। এখানে সবই খুব বড় বড় হয়, কিন্তু আপেল ছোটো। তবে একে বারে ছোটো নয়। আবার কাশ্মিরী আপেলের মতো রংও নয়, বড়ও নয়। শস্য বলতে এখানে আলু। পেঁয়াজ, শশা, তরমুজ পালং, টমেটো, গাজর সবই হয়। আর হল নানারকম ফল। যেমন, আপেল, আঙুর, খাটাকি, জরদালু, তুত, আলুবোখারা, বাদাম। আমরা যাকে বাদাম বলি ঠিক তা নয়। চেপটা চেপটা বাদাম আর খাটাকি একটু লম্বা কুমডোর। মতো। কিন্তু খেতে অপূর্ব। এই খাটাকি পেকে গেলে যদি তার পাঁচ মাইলের মধ্যে কোনও ঘোড়া বা গাড়ি যায় তবে তার শব্দে খাটাকিতে ভাঙন ধরে। সমস্ত গা ফেটে যায়। আর জরদালু হচ্ছে হলুদ রংয়ের একটু পানের মতো আকৃতির ফল। সাইজে ঠিক মাঝারি আলুর মতল। ভেতরে ফাপা, একটা চ্যাপটা দানা আছে। ঠিক আমলকির দানার মতো। জরদালু শুকিয়ে খোবানি হয়। এখানে গমের চাষ হয়। অনেক জায়গায়। ধান কম হয়। ঠিক কম নয় কিন্তু কেউ চাষ করে না। তামাকেরও চাষ হয়। তবে এই চাষ টাস সবই ওই সাত মাসের মধ্যে। মে থেকে নভেম্বর। কারণ এর পরে ঠাণ্ডা পড়ে যায়। আর তারপর বরফ। ঠাণ্ডায় গাছ শুকিয়ে যায়। সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের মধ্যে গম কাটা হয়ে যাবে। আবার নতুন করে গম ছড়াবে। গমের খড়গুলো ঠিক চুলের যেমন কদম ছাঁট হয় তেমনি ভাবে ডাস্ট করে রেখে দেয় গরুর খাবারের জন্যে। তাছাড়া এখানে মটরশুটির গাছের মতো একরকম গাছ হয় সেই গাছের নাম শাওতালা ও রিস্কা। এগুলোও গরুর খাবার। রোজার সময় পাকিস্তান থেকে ব্যবসাদাররা টমেটো, শশা, সান্তারা অর্থাৎ কমলালেবু, কড়াইশুটি, আচার, মুলো, কাঁচা লঙ্কা এবং আরো অনেক অনেক সামগ্রী আফগানিস্তানে নিয়ে এসে চড়া দরে বিক্রি করে। এখানে টাকাকে আফগানি বলে। পঞ্চাশ টাকা থেকে নোট শুরু। এক হাজার ইন্ডিয়ান টাকায় ষাট হাজার আফগানি টাকা পাওয়া যার। জিনিসের দামও খুব বেশি। একটা ডিমের দাম পাঁচশো টাকা। একটা মুরগীর দাম হাজার তিনেক, চারেক। এক গজ কাপড়ের দর আড়াই হাজার। খুব ভালো কাপড় হলে চার পাঁচ হাজার টাকা মিটার। এক ট্রাক্টর কাঠ দুলাখ টাকা। একটা দুম্বার দাম চল্লিশ থেকে আশি হাজার টাকা। এক পাতা ডিসপ্রিনের দাম পাঁচশো টাকা। এক বোতল সিরাপের দাম তিন হাজার। এক চারাগ আলু বাইশশশা এখানে কিলোফ চারাগ বলে। এক লিটার কেরোসিন তেলের দাম চার হাজার। এ দেশে বহু খারাপের মধ্যেও একটি খুব ভালোতা হচ্ছে মৌসুমী বায়ু। জলও অতি চমৎকার। যেমন ঠাণ্ডা তেমনি মিষ্টি। আর হাওয়া? তুলনা হয় না। কারো হাত,পা, শরীর যদি জং ধরা টিনেও কেটে যায় তবুও কোনও টিটেনাস নেওয়ার দরকার পড়ে না। সামান্য ডেটল ও মলম দিলেই সব ঠিক হয়ে যায়। সারাদিনই হাওয়া বয়। হাওয়ার বেগ সন্ধে থেকে বাড়ে। সারা বছর মোটামুটি একটা কিছু রাতে গায়ে দিতেই হবে, নইলে শীত করবে। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বরফ পড়ে। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল অবধি সমস্ত জমা বরফ গলতে থাকে। এই বরফ গলার সময় রাস্তাঘাট কাদায় কাদা হয়ে যায়। মাটি নরম থাকে। আবার মে মাসে শুরু হয় বৃষ্টি। এই সময় দেশের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়ে। গাড়ি তো জানুয়ারি থেকেই প্রায়ই বন্ধ থাকে। রুশি ট্রাক্টার চলে; তবে তার চাকাও হয় বরফে, নয় কাদায় আটকে যায়। কাদা খুঁড়ে, গাড়ি ঠেলে তবেই নিষ্কৃতি। জুলাই থেকে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। ডিসেম্বর থেকে জুন অবধি সবাই ঘরেই বসে থাকে। জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে চাষ শুরু হয়। আঙুর গাছের ডাল হেঁটে ছোট করে বরফের সময় মাটি দিয়ে ঢেকে রাখে। আবার বরফ পড়া শেষ হলে মাটি সরিয়ে গাছকে মুক্ত করে দেয়। জুন মাসে এখানে একরকম শাক হয়। দেখতে ঠিক কঁটানটের মতো। এই শাককে সবাই পিন্ডিই বলে। এর চাষ করতে হয় না। মাটি খুঁড়ে নিজে নিজেই হয়। এই শাক সকলে খায়। আর মরুভূমির বালি খুঁরে একজাতিয় ছোটো লম্বা গোছের সজী হয় তার নাম খেশ।
পাহাড়ের কোলে একরকম ছোটো ছোটো ঝাড় হয়। সেই ঝাড়কে এখানে সবাই বুট বলে। এই বুট যখন শুকিয়ে আসে তখন লোকে সেই বুট তুলে আনে। পরে সেগুলো তোরণের মধ্যে রেখে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালায়। এখানে উনানকে তোরণ বলে। দেখতে একটা তেলের ব্যারেলের মতো। মাটি খুঁড়ে পুরোটা সেই গর্তে নামিয়ে দেয়। মুখটা মেঝের লেভেলের বরাবর রাখে। আফগানিস্তানে গরম নেই বললেই চলে। দিনে সূর্যের প্রখর তাপ। কোনও গাছগাছালির ছায়া নেই। কিন্তু ঘরে ঢুকে গেলে আর তেমন গরম লাগে না বরং একটু শীত লাগে।
যষ্ঠ অধ্যায়
কি যে আমার মন চায়, তা আমি নিজেও বুঝতে পারি না। কখনো মন খুব খুশিতে ভরে ওঠে, আবার কখনো বড় একা হয়ে যাই। এই একাকিত্বকে কিছুতেই আমি এড়িয়ে যেতে পারি না। জাম্বাজ একদিন আমাকে বলল পাগলি, জাম্বাজ আমাকে পাগলি বলেই ডাকে। আমাদের এখানে একটা মেয়ে আছে, যার নাম বাবাকা। সে সকালে ঘুম থেকে উঠে চা জলখাবার খেয়ে আবার শুয়ে পড়ে। শুধু খাওয়ার ও বাথরুমের সময়টুকু ছাড়া বাকি সময়টুকু সে শুয়েই থাকে। তুমিও বাবাকার মতো; ওই সময়টুকু ছাড়া শুয়েই থাক। পরে আমি জেনেছিলাম, বাবাকা অন্ধ, কালা, বোবা। আজ আমার অবস্থাও সত্যিই বাবাকার মতো। চোখ থাকতেও অন্ধ, কান থেকেও কালা। অনেক কথা বলার থাকা সত্ত্বেও আমি যোবা। যে সব বই আমি সঙ্গে করে এনেছিলাম সেগুলো বেশ কয়েক বার করে পড়া হয়ে গিয়েছে। আমি একটি চলমান রাজ্যের গতিময় মেয়ে। কিন্তু আজ আমার কাজ শুধুই খাওয়া, ঘুম আর শুয়ে শুয়ে কল্পনার রাজ্যে চলাফেরা করা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। আইডেল ব্রেন ইজ ডেভিলস্ ওয়ার্কসপ। আমার ব্রেন ঠিক তাই হয়েছে। সারাদিন শুয়ে আমি ভাবি, যদি জাম্বাজের কিছু হয়ে যায়, তখন আমি কী করে মুক্তি পাব এই দেশ থেকে? তবে কি আমি কোনদিন মুক্তি পাব না? এই দেশ থেকে নিজের দেশে ফিরতে পারব না? আমার বাবা, মা এবং আর সবার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না? সবাই আমাকে এই বিয়ে করতে বারণ করেছিল। অপরাহ্নের বেলায় বসে আজ বড় বেশি মনে পড়ছে সেদিনের কথা মনে পড়ছে শ্যামলদার সেই কথা। যেদিন ওরা জানতে পেরেছিল যে, আমি জাম্বাজকে বিয়ে করেছি, সেদিন শ্যামলদা আমাকে বলেছিলেন–
–সুমি তোমার শিক্ষা, রুচি, তোমাদের দাম্পত্য জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে নাতো?
–জাম্বাজ ছেলেটা খুব ভালো; আমার সাথে খুব অ্যাডজাস্ট হবে।
–হলেই ভালো। তুমি যা উগ্র, রাগী! কিছুদিন বাদে আবার পার্সোনালিটির ক্ল্যাস না শুরু হয়, তারপর যেদিন শ্যামলদা শুনলো আমি কাবুলে যাচ্ছি সেদিন বলেছিলেন
–যাচ্ছো যাও; আমি বাধা দেব না। তবে যাওয়ার আগে ভেবেচিন্তে যাও। ওখানে তোমার, জাম্বাজ ছাড়া আপন বলতে কিন্তু আর কেউই নেই। তোমার বিপদে আপদে কেউ পাশে এসে দাঁড়াবে না। জাম্বাজ কিন্তু ওই দেশের ছেলে। তার বাড়ির বা দেশের বিরুদ্ধে কিন্তু সে যাবে না। এই মধ্যাহ্নে এসে নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিই। কেন তখন কারও কথা শুনিনি আমি? কী আশায়, কিসের সন্ধানে আমি এখানে এসেছিলাম? এখানে সর্বত্রই শুধু হাহাকার। সব হারানোর আর্তনাদ। এই সব কথা ভাবলেই আমি বিদ্রোহী হয়ে উঠি সবার প্রতি আমার মন ঘৃণায় ভরে ওঠে। কারণে অকারণে জাম্বাজের সঙ্গে ঝগড়া করি। বাড়ির সবাই আমাকে ভয় করতে শুরু করল। সবাই ভাবল শান্ত মেয়েটা হঠাৎ এত উগ্র হয়ে উঠল কী করে? জাম্বাজের ওপর আঘাতের পর আঘাত হানতে লাগলাম। ওকে একদিন বললাম– আমাকে আমার দেশে এখুনি নিয়ে যাবে কি না বলো? জাম্বাজ চুপ করে আছে দেখে হিংস্র বাঘিনীর মতো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আঁচড়ে কামড়ে ওকে ক্ষত বিক্ষত করতে লাগলাম। আসাম চাচা ধরতে এসেছিল। তার জামা ধরে ছিঁড়ে দিলাম। কালানিশকভ বন্দুক নিয়ে এলাম। সবাইকে গুলি করে নিজের বুকেও গুলি চালাব। জাম্বাজ আমার হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল। আমি তখন ওর চুলের মুঠি ধরে মাটিতে চেপে ধরলাম। এবার ওর দুই ভাই ও আসাম চাচা আমাকে ছাড়াতে এল। আসাম চাচা আমাকে চুল ধরে মাথাটা মাটির সঙ্গে চেপে ধরল। আমার মুখ দিয়ে গোঙানি বেরোতে লাগল। জাম্বাজ নিজেকে ঠিক করতে করতে আসাম চাচাকে বলল, আসাম গোল পাগলিকে ছেড়ে দাও। ওর লাগছে। পাগলির গোঙানি বেরোচ্ছে শুনতে পাচ্ছ না? পাগলির চুল ধরতে তোমায় কে বলেছে? ওর অভ্যাস নেই অত্যাচার, মারধর সহ্য করার। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। জাম্বাজের কথা শুনে আমি মাটির মধ্যে মিশে যেতে লাগলাম। যার ওপর এত অত্যাচার করলাম, কামড়ে রক্ত বার করে দিলাম সেই জাম্বাজ কিনা আমার যাতে ব্যথা না লাগে, সেই জন্যে এতো অনুনয় করছে। আমি স্তম্ভিত! হতবাক! নিশ্চল! জাম্বাজের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। আমার গাল বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। জাম্বাজ আমার মাথাটা নিজের কোলের ওপর রেখে হাত বোলাতে বোলাতে বলল– কেঁদো না পাগলি। আমি নিশ্চয়ই তোমার দেশে তোমাকে নিয়ে যাব। কারও কথাই আমি শুনব না। কেন তুমি কাঁদছ? যে যাই বলুক কারও কথাই তুমি বিশ্বাস করবে না।
সারা বিশ্বে কি এতটুকু লুকোবার জায়গা নেই? এই লজ্জার হাত থেকে যদি নিজের মুখটা কোথাও লুকোতে পারতাম তবে আমি যেন শান্তি পেতাম। কি অপরিসীম লজ্জা। লজ্জার হাত থেকে মুক্তি পেলাম না। দেখলাম জাম্বাজের হাত দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠেছে। ফোলা জায়গাটা দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রস বেরুচ্ছে ক্ষতের চার পাশ নীল হয়ে গিয়েছে। হাতের কব্জিতে এমন কামড়েছিলাম যে সেই জায়গাটা থেকে রক্ত ঝরছে। মাথার চুল থোকা থোকা উঠে গিয়েছে। কি ভয়ঙ্কর! কি বীভৎস। তবু মানুষটা অবিচল! এত কষ্ট, যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে তার আদরের পাগলির কান্না সহ্য করতে পারল না। ভীষণ ভালো লোকটা। আমার শিক্ষা, আমার স্ট্যাটাস পারলো কি আমাকে এই চরম লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে। কি হবে সেই শিক্ষা দিয়ে যে শিক্ষা মুহূর্তে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়? কি হবে স্ট্যাটাস দিয়ে যে স্ট্যাটাস এই মানুষটার মনুষ্যত্বের কাছে হেরে যায়? এরপর আমার পরিবর্তন হল। আমি ওদের সবার সঙ্গে মনেপ্রাণে মিশে যেতে লাগলাম। আমাকে আগে যে যা বলেছিল, সবাইকার সব কথা মিথ্যে মনে হল। আমি সত্যিকারের একটা মানুষকেই আমার জীবন সঙ্গী রূপে পেয়েছি। আমি মনে মনে ভীষণ গর্ব অনুভব করতে লাগলাম যে এমন একটা মানুষের মতো মানুষ আমার স্বামী। সে সময় দেশের সর্বত্র, মর্মান্তিক দারিদ্র। যারা কলকাতায় বা পাকিস্তানে ব্যবসা করে তাদের ব্যাপার আলাদা। কিন্তু এখানকার লোকেদের জীবনে দারিদ্রের যন্ত্রণা তো আছেই তার সঙ্গে আছে সংসারের জ্বালা। কাদির চাচার বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে হেঁটে দুমিনিটের রাস্তা। তার দুই বিয়ে। দুজনেই বেঁচে আছে। প্রথম পক্ষের এক মেয়ে, এক ছেলে। দ্বিতীয় পক্ষের দুই মেয়ে। কাদির চাচারা তিন ভাই। তিন ভাইয়ের বাবা একটাই কিন্তু তিনজনের মা আলাদা। কাদির চাচার বাবা সফরত খান তিনটে বিয়ে করেছিলেন। তিন বৌয়ের তিনটে ছেলে। মেজো বৌ যিনি ছিলেন তিনি সফরত খানকে বিয়ের আগে আর একটা বিয়ে করেছিলেন। সেই আগের স্বামীর ঔরসেও এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। লপু ও পারি তাদের নাম। আর সফরত খানের ঔরসে মাদালাম ও গোলবিবি। এখানে মেয়েদের পাঁচটা ছটা করে বিয়ে হতে পারে। তবে তালাক দিয়ে নয় স্বামী মারা গেলে।
কাদির চাচার দ্বিতীয় বৌ আসার পর থেকেই কাদির চাচাকে নিজের কবজায় করে নিল। বড় বৌ অনাদরে পড়ে রইল। কিন্তু বড় বৌয়ের একটা ছেলে আছে সুতরাং বাপের বাড়ি তাকে পাঠাতে পারবে না। সম্পত্তির ভাগ তাকে দিতেই হবে। তাই একটা ঘর তাকে দিয়েছে। সেই ঘরে মা, ছেলে, ছেলের বৌ ও দুই নাতি নিয়ে তাদের সংসার। কাদির চাচা ও তার দ্বিতীয় বৌ এবং দুই মেয়ে নিয়ে আরেক সংসার। যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দ্বিতীয় বৌয়ের। কষ্ট যা কিছু তা সব প্রথম বৌয়ের। দেশের সর্বত্রই এই ছবি। তবে কিছু ব্যতিক্রমও আছে। সংখ্যায় কম।
প্রতিটি বাবা-মার কম করেও দশটা পনেরটা করে সন্তান। সন্তানদের মানুষ করার চিন্তা তো আর নেই। দুবছর বয়স পর্যন্ত কোনও রকমে বড়ো করে দিতে পারলেই ছুটি। তারপর সব গরুর পাল। সকালে গোয়ালের দরজা খুলে গরুগুলোকে বাইরে বার করে দেয়। তারপর কোনরকমে এক পাঁজা রুটি করে রেখে দেবে আর ওই মানুষ গরুগুলো সারাদিন ঘুরবে ফিরবে আর শুকনো রুটি খাবে। সন্ধে হলে আবার গোয়ালে ঢুকবে। এই হচ্ছে এখানকার শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। মেয়েগুলো বড় হলেই তাদের বাবা ও মা বিয়ে দেওয়ার প্রহসন করে লাখ লাখ টাকা নিয়ে ছেলের বাড়িতে বিক্রি করে দেবে। কপাল ভালো হলে বর ভালো পায় নইলে সব শেষ।
আমাকে এদের এখানে সবাই কাফের বলে, হিন্দু বলে গালাগাল দেয়। আসাম চাচা আমাকে একদিন বলল–তুমি নামাজ পড়। নইলে কিন্তু তুমি জাহান্নামে যাবে। আমি তোমার হাতে জল পর্যন্ত খাব না।
আমি আসাম চাচার কথার উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করলাম না। এই ভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এবার এল রমজান মাস। বাড়ির সবাই রোজা রেখেছে শুধু আমি ছাড়া। আমি যে রোজা রাখিনি সেটা আসাম চাচার কানে উঠলো। তখন তিনি আমাকে বললেন- তোমরা হিন্দু, বাঙালি, তোমরা কাফেরের জাত। তোমাদের ছায়া দেখলেও আমাদের গুনাহ হবে। জাম্বাজ একটা জানোয়ার। তা না হলে একটা বিধর্মী কাফেরকে কখনও বিয়ে করে? আমার সহ্যের সীমা ছাড়াতে লাগল। গায়ের প্রত্যেকটা চুল খাড়া হল। মনে মনে বললাম, তোমাকে আজ আমি পরাস্ত করবই। তুমি শুধু আমাকে নয়–গোটা হিন্দুজাতটাকে গালাগালি দিচ্ছ। তুমি যদি আল্লার প্রেরিত হও তবে আমিও তো আল্লারই সৃষ্টি? তাহলে কেন আমি দীনহীন নতিস্বীকার করব? তাও আবার তোমার মতো একটা সামান্য মানুষের কাছে? অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার নিয়েই পৃথিবীতে জন্মেছি। সত্যিকারের ধর্ম কি তা জানি না। কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামিকে, জাতের নামে বজ্জাতিকে আমি মানি না। কিসে আছে ধর্মের যথার্থ আলো-তার হদিশ আমায় দিতে পার? আমি নাস্তিক নই। আমি বাস্তববাদী। আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বরকে, ভালবাসি মানুষকে। আমি মনে করি মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার নাম ধর্ম। সংসারের প্রতি দায়িত্ব পালন করার নাম ধর্ম। আমি তো চুপ করেই ছিলাম, কিন্তু তোমরাই আমার মুখ খুলতে বাধ্য করলে। যখন বাধ্যই করলে, তখন শোন। আমি আসাম খানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম- চাচা আমি তোমার ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করতে চাই না। কিন্তু তুমি শুধু একা আমাকে নয়, যারা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী তাদেরকেও অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছ। তুমি ভুলে গেলেও আমি ভুলতে পারি না, আমার শরীরের যে রক্ত অস্থি মজ্জা সবই ওই হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী একজন মানুষের দান। আর আমার হৃদয়ের ভালবাসার চেতনা, মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী একজন মানুষের সৃষ্টি। তবুও আমি তোমার অসভ্য আচরণের জন্যে নিরপেক্ষ বিচার করতে পারছি না।
আসাম চাচা আর কিছু বলেনি, নিজের ঘরে চলে গেছে। একটা মূর্খ মানুষের মূর্খামি ভাঙার জন্যেই আমি অনেক কথা তাকে বললাম এবং মনে মনে ভাবলাম কী আছে ধর্মের মধ্যে? সবাই তো মানুষ? একই মানুষ? তবে কোথা থেকে এলো হিংস্র ধর্মরূপি মানুষ? ঈশ্বর আল্লা তে এই হিস্র ধর্মকে সৃষ্টি করেননি? কে এই ধর্মকে জন্ম দিয়েছে? তার কি একটুও লজ্জা করছে না? ধর্মের দোহাই দিয়ে পৃথিবীতে আর কতদিন চলবে হিংসার এই ধ্বংসলীলা? ১৯৯২-তে বাবরি মসজিদ্ নিয়ে কত কাণ্ডটাই না হল? গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজ, তিলজলা, চার নম্বর ব্রিজ, রাজাবাজার ও আরো অনেক অনেক জায়গায় শয়ে শয়ে হিন্দু-মসুলিমদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি হল। রাস্তায় মিলিটারি টহল দিল। কাফু জারি হল। ব্লাক আউট হল। সবই একটা মসজিদ ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হল? ধর্মের জিগির তুলে ধর্মকে আশ্রয় করে, যারা ধর্মের নামে ভণ্ডামি করছে তাদের কি একটুও লজ্জা করে না। এ ধরনের ভন্ডামি থেকে মানুষ কবে মুক্তি পাবে? যারা বাবরি মসজিদের ঘটনায় মারা গেল, তারা কি জীবন দিয়েও বাবরি মসজিদ নতুন করে বানাতে পরল? এর নাম কি ধর্ম? ধর্মের যদি এই ভয়ঙ্কর রূপ হয়, তবে ধিক্কার সেই ভয়ঙ্কর ধর্মকে, আর ধিক্কার সেই ধর্মের পূজারীদের। ধর্ম ধর্ম করে যদি মৃত্যু হয়। তাহলে তথাকথিত ধর্মহীন বিধর্মী হয়ে বেঁচে থাকা কি সুন্দর নয়?
আর একজন কট্টর মুসলিম হলেন গুলবদিন হেমতিয়ার যিনি ১৯৭৯ থেকে যুদ্ধ করে চলেছেন, ডঃ নাজিবুল্লা ও রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে। গুলবদিন হেমতিয়ার ইবি-ইসলামি-আফগানিস্তান পার্টির মাথা। বাইরের জগতে অবশ্য, তার নাম–ইঞ্জিনীয়ার গুলবদিন–হেকমতিয়ার। ১৯৯০-র শেষে যখন নাজিব সরকারের পতন হল তখন সাময়িক ভাবে দুবছরের চুক্তিতে মোজাদ্দিদি সাহেব গদিতে বসলেন। চুক্তির মেয়াদ শেষে, আবার দুবছরের চুক্তিতে এলেন রাব্বানি। কিন্তু দুবছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও রাব্বানি গদি ছাড়লেন না। তখন গুলবুদিন যুদ্ধ শুরু করলেন। সে কি তাণ্ডব। আমাদের গ্রাম থেকেও প্রচুর ছেলে তুলে নিয়ে গেল যুদ্ধের জন্যে। আমরা আমাদের বাড়ির ছেলেকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিলাম। বাতাসি চাচির ভাই আয়ুপ মারা গেল। রহমত যার মাত্র দুমাস বিয়ে হয়েছে যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হল। রহিম খান, দৌলত খান, আব্দুল খান, বসির খান, ইসলাম, সাত্তার, বিশমিল্লা, রসিদ, গুলখান, সুলতান–এরা সবাই গুলবদিনের যুদ্ধে শহিদ হল। গুলবদিনের প্রধান ঘাঁটি হল চারাশিয়া। এই চারাশিয়া থেকে কাবুল মাত্র আধ ঘণ্টার পথ। সাধারণ মানুষ কিছুদিনের জন্যে একটু হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। মোজাদ্দিদি সরকারের সময় সাময়িক ভাবে কিছুদিন যুদ্ধ বন্ধ ছিল। কিন্তু হঠাৎ আকাশে আবার কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। কাবুলের রাস্তায় কামানের গর্জন স্তব্ধ হতে না হতে আবার যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। এই যুদ্ধ রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে বা নাজিবের বিরুদ্ধে নয়! এক মুসলিমের সঙ্গে অন্য মুসলিমের। শুরু হল গৃহযুদ্ধ।
আর এই গৃহযুদ্ধ শুরু করলেন দেশভক্ত ইসবি-ইসলামি-আফগানিস্তান পার্টির মাথা ইঞ্জিনীয়ার গুলবদিন হেমতিয়ার। গৃহযুদ্ধের মূল বিষয়বস্তু হল ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব। আবার নতুন করে জনগণের রক্ত দিয়ে ইতিহাসের পাতা লাল হতে লাগল। রাব্বানি যখন বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য উৎপাদন ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় শোষণের এক রূপের জায়গায় অন্য আর এক রূপের আবির্ভাব ঘটল। আবার রাষ্ট্রযন্ত্রের ভাঙন সূচনা করল এই গৃহযুদ্ধ।
যে সময় আফগানিস্তানের প্রত্যেকটি বিপ্লবী দলের প্রধান কর্তব্য ছিল নূর মহম্মদ তারাকি থেকে নাজিব সরকার পর্যন্ত যারাই ক্ষমতায় এসেছেন তাদের শাসন ও নিপীড়ক অঙ্গগুলিকে কেটে বাদ দেওয়া গুলবদিন হেকমতিয়ার ঠিক সেই সময়ে ঘৃণ্যতম পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। যে গুলবদিন সুদীর্ঘ কাল ধরে কাবুলে মুসলিম শাসন কায়েম করার জন্যে লড়াই করে এসেছেন। আজ তিনিই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছেন। কাবুলের রাস্তায় লাশের পাহাড়। নর-নারী শিশুর-ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ রাস্তার মাটির সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। পেটের নাড়ি-ভুড়ি বেরিয়ে রাস্তার ধুলোর সঙ্গে দলা পাকিয়ে গেল। মানুষজন শহর ছেড়ে পাহাড়ের ওপর আশ্রয় নিল। সেখানে রেহাই পেল না কেউ। শহরে কামান, আর পাহাড়ে ঠাণ্ডা। অনাহারে, অনিদ্রায় সেখানে সবাই মারা যেতে লাগল। লাশে যখন পচন ধরল, তখন রাজ্যে টেকা দায় হয়ে পড়ল।
কিন্তু এত লাশ সরাবে কে? তাই দুই পক্ষ থেকে একটা নির্দিষ্ট টাইম ঠিক করা হল। সেই টাইমে কোনও পক্ষই কোনও পক্ষকে গুলি ছুড়তো না। যুদ্ধ বন্ধ থাকতো। সাদা পতাকা নিয়ে লাশ সরিয়ে আবার যুদ্ধ শুরু হত। নতুন করে কেউ তার বাবা কেউ তার সন্তান হারাল। কেউ হলো স্বামীহারা। কেউ হারাল ভাই। যারা একসময় বলেছিল ডঃ নাজিব গদিচ্যুত হলে দেশে শান্তি কায়েম হবে, তারাই এবার বলতে লাগল, এর থেকে নজিব সরকার ভালো ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কর্ণধারগণ গুলবদিনকে অনুরোধ জানালেন যুদ্ধ থামাবার জন্যে। কিন্তু গুলবদিনের গদি চাই-ই চাই। থামলে কি চলে, দেশের প্রত্যেকটা মানুষ যদি যুদ্ধে মরেও যায়, তাতেও তার কিছু এসে যায় না।
গুলবদিন চান মৃতদেহে ভরা একটা গোটা রাজ্য। সুতরাং জীবিত মানুষের কলরব-মুখর অর্ধেক রাজ্যের কোনও মূল্যই তাঁর কাছে নেই। অবশেষে বিশ্ব প্রতিনিধির মধ্যস্থতায় ঠিক হল, গুলবদিন প্রধানমন্ত্রী হবেন, রাব্বানি হবেন রাষ্ট্রপতি, মাসুদ আহমেদ শাহ সৈন্য প্রধান, আর হাজি রুস্তম হাওয়াই আজ্ঞা প্রধান। হাওয়াই আজ্ঞা অর্থাৎ বিমান কেন্দ্র। যখন সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল, তখন গুলবদিন মক্কায় গিয়ে কোরান শরীফের ওপর হাত রেখে এই বলে শপথ করে ফিরে এলেন যে, কোনও দিন, কোনও মতেই তিনি আর যুদ্ধ করবেন না। কিন্তু মাস যেতে না যেতেই আবার গুলবদিন যুদ্ধ শুরু করলেন। কারণ গদিতে অন্য কাউকে রাখতে চান না। তিনি একাই দেশের রাজা হবেন। এই হচ্ছে কট্টর মৌলবাদী মুজাহিদ ধর্মনিষ্ঠ মানুষের চেহারা। আজ আফগানিস্তানে পবিত্র ইসলামের নামে যে ত্রাসের রাজত্ব চলছে তার নেতৃত্বে আছেন ইঞ্জিনীয়ার গুদিন হেমতিয়ার। যিনি নাকি দেশে মুসলিম শাসন কায়েম করার জন্যে ৭৯ থেকে ক্রুসেড চালিয়ে যাচ্ছেন। গুলবদিন যদি সেদিন গৃহযুদ্ধ রচনা না করত তবে তালিবান প্রবেশ করতে পারত কি? অভূতপূর্ব! অদ্ভুত! চমৎকার। আমি নির্বাক হয়ে গেলাম এই কট্টর মুসলিমের কট্টর ধর্মপরায়ণ দেখে। আর হাসি পেল জনগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখে। যে নাগরিকরা একদিন নাজিবের বন্দী হওয়ার দিনটাকে উৎসবের দিন বলে ঘোষণা করেছিল। সোনার অক্ষরে স্বাধীন দেশের নাম লিখেছিল; আজ তারাই আবার নাজিবের মুক্তির জন্য আল্লার দরবারে মাথা ঠুকছে। তারাই বলছে নাজিবই ভালো ছিলেন। তিনি নাকি দেশ ভালোই চালাচ্ছিলেন।
আমি মনের ভিতর একটা শান্তি অনুভব করতে লাগলাম। ভাবলাম, ওদের পবিত্র কোরান শরীফ-কে অবমাননা করার, দুঃসাহসিকতা ও স্পর্ধার কর্কশ গদ্যের চাইতে; আমার বিধর্মী কাফের পরিচয় অনেক রম্যকাব্য। আমি বিধর্মী হলেও কোনও তীর্থক্ষেত্রে পবিত্র ধর্মগ্রন্থের ওপর হাত রেখে মিথ্যে শপথ করবার সাহস বা প্রবৃত্তি কোনটাই আমার নেই। কোনও ধর্মের অসম্মানও আমি করতে পারব। ধর্ম না মানলেও রুচিকে তো অস্বীকার করতে পারি না। মানুষকে তো মানি।
সপ্তম অধ্যায়
গরমের শেষ। শীতের হাওয়া লেগে গাছের পাতা একে একে ঝরে পড়ে যাচ্ছে। সব বাড়িতেই মোটামুটি শীতের খাবার ঘরে তোলা হয়ে গিয়েছে। প্রায় সব বাড়িই এখন আগুনের তাপে ঘর গরম করে। ঘরের ভিতর একটা সুড়ঙ্গের মতো করা আছে। সেই সুড়ঙ্গের একটা মুখ রান্না ঘরে বড় উনানের সঙ্গে যুক্ত। আর একটা মুখ ঘরের ভেতর দিয়ে গিয়ে অপর দেওয়াল দিয়ে ছাদে উঠে গিয়েছে। এই মুখটা দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যায়। ঘরের মেঝে পাতলা অথচ বেশ চওড়া পাথর দিয়ে তৈরি। এই পাথর গরম হয়ে ঘর গরম হয়। এই সময়টাকে এখানকার লোকে মুনাই বলে। আর শীত শেষ হয়ে যখন গ্রীষ্ম আসে তখন সবাই বলে-মুনাই উড়াল, সুরমুনাই রাগালাই–অর্থাৎ শীত চলে গিয়ে বসন্ত কাল গরম এল। এই সময় এখানে বৃষ্টি শুরু হয়। বসন্তকালের বসন্ত আর থাকে না।
শীতের পড়ন্ত বিকেল। অস্তমিত সূর্য তার শেষ রশ্মিটুকু ঢেলে দিয়ে সমস্ত আকাশটাকে রাঙিয়ে তুলেছে। পাখিরা কিচির-মিচির ধ্বনি তুলে নিজের নিজের কুলায় ফিরছে। আমার সেজো জা সাগি কুয়া থেকে ঘড়ায় করে জল আনছে রাতের জন্যে। এখানে জলকে বলে। সকালবেলাকে বলে গিস। দুপুরকে বলে গরমা। আর বিকেল বেলাকে মাস্পীন ও রাতকে বলে মকাম। আমার ছোট জা রান্নাঘরে রুটি তৈরি করছে। রুটিকে এরা মারুই বলে। আমি ঘরে বসে আমার মেজ দেওরের মেয়ে তিন্নিকে A.B.C.D পড়াচ্ছিলাম। হয়ত এই শিক্ষা তাকে আলোর পথ কোনদিন দেখাবে না, কিন্তু আমার তো সময় কাটবে। জন্ম মুহূর্ত থেকে তিনি আমার কাছে। আমার সন্তান নেই বলে এই মেয়েকে দেওর ও জা পবিত্র কোরান শরীফের ওপর হাত রেখে, দশটা মানুষের সামনে, জাম্মাজের সামনে আমাকে দান করেছে। বলেছে, এই মেয়ে তোমার। এর ভালো মন্দ, জীবন মরণ সবই তোমার ও জাম্বাজের। তারপর থেকেই তিন্নিকে সবাই আফগানিস্তানের সমস্ত মানুষ হিন্দুস্তানের সবাই জাম্বাজের ও সাহেব কামালের মেয়ে বলেই জানে। মেয়েও জানে আমিই তার মা। ছটা বছর আমার জীবন থেকে বিদায় নিল। আমি, আন্দামানের জেল নয়, আফগানিস্তানের পারিবারিক কয়েদখানায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত! কিন্তু কি যে আমার অপরাধ, তা জানতেই পারলাম না। সারাদিন প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আমাকে অভিনয় করতে হয়। মনের যন্ত্রণা লুকিয়ে মুখে হাসি দেখাতে হয়। পুরো তিনবছর চার মাস হলো। আমি একা এখানে আছি।
জাম্বাজ এখানে নেই। রাত কত হবে কে জানে সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। সারাদিনের অভিনয়ের শেষে, এই রাতটুকু আমার; সম্পূর্ণ আমার। এই রাতের অন্ধকারেই আমি খুঁজে পাই নিজেকে। মাত্র তিন বছরের স্মৃতি এবং পরিপূর্ণ প্রেমের কত আনন্দমুখর মুহূর্ত, কত রাত জাগানো কাব্যপ্রেরণা, কত আকাঙ্ক্ষিত সুখের প্রতিশ্রুতি অন্ধকারে বিসর্জন দিয়ে মুখোমুখি হলাম নিজের সঙ্গে। অসহ্য জীবনযাত্রার প্রশ্নে ও চিন্তায় আমি দিনরাত জর্জরিত। তীব্র সংশয়ে সর্বক্ষণ আমি আচ্ছন্ন। এই আদিম পুরুষ শাসিত মৌলবাদীর দেশ থেকে আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার দেশে আমি কি কোনও দিন ফিরতে পারব? এই বন্দীদশায় নিজেকে আর আমি কোনও মতেই মানাতে পারছি না। যে করেই হোক, আমার দেশে, আমার জন্মভূমিতে ফিরতে আমাকে হবেই। যেখানে আমি মুক্ত। আমার আত্মার ও সত্তার মুক্তি। অপ্রত্যাশিত ডাকে ভাবনায় ছেদ পড়ল। আমার মেজো দেওর আমার নাম ধরে ডাকছে। আমি বুঝলাম হঠাৎ এত রাতে কেন আমাকে তলব! সাদগির বাচ্চা হবে। বিকেলে আমি ওর মুখের ও শরীরের অলসতা দেখে বুঝেছিলাম আজ একজন নতুন অতিথি আমাদের বাড়িতে আসছে। ভগবান এই ব্যাপারটায় আমার প্রতি সদয়। একা পালাবার পথ পাচ্ছি না, তায় সুগ্রীব দোসর। যাই হোক, কর্তব্যের খাতিরে সাদগির ঘরে গেলাম। এখানকার মেয়েদের বাড়িতেই ডেলিভারি হয়। যার ভাগ্য প্রসন্ন সে বেঁচে থাকে, আর ভাগ্যদেবী বিমুখ হলেই ঘটে বিপর্যয়। আমার জ্যাঠতুতো ননদ ওই বিমুখের দলে। তার ছয় ছেলে এক মেয়ে। তাতেও তার স্বামী খুশি নয়। আবার সে সন্তানসম্ভবা। যথাসময়ে তার ডেলিভারিও হল। আবার একটা ছেলে। সেই আনন্দে সারা বাড়ি মত্ত! কিন্তু ঠিক সেই সময় প্রসূতি অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। তার প্লাসেন্ট্রা তখনো তার গর্ভে। পরের দিনও চলল যন্ত্রণা। অবশেষে এল মুক্তি। পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিল সে। পড়ে রইল তার সদ্যোজাত শিশুপুত্র-যার জীবনযাত্রা অবাঞ্ছিতের মতো। মায়ের স্নেহভরা কোলের বদলে মিলল পৃথিবীর কঠিন শয্যা। অসহ্য! অসম্ভব সব কাণ্ডকারখানা। যা শুনলে যে কোনও সুস্থ মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লোম খাড়া হয়ে উঠবে। আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী। এই অসহ্য জীবনের সঙ্গে আমি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পরেছি।
সাদগির আবার মেয়ে হয়েছে। এই নিয়ে তার চারটে মেয়ে হল। ১৯৯১-এ তার বিয়ে হয়েছে। ৯১ থেকে ৯৪ পর্যন্ত তার চারটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। সে যখন একবছর বাপের বাড়ি ছিল বিয়ের আগে তখনই সে গর্ভবতী হয়। শ্বশুড়বাড়ি আসার তিনমাস বাদে মেয়ে হয় প্রথম। গোয়ালে তো জায়গা আছেই, সুতরাং সন্তান না হওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।
রাত গিয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। আমি দাঁত ব্রাশ করে ঘরে গিয়ে বসলাম। ততক্ষণে আমাদের আশ্রিতা গুলগুটি চা নিয়ে এসেছে। গুলগুটির স্বামী বাইরের দেশে গিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। তার যাওয়ার আর কোনও জায়গা নেই। তাই আমাদের বাড়িতেই থাকে। যতদিন স্বামী নামে জন্তুটা বেঁচে থাকবে ততদিন সে আর কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। আমি তাকে আমার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছি। আমার ঘরে আমার পাশে সে শোয়। এখন আমি একা। সম্পূর্ণ একা। মাঝে মধ্যে মনের পর্দায় ভেসে ওঠে জাম্বাজের প্রতিশ্রুতিময় ভালবাসার রঙিন দিনগুলোর ছবি। তবে কি সবই মিথ্যে? সমস্তটাই কি তার ছলনা? জীবনের প্রথম দিনটাই কি আমার মিথ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল? এই অপমান, অবহেলা সারা জীবন আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে? কোনও স্বামী তার স্ত্রীকে না জানিয়ে কোথাও চলে যাবে–এটা আমার কাছে কল্পনারও অতীত। আমার বাড়ির ভিতটা এত নড়বড়ে হবে, তাকি আমি স্বপ্নেও ভেবেছি। শুধু আমি কেন কেউই কি তা ভাবতে পারে! নাকি তা সম্ভব? আমার জীবনে ঘটল এই অসম্ভব ঘটনা।
আমার দেওররা আমাকে চিনতে পারেনি। প্রতিহিংসার আগুনে আমি এদের পুড়িয়ে ছাই করে দিতেও কুণ্ঠিত বোধ করব না। আমার প্রথম কাজ হবে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে বার করা। দ্বিতীয় কাজ, যাতে জাম্বাজের ভাইরা জীবনে কোনদিন হিন্দুস্থানে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। আমি জানি ব্যবসার খাতিরে হিন্দুস্থানে এদের যেতে হবেই। কারণ এদের ব্যবসা একমাত্র ওখানেই আছে।
আজ তিন বছর ধরে আমি অপেক্ষা করে আছি কবে এরা আমাকে, আমার দেশে নিয়ে যাবে।
হয় মৃত্যু না হয় সুস্থ জীবন। দুটির অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। মৃত্যু আর জীবন এক সঙ্গে হতে পারে না। মৃত্যুকে বাদ দিয়ে যদি জীবন চাই তবে আমার দেশে যেতে হবেই। আমার দেওররা আমাকে কেন যে এখানে ধরে রেখেছে, কেন যে কিছুতেই দেশে ফিরে যেতে দেয় না তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। ছোট থেকে বড় সবার কাছে আমি রোজ আকুতি জানাই আমাকে বাবা-মার এবং স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে। আল্লার দরবারে মাথা ঠুকি। কোরান শরীফের কাছে কেঁদে কেঁদে অনুরোধ করি যেন আমার দেওরদের মনে আমার জন্যে একটু মায়া হয়। খেতে, বসতে, শুতে, মনের মধ্যে শুধু একই চিন্তা কবে আমার আপনজনেদের কাছে যাব। যারা আপন তারা কেউ আজ আমার পাশে নেই। আর যে মানুষটাকে নিজের অনেক আপন করে নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলাম–সেও তো আমার পাশে নেই। চোরের মতো করে সে পালিয়েছে। প্রতিদিন ভোরের সূর্যকে দেখে মনে করতাম–আজ হয়ত আমার দেওর আমাকে বলবে, চল তোমাকে আমরা নিয়ে যাবো কিংবা রাতে হঠাৎ জাম্বাজ আসবে। তখন আমি জাম্বাজের সামনেই যাব না। কথাই বলব না। কিন্তু সব ভাবনা ভাবনাই থেকে যায়। জাম্বাজও আসে না, আর ভোরের সূর্যের আলো আমার অন্ধকার জীবনকে এতটুকুও আলোকিত করে না। আবার আমি সবার কাছে আমার মুক্তির জন্যে অনুরোধ করি। আর সবাই আমাকে নিয়ে মজা করে। মুচকি হাসে। চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে। আমার জায়েরা মজা করে বলে এই তো সামনের মাসে তোমাকে নিয়ে যাবে। সামনের মাস শেষ হলে বলে, পরের মাসে নিয়ে যাবে। আকাশে, বাতাসে নীরবে মিশে যায় আমার হাহাকার, আমার কষ্ট, আমার দুঃখ।
একদিকে আছে মুক্তি না-পাওয়ার হাহাকার। অন্যদিকে আছে শারীরিক অত্যাচার। দেওররা গায়ে হাত তুলতে দ্বিধা বোধ করে না। এখানকার প্রতিটি মানুষকেই সহ্য করতে হয় এই অত্যাচার। স্বামীরা গার্হস্থ্য দায়িত্বের সব বন্ধন স্ত্রীর অঙ্গে সহস্র পাকে জড়িয়ে দিয়ে পাড়ি দেয় হিন্দুস্থানে। কেউ চারবছর, কেউ বা ছবছর করে থাকে। আর তাদের বিবিদের সহ্য করতে হয় শ্বশুরবাড়ির সবার অকথ্য অত্যাচার। এই অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি নেই তাদের। আমিও সেই অসভ্য আদিম মানুষের অত্যাচারের শিকার হয়েছি। জীবনের এই অজানা দিকটাকে জানছি।
আফগানিস্তানের মেয়েদের কোনও স্বপ্ন নেই। বিরাট কিছু পাওয়ার আশা নেই। এদেশের মেয়েরা বাবা-মার ব্যাঙ্ক ডিপোজিটের সার্টিফিকেট। আর একটু দৈহিক সুখের বিনিময়ে সারাজীবন স্বামীর বাড়িতে মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করতে হয়। আমার ঘরে ঢুকে বাঁ-দিকের দেওয়ালে জাম্বাজের একটা বেশ বড় ছবি টাঙানো আছে। কখনো ভুলেও আমি ছবিটার দিকে তাকাই না। ঘৃণা, নাকি ভীষণ ভালবাসা, অথবা অসহ্য বিতৃষ্ণা–ঠিক কী যে আমার মনে ছেয়ে আছে তা আমি নিজেই বুঝতে পারি না। কেন যে আমি ছবিটার দিকে তাকাই না তার উত্তর খুঁজে পাই না। তবুও যদি কখনো তাকাই তবে একটা বোবা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকি। মনে মনে তখন আমি কি বলি কে জানে! অনুযোগ? অভিযোগ? নাকি তাকে কাছে পাওয়ার একটা আকর্ষণ অনুভব করি। না, কোন আকর্ষণ অনুভব করতে পারি না। চোখ দুটো দিয়ে শুধুই যেন আগুন ঝরতে থাকে। শুধু প্রতীক্ষা, কবে আমি হিন্দুস্থানে পৌঁছব? তারপর লুকিয়ে একটা পাসপোর্ট জোগাড় করে পাড়ি দেব বিদেশে। আর এটাই হবে জাম্বাজের উপযুক্ত শাস্তি। এইভাবেই সারারাত আমি একটা অদ্ভুত কল্পনার রাজ্যে চলাফেরা করি। মাঝে মাঝে ভাবি, আমি পালিয়ে চলে যাচ্ছি আমেরিকায়। কল্পনায় সেখানে একটা নাটকের হল তৈরি করে নিই। আর নাটকের নায়িকা আমি। অভিনয় আমি জানি। অভিনয় করার শখটা জেগেছিল একটা সিনেমা দেখে। আমি তখন বেশ ছোটো। বাগুইহাটিতে গিয়েছি।
বিনোদিনী সিনেমা হল তখন নতুন হয়েছে। বাগুইহাটি বাজার ছাড়িয়ে দমদম পার্কের দিকে যেতে পড়ে হলটা, গায়ত্রীর মামার বাড়ি ওখানে। প্রথম আমি সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। মনের মধ্যে ভীষণ এক উত্তেজনা। আবার ভয়ও করছে। বাড়িতে দুপুরবেলা ঠাকুমা যখন দেখবে আমি নেই, তখনি খোঁজ পড়বে। সেদিন আমি গায়ত্রীর সঙ্গে সিনেমা দেখে হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলাম, মহাতীর্থ কালীঘাটের কালী ঠাকুরের চরিত্রটা যদি আমি করতাম তাহলে কেমন হতো? কী যেন একটা চিন্তা আমার মনকে ব্যতিব্যস্ত করতে লাগল। শয়নে স্বপনে সব সময় আমি যেন ওই কালী ঠাকুরের চরিত্রের মধ্যে ঘোরাফেরা করতাম। যার ওপর রাগ হতো তাকে যেন ভষ্ম করে দিতাম। আবার শিবের ধ্যান করতাম।
একদিন মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেলাম। তারপর মাকে যখন আমার মনের কথা খুলে বললাম তখন মা শুনে অবাক। মা হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারত না। আমাকে কি বলবে ভেবেই পায় না। শেষে বলল, দাঁড়া, তোর কালী ঠাকুর হওয়া বার করছি। বাবাকে বাড়ি আসতে দে। কান ধরে একপায়ে যখন দাঁড় করিয়ে দেবে তখন কালী ঠাকুর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকিস। অবশ্য একপায়ে দাঁড়াতে হয়নি। কারণ ঠামা। ঠাম্মাকে গিয়ে ব্যাপারটা একটু এদিক সেদিক করে বললাম। ব্যস। ঠামাই তখন আমার হাতের খাড়ার কাজ করতে লাগল। আমাকে বাঁচাবার জন্যে মাকে বলল, শুনে রাখো বৌমা, আমার নাতনির নামে যদি তুমি কেষ্টর কাছে। নালিশ করো, তবে কিন্তু আমি বাপের বাড়ি চলে যাব। কথাটা মনে থাকে যেন।
মা চুপ। সাহস নেই আর বাবার কাছে নালিশ করার। তবুও ঠাকুমার সব কথা মা রাখতে পারেনি। আমার অভিনয় করার কথা বাবাকে বলে দিয়েছিল। বাবা শুনে একটু বকলেন। তারপর বললেন, অভিনয়-টভিনয় বাজে জিনিস। মন দিয়ে পড়াশুনা কর। পড়াশুনায় সাকসেসফুল হলেই জীবনে আসবে সব সার্থকতা। নতুবা সবই শূন্য। অভিনয় করে ভালো বর পাওয়া যায় না; তার জন্যে চাই শিক্ষা। ডিগ্রি। মনে মনে আমি বাবাকে বলতাম, পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে আমি তো কিছু করতে চাইছি না? কিন্তু পারতাম না। ভয়ে চুপ করেই থাকতে হতো। সেই সময় আমার বয়স মাত্র বারো বছর। ক্লাস সিক্স-এ সবে উঠেছি। নতুন বই কেনার ধুম। তারপর সেই বইয়ের মলাট দেওয়া নিয়ে ব্যস্ততা। সব মিলিয়ে মনের মধ্যে সে এক ভীষণ উত্তেজনা। এই সবের পরে আছে সরস্বতী পুজো। একদিকে উঁচুক্লাশে ওঠার আনন্দ, অন্যদিকে সরস্বতী পুজো। সঙ্গে চকচকে নতুন বইয়ের মেলা। সব মিলিয়ে শুধুই ভালো লাগা আর ভালো লাগা। তাবলে অভিনয় করার ইচ্ছেটা যায়নি বরং আরো প্রবল হয়ে উঠেছে।
১৯৭২। চার বছর যে কী ভাবে এত তাড়াতাড়ি চলে গেল তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আবার ফিরে এল সরস্বতী পুজো। কিন্তু এবারের পুজোতে আমার জীবন থেকে সব চাইতে বেশি আপনজন বিদায় নিলেন। আমার প্রিয় মানুষ আমার ঠাকুরদাদা, যার ভয়ে আমাকে সামান্যতম শাসন করার অধিকারও কারো ছিল না। যাঁর স্নেহ ও ভালবাসার ছায়ায় আমি বড় হয়ে উঠেছি। সেই একেবারে কাছের মানুষ দাদু বিনা নোটিসে ভঁর ইহজগতের চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। আমরা সবাই কেঁদে কেঁদে তাকে ফেয়ার-ওয়েল দিলাম। এগারো দিনের দিন তার আত্মার শান্তি ও তুষ্টি কামনা করে অন্তিম বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। তারপর অনেক সময় পিছনে আমি ফেলে এসেছি। যে সময়ে আমি ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। পড়াশুনার চাইতে নাটক শেখার দিকে আমার বেশি ঝোঁক। আলমবাজারে প্রায়ই যেতাম একটা নাটকের গ্রুপে নাটক শিখতে। এই সময়টাতে আমি কোলকাতাতেই থাকতাম। সেই নাটকের গ্রুপের নাম বান্ধব সমাজ। গ্রুপের সবাই আমাকে নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করতেন। আর শ্যামলদার কাছেও নাটক শিখতাম। এই শ্যামলদার বাড়িতেই আমার পরিচয় হয়েছিল বিশাখা বৌদির। শোভন মুখার্জির স্ত্রী বিশাখা বৌদি। শ্বশুরবাড়ি রডন স্ট্রিটে। বিশাল রাজপ্রাসাদের মতো ছিল বাড়িটা। শোভনদার মা সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু স্বভাবে মোটেও ভালো ছিলেন না। শোভন মায়ের আঁচলের তলায় পড়ে থাকত। ছোটভাই মাকে বেশি পাত্তা দিত না। মায়ের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত। তাই ছোট ছেলের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন। নিজের ছেলেদের থেকে তার বেশি প্রিয় ছিল ভৃত্য পুত্র সচ্চিদানন্দ। তার পোয্য পুত্র। পরে, বহু পরে জেনেছি যে সচ্চিদানন্দ পোষ্য পুত্র নয়, পোষ্য স্বামী–অলিখিত। ছোট ছেলে মায়ের এই সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে করতে একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। আর বড় ছেলে শোভন? ঘরে বৌ থাকতেও বাইরে গিয়ে বারবনিতাদের সঙ্গে রাত কাটাত। তার মা এই সব নোংরামি, নষ্টামিকে প্রশ্রয় দিতেন। প্রতিবাদ করার প্রয়োজন বোধ কোনদিন করতেন না। পয়সার টান পড়লেই বিশাখা বৌদির গহনাতে হাত দিতেন। বৌদি যখন ব্যাপারটা জানতে পারল তখন লাগাম টেনে ধরল। যখন বৌদি আর গহনা দিতে রাজি হল না তখনই হল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি। তারপর সে অনেক কাহিনী মোটেই শোভনীয় নয়।
যাক সে সব কথা এখন নাটকের কথাই বলি। আগে যা বলছিলাম তারপর আমি অনেক নাটক করেছি। অনেক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। কিন্তু বান্ধব সমাজের প্রযোজনায় একটা নাটকে একটি মূক চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করে যে থ্রিল ও আনন্দ পেয়েছিলাম আর কোনও নাটকে তেমন পাইনি। সময় মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয়। আমিও তাই সব ভুলেছি, ভুলতে বাধ্য হয়েছি। নতুবা কেমন করে ভুললাম সেই বান্ধব সমাজকে? যে আমার এত আপন, যাঁরা আমার নিজের ছিল। কই আমি তো পরে কোনদিন তাদের কাছে দেখা করতে যাইনি? আমাকে কি তারা অকৃতজ্ঞ ভাবছেন না? যদি না ভাবেন ভালোই। এরপর ভাবলাম, অভিনয়ের পালা সাঙ্গ করে আবার পড়াশুনার জগতে ডুবে যাব। এক সময় আমার স্বপ্ন ছিল, হয় ডাক্তারি, নতুবা I.A.S পড়ব। কিন্তু I.A.S পড়ার জন্যে যে মনোযোগ দরকার সে মন ও সময় আজ অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। একটা সুদীর্ঘ সময় আমি পৃথিবীর সমস্ত রকম ভালো-মন্দ, উত্থান-পতন, পলিটিক্স, বিজ্ঞান, দেশবিদেশের সমস্যা ও সমাধান ইত্যাদি কোনও ব্যাপারেই নজর দিইনি। খবর রাখিনি। আর I.A.S পড়তে গেলে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পর্কে জেনারেল নলেজ থাকা চাই-ই চাই। সুতরাং I.A.S পড়া হবে না। বাকি রইল ডাক্তারি। এটাই আমার কাছে সহজ বলে মনে হয়।
আমার মেজো জা ঘরে ঢুকে জানালার পর্দা সরিয়ে দিল। চোখে আলো পড়তেই দেখি চারদিক রোদে ঝলমল করছে। সুন্দর সকাল। ভারাক্রান্ত ভাবটা যেন খানিক হালকা হয়ে গেল। সারা রাত ধরে আমি কল্পনার মধ্যে জাম্বাজকে অনেক শাস্তি দিয়েছি। তবে সত্যিকারের শাস্তি দিতে গেলে এখান থেকে বেরোতেই হবে। তাই ঠিক করলাম, যেমন করে হোক যে করেই হোক এখান থেকে, এদের হাত থেকে আমাকে পালাতেই হবে। পালানো ছাড়া আর অন্য কোনও পথ নেই। সোজা পথের আশায় ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত আমি এক অসহ্য উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করেছি। ১৯৮৮-এ যখন এখানে প্রথম এসেছিলাম, তখন জাম্বাজ মাত্র এক বছরের নাম। করে আমাকে এখানে বেড়াতে এনেছিল। কিন্তু সাত বছরেও তার এক বছর পূর্ণ হয়নি।
কিন্তু পালাব কেমন করে? কে আমাকে সাহায্য করবে? কোথায় পাবো একটা গাড়ি? যে গাড়ি আমাকে আফগানিস্তানের বর্ডার পার করে দেবে? এখানে তো যানবাহন বলতে জিপ, টয়টো, আর ট্রাক্টর, লরি। এবং গাধা, উটও আছে তবে সবার জন্যে নয়। যারা জঙ্গলে থাকে তাদের উটে করে চলাফেরা করতে দেখা যায়। আর যারা যাযাবর। এখানে যাযাবরকে কোচি বলে। এই কোচিয়ানরা শীতের সময় পাকিস্তানে চলে যায়। আর গরমের দিনে আফগানিস্তানে এসে তাঁবু বাঁধে। মরুভূমির বুকে তখন অনেক সাদা সাদা তাঁবু দেখা যায়। আর দেখা যায় কোচিয়ানদের ছাগল ভেঁড়া, গরু, গাধা এবং লম্বা লম্বা উট। এখানকার লোক বুকে খেমাক বলে। গাধাকে খাঢ় বলে। গরুকে গোয়াই বলে।
এই দেশে তো আবার মেয়েদের একা গাড়িতেও কেউ তুলবে না। সঙ্গে পরুষ থাকলে তবেই তুলবে। পুরুষ হচ্ছে একটা লাইসেন্স। কোথায় পাবো এখন আমি এই লাইসেন্স? হঠাৎ একজনের কথা আমার মনে পড়ল। সে মানুষটা অনেক বিষয়ে আমার কাছে কৃতজ্ঞ। ভাবলাম, তাকে সব খুলে বলে সাহায্য চাইলে কেমন হয়? আর যদি কিছু অর্থ তাকে দিই তবে সে আর কিছুতেই না বলবে না সেটা আমি নিশ্চয়ই করে বলতে পারি। কিন্তু তার কাছে যেতে গেলেও তো লুকিয়েই যেতে হবে। বাড়ির কেউ যাতে জানতে না পারে। আবার ভাবি সে যদি গাড়ির ব্যবস্থা করেও দেয় কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে তো পারবে না! আমিও নেই সেও নেই। সবাই বুঝে ফেলবে কে আমাকে পালানোর পথ দেখিয়েছে।
এদিকে একা যাবো ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়। কারণ এখানে এখন সর্বত্রই তালিবান প্রহরায়। আমাকে একা দেখে যদি ধরে ফেলে? সমস্ত রাস্তার মোড়ে মোড়েই তালিবানরা দাঁড়িয়ে সর্বত্র নজর রাখছে। যদি দেখে কোনও মহিলা পুরুষ ছাড়া রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে যাচ্ছে; তবে আর রক্ষে নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আটক করে হাজারো জেরা শুরু করবে। আর যদি জানতে পারে আমি পালিয়ে যাচ্ছি তখন ওরা আমার কোন কথাই শুনবে না, গুলি চালাবে নির্মমভাবে। আমার শরীরটা ঝাঁঝরা করে দেবে।
তালিবানরা অনগ্রসর, চরম মৌলবাদী ও রক্ষণশীলতার প্রতীক। বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে, অর্থনৈতিক ও মানবিক ভাবধারার উন্নয়ন এবং বিকাশ ইত্যাদি ব্যাপারে হাজার বছর পিছিয়ে। সমস্ত মৌলবাদী পুরুষরাই, মেয়েদের শক্তি সম্পর্কে ভীষণ সচেতন। পুরুষেরা খুব ভালো করেই জানে যে, একবার যদি মেয়েদের শক্তি এবং তাদের চেতনাকে জাগ্রত ও অর্গল মুক্ত করা হয়, তবে পুরুষ জাতের বা পিতৃতন্ত্রের শক্তি এবং আধিপত্য প্রবলভাবে ব্যাহত হবে। তাই আজো সমস্ত মেয়ে জাতটাকে মৌলবাদীরা দাবিয়ে রাখে। মেয়েরা যাতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে না পারে তার জন্যে এই শ্রেণীর পুরুষরা বিশেষত তালিবানরা যথাসম্ভব কঠোর শাসনের গণ্ডি বেঁধে দিচ্ছে। নিজেদের স্বার্থ, কামনা, বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কাল্পনিক নিয়ম কানুনকে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা বলে সবাইকে সন্ত্রস্ত করে তুলছে। মহিলাদের সমান অধিকারের ক্ষেত্রে, বিশ্বের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রই সমান রক্ষণশীল। ইসলাম ধর্ম শাস্ত্র এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এখানে যা দেখছি বা বি.বি.সি খবরে রেডিওতে যা শুনছি, তাতে মনে হয় তালিবানরা ইসলাম ধর্মকে কলঙ্কিত করছে। সমগ্র মানুষের মনে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ভয়ের সৃষ্টি হচ্ছে।
কোরান শরীফের নির্দেশ বলে তালিবানরা যা করছে বা রটাচ্ছে তা সত্য নয়। কোরান শরীফের কোথায় লেখা আছে, যদি কেউ নামাজ না পড়ে তবে তাকে ধরে মারতে হবে? দাড়ি না রাখলে হাত, পা কেটে দিতে হবে? কোরানের কোথায় লেখা আছে যে চুল মুখে এসে পড়লে নামাজ হবে না? কোথায় লেখা আছে যে পুরুষহীন সংসারে বাড়ির মহিলারা চাকরি, ব্যবসা বা অন্য কোনও পেশাকে অবলম্বন করে সংসার চালাতে পারবে না? তবে কি পুরুষহীন সংসারের সবাই না খেয়ে মরবে? নাকি আত্মহত্যা করবে? তালিবান জল্লাদেরা কারুর মুখে অন্ন জোগানোর দায়িত্ব নেবে না। যারা আত্মহত্যা করবে তাদের সেই মহা পাপের ভাগও নেবে না। যাদের কোনও দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা নেই তারা কোন স্পর্ধায় মেয়েদের সব রকম অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের কোরানের নিষেধাজ্ঞার গণ্ডি টেনে দিচ্ছে? মানবতার অপমান করছে, মুসলিম জাতকে হেয় করছে? তালিবানরা মেয়েদের ওপরও অত্যাচার করছে। রাস্তায় মেয়েদের ধরে মারধোর করছে। এরাই কি নামাজি? যাদের অন্ন দেবার ক্ষমতা নেই, তারা কোন অধিকারে অন্ন কেড়ে নেয়? আমার ইচ্ছে করে তালিবানের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে। আঘাতের পরিবর্তে আঘাত হানতে। এক জোট হয়ে বলতে ইচ্ছে করে তালিবান হটাও। ধর্মান্ধরা দূর হও, আমাদের বাঁচতে দাও। অধিকার দাও। সারা বিশ্বে যখন নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে নরনারী নির্বিশেষে ক্ষমতার জোরদার লড়াই চলছে, সেখানে কেন চুপ করে থাকবে আফগান জনগণ? অফগান নারী?
অষ্টম অধ্যায়
আজ মঙ্গলবার। কাল আমি এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। এখান থেকে সোজা হিন্দুস্তানে যাওয়া যাবে না। তাই পাকিস্তান যাবো বলে ঠিক করেছি। কাবুলে এখন যুদ্ধ হচ্ছে, তাছাড়া কাবুলের থেকে পাকিস্তান অনেক উন্নত। দেশের শাসন আছে। নিয়ম কানুন আছে। কাউকে মারলে তার শাস্তি আছে। কোনও মহিলার ওপর অত্যাচার করলে পুলিসের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যার কোনটাই আফগানিস্তানে নেই। যখন খুশি যে ভাবে খুশি কাউকে মেরে ফেলা যায় এখানে। আফগানিস্তানে একটা মানুষের ততটাই মূল্য যতটা একটা মুরগীর। এখানে মানুষের চেয়ে একটা গাধার দাম অনেক বেশি। আফগানরা গাধাকে খুব যত্ন করে কারণ গাধাতে চড়ে বেড়ানো যায়। গাধার পিঠে করে মাল বওয়া যায়। এই তো সেদিন, মাত্র মাস চারেক আগে জলিলকে গুলি করে মেরে ফেলে দিয়ে গেল ওর চাচার ছেলে। সামান্য ব্যাপার। জলিলের কাছে শরিফ বলেছিলো জলিলের চাচার ছেলের নাম শরিফ। জলিল, তোর একটা আঙুরের বাগান আমার গমের বাগানের সঙ্গে বদল কর। জলিল তাতে রাজি হয়নি। তখন একদিন বিকেলে শরিফ জলিলকে বলল, চল, জঙ্গলে বাজপাখি শিকার করতে যাবো। এখানে প্রায়ই কেউ না কেউ বাজপাখি ধরতে যায়। তাই জলিলও রাজি হয়ে গেল। নিজের চাচার ছেলে অবিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। আনন্দে ভাইয়ের সঙ্গে শিকারে যাচ্ছে। বিবিকে বলল পাতিরা করে প্যাকেটে দিয়ে দিতে। পাতিরা হচ্ছে আটা দিয়ে বানানো একটা বড় চাকির মতো জিনিস। আটা, ঘি, চিনি দিয়ে মেখে বানাতে হয়। জলিলের বিবি কিন্তু বলেছিল কি দরকার শরিফের সাথে শিকারে যাওয়ার? শরিফ ছেলেটা ভালো নয়। কিন্তু নিয়তি বাধা মানবে কেন? জলিলও কারো কথা শোনেনি। সেজেগুজে বেরিয়ে গেছে শরিফের সঙ্গে। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় জলিল ভাবতেও পারেনি আজ কোনও ঘটনা ঘটতে পারে। প্রায় দশ মাইল রাস্তা পেরিয়ে একটা বাঁক। সেই বাঁকের মুখে একটা খালি গুমটি ঘরের মতো আছে। সেখানে এসে শরিফ দাঁড়ালো। তারপর কী ভাবে যে জলিলকে সে মেরেছে তা বলতে পারব না। পরের দিন যখন জলিলের লাশটা সবাই বাড়িতে নিয়ে এল, সেই মরদেহ চোখে দেখা যায় না। খবরটা শুনে আমি গিয়েছি ওদের বাড়িতে। তখনো জলিলের দেহ বাড়িতে আনেনি। জলিলের বৌ রহিসা আমাকে ধরে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। ছোটো ছোটো তিন মেয়ে এবং এক ছেলে জলিলের। তারা কিছু না বুঝতে পেরে মায়ের কান্না দেখে কাঁদতে লাগল। বাড়ির সবাই কী বিলাপ যে করছে। সে বিলাপে হয়ত খোদার আসনও একটু নড়েচড়ে উঠেছে বলে মনে হয়। এমন সময় একজন এসে খবর দিল সবাই চুপ কর, জলিলকে নিয়ে আসছে। জলিলের আগমন বার্তা বহনকারি যেমন দৌড়ে এসেছিল ঠিক অেনি ব্যস্ততার মধ্যেই বেরিয়ে বাইরে চলে গেল। এবার বাড়ির সবাই আরো জোরে কাঁদতে লাগল। আমিও ওদের সঙ্গে কান্নার সঙ্গী হলাম। না কেঁদে কি উপায় আছে। কদিন আগেও তো আমি জলিলের গাওয়া গান শুনেছি। আমি হিন্দুস্থানি বলে জলিল বেশ আগ্রহের সঙ্গে আমাকে খুশি করার জন্যে হিন্দি গান গেয়েছে। মেরে আঙ্গনেমে তুমারা কেয়া কাম হ্যায় পরদেশি মেরা দিল লে গ্যায়া। আরো অনেক। সে আর কোনদিন আমাকে খুশি করার জন্যে গান গাইবে না। কাঁদছে, সবাই কাঁদছে। উঠোনের ঠিক মাঝখানে একটা খাটের ওপর জলিলকে শোয়ানো হয়েছে। সমস্ত শরীর তার ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। কম করেও তিরিশটা গুলি চালিয়েছে। কী নিষ্ঠুর! কী নির্মম! এইভাবে কেউ কাউকে হত্যা করতে পারে? এই দেশের মানুষের মধ্যে কি একটুও দয়া মায়া নেই? সামান্য জমির জন্যে একটা মানুষের জীবন নিতে একটুও হাত কাপল না? কী দাম তবে জীবনের?
চলে গেল জলিল। একটা জ্বলন্ত প্রদীপ হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় নিভে গেল। আর জলিলের বিবি? তার কথা পরে হবে। এখন বরং দেখা যাক কী ভাবে পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করি।
যে একজনের কথা আমি ভেবেছিলাম সে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিল একটা গাড়ি ঠিক করে দেবে এখান থেকে তামির পর্যন্ত। আমার সঙ্গেও সে তামির অবধি যাবে তারপর আমাকে একাই যেতে হবে। আমি আর অমত করলাম না অমত করলে যদি এইটুকু ব্যবস্থাও না করে?
আমি তাকে গাড়ি নিয়ে বুধবার সকাল আটটার সময় আলেকদারি বলে একটা জায়গায় দাঁড়াতে বললাম। আজ মঙ্গলবার। আগামী কাল আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত দিন বুধবার। আলেকদারির ফকিরকালা গ্রামে আমার ননদের বাড়ি। ননদ এখন কাবুলেই থাকে। আমি প্রায়ই ননদের বাড়ি বেড়াতে যাই। এবং দশ দিন পনেরো দিন করে থাকি। কেউ আমার খোঁজও নিতে যায় না।
বেশ কিছুদিন ধরেই কথা চলছিলো ননদের সঙ্গে আমি আবার পনেরো দিন গিয়ে ওর বাড়িতে থাকব। কারণ ওর বাচ্চাদের জন্যে জামা সেলাই করব মেশিনে। কিন্তু যাবো যাবো করেও যাওয়া হচ্ছিল না। হবে কি করে? আমি তো এদিকে ওই লোকটার জন্যে অপেক্ষা করছি। সে এসে আমাকে সঠিক কথা দেবে, যে কবে আমাকে একটা গাড়ি ঠিক করে দেবে। বাড়িতেও সবাই জানে আমি ননদ গুনচার বাড়ি যাবো যে কোন দিন। যখন লোকটা আমাকে দিনক্ষণ বলে সব ব্যবস্থা করে গেলো তখনই ঠিক করে নিলাম যে এবার কী ভাবে আগের দিন আমি বাড়ি থেকে বেরোতে পারি। অথচ গুনচার বাড়িতেও যেতে হবে না। বুধবার আটটায় গাড়ি। সুতরাং বুধবারেই বেড়িয়ে গাড়ি ধরা অসম্ভব। প্রথমত অনেক ভোরে বেরোতে হবে। পুরো দুঘণ্টা হেঁটে গেলে তবেই পড়বে আলেকদারি। তাই যে করেই হোক আগের দিন বেরিয়ে অন্য কোনও বাড়িতে থাকতে হবে। পরের দিন যাতে ভোরে গুনচার বাড়ি যাওয়ার নাম করে সেখান থেকে বেরোতে পারি। আমি হাতিয়ার হিসাবে গুলগুটিকে ব্যবহার করলাম। ওর বোন বদ্রির বাড়ি রস্তুলখেল। যেখান থেকে আলেকদারি মাত্র দশ মিনিটের পথ। গুলগুটি আমার মনের কথা কিছুই বুঝতে পারল না। না বুঝেই খুশিতে সে তৈরি হয়ে নিল বোনের বাড়ি বেড়াতে যাবে বলে। দেওররাও অমত করল না। অমত করার প্রশ্নই ওঠে না। এমন একা আমি এর আগেও গুনচার বাড়িতে গিয়েছি। আমি একটা আফগানিস্তানের মেয়েদের পোশাকের মতো পোশাক তৈরি করে রেখেছি এই পালিয়ে যাওয়ার দিনটার জন্যেই। পাঞ্জাবি পোশাক দেখলে সবার সন্দেহ হতে পারে বলে। সেই পোশাকটা পরে নিলাম। তিন্নির জন্যেও একই রকম বাচ্চাদের পোশাক বানিয়েছিলাম। সেটা ওকে পড়িয়ে নিলাম। ইন্ডিয়া থেকে জাম্বাজ আমার জন্যে হাত খরচার টাকা পাঠাতে। তাছাড়া আমার নিজের টাকা, সব মিলিয়ে আফগানি চার লাখ টাকা। সেই টাকাগুলো কোমরে বেঁধে নিলাম। তারপর বাড়ি থেকে বাইরে পা রাখলাম। একটা ভয়, উল্কণ্ঠা, তার সঙ্গে মুক্তির আনন্দ। মনের মধ্যে বুকের ভিতর কেমন যেন একটা অস্থিরতা, যেমন ভীষণ আনন্দে হয়, ঠিক তেমনি হচ্ছে। সমস্ত রাস্তা গুলগুটির সঙ্গে অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে লাগলাম। আমার এত খুশির ভাগীদার কাউকে করতে পারছি না বলে একটা চাপা দুঃখ যেন আমাকে পেয়ে বসল। অহেতুক রাস্তার ধারে বসে পড়লাম। গুলগুটিকে টেনে বসালাম। কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, আমি ফাঁকা রাস্তায় গলা ছেড়ে গান ধরলাম ও আমার দেশের মাটি। এটা শেষ করে আবার একটা করলাম ভারত আমার ভারতবর্ষ। সবকিছু যেন আজ অনেক ভালো লাগছে। খুব যন্ত্রণা থেকে আজ আমি নিজেকে যেন আলাদা করে বাঁচার স্বাদ দিতে লাগলাম।
বেলা দুটো বাজে। আমরা বদ্রি আকিইর বাড়ি পৌঁছলাম। বদ্রি জাম্বাজের পিসির বড় মেয়ে। বদ্রিকে সবাই আকিই বলে। আমিও তাই আকিই বলে ডাকি। বদ্রি তো আমাদের দেখে খুশিতে জড়িয়ে ধরল। তারপর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁহাতে একটা বেশ বড় ঘর। পুরোনো আমলের ঘর। কোনও জানালা নেই। ঘরে দেওয়ালের ওপর দিকে একটা ছোটো কাঁচ লাগানো। ওই কাঁচকে ভেদ করে যতটুকু আলো আসে তাতেই ঘর সামান্য আলোকিত হয়। পুরোনো দিনের সব ঘরই এইরম। এখন নতুন বাড়ি যারা বানাচ্ছে তারা সবাই ঘরে বড় বড় জানালা রাখে। বদ্রি আমাদের বসিয়ে তারপর খাবার ও চা আনতে গেল। বদ্রির মেয়ে বেনেজিরও মাকে সাহায্য করতে গেল। আমার তো খেতে ইচ্ছেই করছে না। তবুও কিছু খেতে হবেই। বদ্রি একটা কানা-উঁচু প্লেটে করে চারটে ডিম পোচের মতো করে নিয়ে এল, গাওয়া ঘিয়ের মধ্যে পোচগুলো ডুবে আছে। আর দুটো সাদা চিনে মাটির বাটিতে করে দিল দই। আমি গুলগুটি, তিন্নি, কিসম ও শবেরা সবাই মিলে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে লাগলাম। কিসম ও শবেরা গুলগুটির মেয়ে। কিমৎ বড়, বছর আটেক বয়স, আর শবেরা ছোটো এই বছর তিনেক বয়স হবে। খাওয়া-দাওয়ার পর বসে বসে নানারকম সুখ-দুঃখের গল্প করতে লাগলাম। বদ্রি আমাকে অনেকবার ধন্যবাদ জানালো গুলগুটিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্যে। স্বামী তার থেকেও নেই। সংসার থেকে তাকে বিদায় দিয়েছে। বাবা মা মারা গেছে, ভাইরা তাদের সংসারে বোনকে রেখে অশান্তি বাড়াতে চায় না। এক জন তো না? তিনজনের ভার, কে নেবে? গুলগুটি আমার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। দুঃখ ছাড়া তার জীবন থেকে আর কিছুই পাওয়ার নেই। সারাদিন আমাদের সংসারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, তাতেও আমার দেওররা তাকে নিষ্কৃতি দেয় না। মারধোর তো আছে, আর আছে না খেতে পাওয়ার কষ্ট। আমার দেওররা গুলগুটির দুই মেয়েকে একটু দুধের চা অব্দি দেয় না। দেওররা যখন সকালে বসে চা খায় তখন কিসম ও শবেরা, ওদের সামনে একটুকরো শুকনো রুটি নিয়ে বসে অপেক্ষা করে, কখন চাচারা তাদের একটু শেরচা দেবে। এখানে দুধের চা-কে শেরচা বলে। কিন্তু আমার দেওররা এত নির্মম যে পৃথিবীতে এর বিকল্প পাওয়া যাবে না। নিজেরা ও নিজেদের বাচ্চাদের যখন খাওয়া হয়ে যাবে তখন কেটলিতে একটু চিনি ও জল দিয়ে নেড়ে চেড়ে ওই দুধের শিশু দুটোকে কাপে ঢেলে দেবে। রংটা ঘোলাটে দুধের রং-এর মতোই হয়। কিসম ও শবেরা তাই-ই খেয়ে নেয়। গুলগুটি তখন ঘরের কোণে বসে অঝোরে কেঁদে চলে। তার কান্নাই এখন চলার পথের সাথী। বদ্রি এই জন্যেই খুশি হয়েছে ওদের নিয়ে এসেছি বলে। অন্তত একটা দিন তো একটু ভালো কিছু খেতে পারবে। নিজেকে আমি নিজেই ভীষণ আঘাত করতে লাগলাম। এই অসহায় মহিলাকে আমি কি সত্যিই বেড়াতে নিয়ে আসতে পারতাম না, যখন আমার সময় ছিল তখন তার কথা মনে পড়েনি। আজ বেড়ানোর জন্য নয়, আমি আমার স্বার্থে তাকে হাতিয়ার করে নিয়ে এসেছি।
ভোর চারটে। বদ্রি ও গুলগুটি উঠে অজু বানাতে গেছে। তারা এবার নামাজ পড়বে। আমিও উঠে পড়লাম। আমাকে উঠতে দেখে ওরা বলল, এখুনি কেন উঠলে? নামাজ পড়বে?
মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে গেলো একটা মিথ্যে–হ্যাঁ। ওরা বেশ অবাক হয়ে বলল, সুমতি হয়েছে তবে? এসো-এসো অজু বানিয়ে নাও। আমি বেশ অসোয়াস্তিতে পড়লাম। হ্যাঁ যখন বলেছি তখন নামাজ আমাকে পড়তেই হবে। নামাজ পড়বো বলে অসোয়াস্তি নয়…. অসোয়াস্তি আল্লার নামে পড়া নামাজকে কেন্দ্র করে মিথ্যে বলে নিজের কার্যসিদ্ধি করছি ভেবে। আমি এত জঘন্য মনের হতে পারি অতীতে কোনদিন তা ভাবতে পারিনি। ঈশ্বরকে নিয়েও ছেলেখেলা করছি। মনে মনে বেশ কয়েকশো বার আল্লার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। প্রথমে অবশ্য বার বার বলেছি ভগবান তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তারপর হঠাৎ মনে হলো, এখানকার লোক তো সবাই আল্লা বলে। সুতরাং সবার আল্লা বলার মাঝে ভগবান বললে যদি আল্লা বুঝতে না পারে আমি কাকে বলছি কথাটা? গুলিয়ে ফেলে? তাই আবার ভগবান ছেড়ে আল্লাকেই অনুরোধ জানালাম। দুর ছাই। আমার বোধ বুদ্ধিও লোপ পেয়ে গেলো! আল্লা, ভগবান, ঈশ্বর, গড়, সবই তো এক। কোনও প্রভেদ নেই। মানুষরা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যেই ঈশ্বরকে নামে নামে ভাগ করে নিয়েছে। একটা আকাশের চাঁদ কি দশটা? নিশ্চয়ই তা নয়। কিন্তু মানুষ তাকে অনেক নামে ডাকে। কেউ চাঁদ বলে, কেউবা মুন বলে, আবার কেউ বলে চঁন্দা, এখানে স্পাঙ্গি বলে। এই ভাবেই ঈশ্বরকেও নানা নামে ভাগ করে নিয়েছে। মানুষ আসল কথা ভুলে গিয়ে নানা রকম নাম গড়া জাতে, ধর্মে, নিজেদের বিভক্ত করে নিয়েছে। একই মায়ের সন্তান, কেউ আর্য হয়েই রইল আর কেউবা অনার্য হয়ে গেল। রক্ত কিন্তু একই। আর সেই অপদার্থ সন্তানকে পৃথিবীর আলোয় প্রস্ফুটিত করার লজ্জায় মুখ লুকালেন সৃষ্টিকারী ঈশ্বর। যিনি নিরাকার। যার ক্ষমতা অপার অসীম। এত জেনেও মূর্খের মতো ভাবার জন্যে আবার একবার নিজেকে ধিক্কার দিলাম।
অজু করে ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লাম। ঈশ্বরের হয়তো এটাই ইচ্ছা যে আমি এখান থেকে তার নাম করে রাস্তায় পা রাখি নামাজ তোক আর পুজোই হোক সবই ভগবানকে ডাকা। নামাজ পড়ার পর বদ্রি আমাদের জন্যে চা নিয়ে এল। আমি তিন্নিকে ডেকে তুললাম। গুলগুটি আমাকে বলল, কেন এখুনি ওকে তুলছি? এখনো তো ভালো করে দিনের আলো ফোটেনি? আমি মুখে কিছু বললাম না। ওকে তুলে বললাম যাও বেনেজির তোমাকে মুখ ধুয়ে দেবে। ততক্ষণে বেনেজিরও উঠে মুখ ধুয়ে আমাদের সঙ্গে চায়ে যোগ দিয়েছে। চা-পরোটা খেয়ে নিয়ে আমি এবার গুলগুটিকে বললাম, আমি আর বসবো না, যাবো। অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে।
গুলগুটি আমাকে হঠাৎ অবাক করে দিয়ে কেঁদে বলে, আর হয়তো তোমার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে না তাই না?
আমি একটু হতভম্ব হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। আমি বুঝতে পারছি তুমি আজ যে যাচ্ছো তা আর ফিরে আসার জন্যে না।
আশ্চর্য! যাকে এতদিন বোকা, কিছু বোঝে না, নির্বোধ বলে জেনে এসেছি সেই মেয়েটা… তুমি কি করে বুঝলে আমি আজ মুক্তির স্বাদ পেতে চলেছি?
ও আমার দিকে তাকালো। তারপর আস্তে আস্তে যা বলল তা হল, তোমার আনন্দ ও তোমার অহেতুক অনেক কথা বলা, এবং বদ্রির বাড়ি এসে রাত কাটানোই আমাকে বুঝতে সাহায্য করেছে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছো।
এটা ও ঠিকই বলেছে। আমি নিকট আত্মীয় ছাড়া অন্য কারো বাড়িতে আজো রাত্রিবাস করিনি। আর হ্যাঁ, একটু বেশিই আনন্দ প্রকাশ করে ফেলেছি। কিন্তু তা বলে গুলগুটি যে ধরে ফেলবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।
মনে পড়লো আমার বাবার কথা। বাবা বলতেন, কোন সময় নিজেকে কারো থেকে বেশি চালাক ভাববে না। সব সময় মনে রাখবে অপর পক্ষ বেশি চালাক বা অনেক শক্তিমান।
কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। অবশ্য গুলগুটি আমাকে বাধা দেয়নি। বরং আমার সঙ্গে আলেকদারি পর্যন্ত যাবে বলল। আমরা বদ্রির বাড়ি থেকে ঠিক পৌনে সাতটায় বেরিয়ে পড়লাম। বদ্রির বাড়ির কাছ থেকে হেঁটে আলেকদারি মাত্র আধ ঘণ্টা সময় লাগে। আবার সেই ঢিপঢিপানি শুরু হলো বুকের মাঝখানটায়, বুক থেকে গলা অবধি কেমন যেন চঞ্চলতা কি অন্য কিছু একটা হতে লাগল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল। হৃদয়ের টিটিক্ আওয়াজ কানে আসছে। মন অস্থির হল। বার। বার পিছন ফিরে দেখতে লাগলাম আমাদের চেনাশোনা কেউ বা দেওররা কেউ এদিকে আসছে কিনা। আমার যখন এমন অবস্থা ঠিক তখন রাস্তার মাঝে আমাদের সামনে ধূমকেতুর মত হাজির হল রম্মাজান। আমার নাই। সর্বনাশ। গুলগুটি এখন কি হবে? গুলগুটিও ভয়ে কাঁপছে। যদি জানতে পারে আমি পালিয়ে যাচ্ছি, আর গুলগুটি আমাকে গাড়িতে তুলে দিতে যাচ্ছে তবে … না আর ভাবতে পারছি না। বুকের ভিতরটা কেমন সব ফঁকা। চোখের সামনে যেন সব অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে। একটা কান্নার রেশ গলার কাছে আটকে আছে। কান্নাটা বেরোতে চাইছে কিন্তু বেরোতে না পেরে গলার কাছে গুমরাচ্ছে। কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে নন্দাইকে বললাম, আরে রম্মাজান ভাইয়া তুমি? আমি তো তোমার বাড়িতেই যাচ্ছি।
-আমিও তো তোমাকে আনতে যাচ্ছিলাম। শাওয়ালি কাল রাত্রে আন্দার গিয়েছিল ডিম আনতে, ফেরার পথে রাত হয়ে গিয়েছিল বলে আমাদের বাড়িতে চলে এসেছিল। শাওয়ালিই বলল তুমি বদ্রির বাড়িতে রাত্রে থেকে সকালে আমার বাড়িতে আসবে। তাই তোমাকে বদ্রির বাড়ি থেকে আনতে যাচ্ছিলাম।
-গুলগুটি বদ্রির বাড়িতে এল দেখে আমিও চলে এলাম। ভাবলাম এতটা পথ একবারে না গিয়ে বদ্রির বাড়ি রেস্ট নিয়ে তারপর তোমার বাড়ি যাবো।
-গুলগুটি কোথায় যাচ্ছে এখন? আমার বাড়িতে?
-না, আমি শাশুড়ির কবরে যাচ্ছি। সাহেব কামাল একা আসবে তাই এক সঙ্গেই চলে এলাম।
আমি আবার গুলগুটিকে বাহবা না জানিয়ে পারলাম না। সত্যি, কী উপস্থিত বুদ্ধি ওর। এদিকে আমার চিন্তা হচ্ছে কি করে আমি রম্মাজানকে কাটাব। কেমন করে আমি গিয়ে গাড়িতে উঠব। তবে কি আমি যেতে পারব না? আমার সব আশা এই ভাবে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে? হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল। রম্মাজানকে আমার হাত মেশিনটা বাড়ি থেকে আনতে বললে কেমন হয়? রম্মাজানকে হঠাতে পারলেই আমি পালাতে পারব নতুবা সব ইতি। তাই রম্মাজানকে বললাম
-ভাইয়া, একটা কাজ করতে হবে আপনাকে।
-কি কাজ? রম্মাজান আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম।
-আমার বাড়িতে যান। আমি সাদগিকে বলে রেখেছি আপনি গেলেই আমার মেশিনটা ও আপনাকে দেবে। আপনি মেশিনটা সাইকেলের পেছনে বেঁধে নিয়ে চলে আসুন। মুখে বললাম সাদগিকে বলে রেখেছি মেশিনের কথা কিন্তু এটা যে কত বড় মিথ্যে তা আমার থেকে ভালো আর কে জানবে?
-কাল আনলে হবে না? আমি তবে এখন একটু মক্তবে ডাক্তারের কাছে যেতাম। ভীষণ কাশি হয়েছে। সে অনুমতির অপেক্ষা করছে।
-বেশ, তবে আজ মক্তাবেই যান। কাল মেশিন আনবেন। মনে মনে ভাবলাম এর থেকে সুন্দর প্রস্তাব আর কী হতে পারে। এখান থেকে মুক্তাব যেতে আসতে কম করেও চার ঘণ্টা সময় লাগবে। ততক্ষণে আমি গরদেশ ছাড়িয়ে চলে যাবো। চার ঘণ্টা পরে রম্মাজান বাড়ি এসে যখন দেখবে আমি নেই, তখন আর এদের বুঝতে বাকি থাকবে না ঘটনা কী ঘটেছে। তবুও রম্মাজান একা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। আবার আমার বাড়ি যাবে। আমার বাড়িতে যেতেও এক ঘণ্টা সময় লাগবে সাইকেলে। অবশ্য তারপরে গাড়ি নিয়ে সবাই বেরিয়ে পড়বে। আমি তখন খোস্ত শহরে পৌঁছে যাবো। আর রাতে রম্মাজানরা খোস্তে যেতে পারবে না। সকালে যেতে হবে। আমিও সকালে খোস্ত থেকে মিরামশার গাড়ি ধরব। ওরা যখন খোস্তে পৌঁছোবে আমি তখন মিরামশাতে। এই সময়ের ক্যালকুলেশানের এক চুল এদিক ওদিক হলে আমি নির্ঘাৎ ধরা পড়ে যাবো। আমাকে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে রম্মাজান বললে, সাহেব কামাল, কী এত ভাবছ? যাও তোমরা। চলে যাও আমিও যাই। বেলা হলে আবার গরম লাগবে। রম্মাজান সাইকেলে উঠে চলে গেল। আমরাও আবার হাঁটতে আরম্ভ করলাম। একটুখানি যাওয়ার পর গুলগুটি বলল-কী হবে সাহেব কামাল?
-কিসের কী হবে? রম্মাজান তো চলে গেল। গুলগুটি চুপ করে রইল। দুজনে পাশাপাশি হাঁটছি। কারো মুখে কোন কথা নেই। বুঝতে পারছি ও ভয় পেয়েছে। হয়তো ভাবছে আমার পালিয়ে যাওয়ার পর যদি ওকেই সবাই দায়ী করে যদি বলে ওই আমাকে পালাতে সাহায্য করেছে, একটা অসহায় মেয়েকে এই ভাবে বিপদের মধ্যে ফেলে যেতে আমার বিবেকে বাঁধছে। তবুও আমাকে যেতে হবে। বাঁচার মতো করে বাঁচতে হবে। পিছন ফিরে তাকালে চলবে না। সামনের দিকে এগুতে হবেই।
এখান থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি দূরে একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। আর জিপের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ওই লোকটা। গুলগুটিও দেখছে। এবার আমার সত্যিই ভয় করতে লাগল। আমার সময়ের ক্যালকুলেশান যদি ফেল হয়ে যায়? যদি ধরা পড়ি? নাঃ, আর কিছু ভাববো না। যা হবার তা হবেই। তবুও আমি আর ফিরে যাবো না। এই সুযোগ চলে গেলে আর কোনদিন আসবে না। আমি হাঁটার গতি বাড়ালাম। গাড়ির কাছে এসে গেলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই। এবার গুলগুটিকে বিদায় জানিয়ে আল্লার নাম করে গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি স্টার্ট দিল। ওই লোকটা সামনের সিটে বসেছে। আমি আর তিনি পেছনের সিটে বসেছি। তিনি আমার নয়নের মণি। আমার প্রাণ। উঁচু, নিচু, এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলেছে। হঠাৎ পিছনে একটা মটরসাইকেলের আওয়াজে আমি চমকে উঠলাম। তবে কি আমার ধরা পড়ে যাওয়ার সময় হল? নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হল। হাত পা কেমন অবশ হয়ে গেল। আর কোনও উপায় নেই দেখে আমার সমস্ত শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল। আমি গাড়ির সিটে হাত পা ছেড়ে দিয়ে হেলান দিয়ে বসে রইলাম শেষ দেখার। জন্যে। মটরসাইকেলের শব্দটা আরো কাছে এলো। আমি দেখার জন্যে ব্যাকুল হলাম না। আরো কাছে শব্দ এল আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল।
নবম অধ্যায়
মুক্তি, মুক্তি, এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। একটা কী ভীষণ আতঙ্কের অবসান হল। আমরা যাচ্ছি। আরো অনেক অনেক পথ পিছনে ফেলে এসেছি। আর একঘণ্টা পথ চলার পর আসবে তামির। ওই লোকটা তামির পর্যন্তই আমার সঙ্গে থাকবে বলেছে তারপর আমি একা। এই গাড়িটাও তামির অব্দি যাবে। তামির থেকে অন্য গাড়ি নিতে হবে। এই জিপের লোকটাকে ষাট হাজার আফগানি টাকা দিতে হবে। আর ওই লোকটাকে দিতে হবে এক লাখ আফগানি। মুক্তির পণ হিসাবে এই মূল্য কিছুই মূল্যবান নয়। তেষ্টায় বুকের ছাতি পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তবুও এক মিনিটের জন্যেও গাড়ি দাঁড় করাতে সাহস পাচ্ছি না। কিন্তু পারলাম না। গাড়ি দাঁড় করাতেই হল। কুচি পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া স্বচ্ছ জলের কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ওই লোকটাকে বললাম একটু জল আনতে। লোকটা গাড়ির একটা মগ নিয়ে জল নিতে গেল। আমি সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছি। এমন সময় আমার চোখ পড়ল জিপের ডানদিকের আয়নায়। আয়না দিয়ে অস্পষ্ট দেখলাম একটা সাদা টয়টো গাড়ি আসছে। আমি জানালা দিয়ে মুখ বার করে দেখলাম যে গাড়িটা ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম গফর চাচার গাড়ি। এই গাড়িতে আমি অনেকদিন চেপেছি। এই তো সেদিন নয়িম চাচার ছেলের বিয়েতে বরযাত্রী গেলাম গফর চাচার এই সাদা টয়টাতে চড়ে। গফর চাচার মেজো ছেলে বিসমিল্লাজান গাড়িটা চালিয়েছিল। সুতরাং এই গাড়িটা না চেনার কোনও কারণ হতেই পারে না, গাড়িটা এগিয়ে আসছে। ওই লোকটার কি এখনও জল নেওয়া হয়নি? এখনও যদি গাড়িটা স্টার্ট করা যেত, তো– কিই বা হতো? ওরা আমাকে ঠিক ধরে ফেলবে। আর পারছি না। যা হবার হোক। উৎকণ্ঠা, সংশয়, আতঙ্ক ভয়। আর কত? কতক্ষণ এই সবের মধ্যে সময় কাটানো যায়? মুক্তির সাধ? মুক্তিই নেই তো মুক্তির সাধ। জীবনই যখন নেই তো কিসের মৃত্যুর ভয়? ওই লোকটা গাড়িতে উঠল। আমি আর তিন্নি জল খেলাম। এবার গাড়ি স্টার্ট করল টয়টোর স্পিড় যেন আরো বেড়ে গেছে। যমদূতের মতো আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আসুক। আর আমার একটুও ভয় করছে না। ভয় করতে করতে এমন অবস্থা এখন আমার, সব ভয়কেই আমি জয় করে ফেলেছি। ভয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। টয়টোটা কাছে এসে গেছে। একেবারে আমার পাশে। এবার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আমার। বাব্বাঃ। এতক্ষণ কি ভয়টাই না আমি পাচ্ছিলাম। না, এটা গফর চাচার গাড়ি নয়। আবার একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আর কেউ আমাকে ধরতে পারবে না। শত চেষ্টা করেও পারবে না।
ঠিক এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়েছে। ওই লোকটা টাকা পেয়ে খুশিতে আমাকে গড়দেশ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। নিজে আমার সঙ্গে এসে আমাকে খোস্তের গাড়িতে উঠিয়ে দিয়েছে। একটা টয়টো গাড়ির সামনে ড্রাইভারের পাশের দুটো সিটই আমি ভাড়া করেছি। তিন্নির জন্য একটা সিট না নিলেও চলে। তবু পাশে যাতে আর কেউ বসতে না পারে তাই দুটোই আমি ভাড়া নিয়েছি। গড়দেশ থেকে পুরো চার ঘণ্টা সময় লাগে খোস্ত অবধি। এবার রাস্তা পাকা। কিন্তু পাহাড়ি। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে এঁকেবেঁকে উঠে এসেছে। সমস্ত পাহাড়টা ঘুরে ঘুরে গাড়ি চলেছে। ড্রাইভারটা আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি খোস্তে কোথায় যাবো? আমি যখন বললাম পাকিস্তানে যাবো তখন ড্রাইভারটা বলল, পাকিস্তানে যেতে গেলে সকালে যেতে হবে। কারণ খোস্ত পৌঁছোতে বিকেল হয়ে যাবে। বিকেলে খোস্ত থেকে কোনও গাড়ি পাওয়া যাবে না।
-তবে কি হবে? আমার সাথে কেউ নেই। রাতে থাকবো কোথায়?
-খোর, তুমি ইচ্ছে করলে আমার বাড়িতে থাকতে পার রাতে। সকালে আমি তোমাকে গাড়িতে তুলে দেব। খোর মানে বোন।
-না-না, বরং তুমি আমাকে একটা হোটেল ঠিক করে দিও হলেই হবে।
খোর, হার চা কোরকে, আকপল মোর খোর স্তা। তুম মা খোর ইয়ে। অর্থাৎ, সবার ঘরে মা বোন আছে। তুমিও আমার বোন।
-সে তো নিশ্চয়ই। মুখে বললাম বটে, ঠিক আছে কিন্তু মনে মনে চিন্তা করলাম, যদি এদের বাড়িতে আমাকে জোর করে ধরে রাখে? আমাকে এত দরদ দেখাচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই কোনও মতলব আছে। শেষমেশ টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে, তেঁতুল তলায় বাস করতে হবে? এতদিন তবু নিজের বাড়িতে ছিলাম, এবার কার বাড়িতে যাবো? আমাকে আটকে রাখলে কেউ তো জানবে না আমি কোথায় আছি? তাই ছেলেটিকে বললাম, না, তুমি একটা হোটেলই আমাকে ব্যবস্থা করে দাও।
-কিন্তু খোর, হোটেলে একা তুমি তো থাকতে পারবে না? কারণ তালিবান তোমায় গ্রেপ্তার করবে। তাছাড়া বদমায়েস লোকও তো আছে। আমার বাড়ি শহর থেকে একটু ভেতরে। আমার পিসির বাড়ি বাজারের গায়ে। তুমি সেখানেও থাকতে পার। ও গাড়ি চালাতে চালাতেই আমার দিকে ফিরে বলল কথাগুলো।
আর দ্বিমত করার প্রশ্নই ওঠে না। শহরের ওপর যখন, তখন আটকে রাখতে পারবে না। ড্রাইভারের পিসির বাড়িতে নিয়ে গেল। এমন নোংরা জায়গা বোধহয় আমার জীবনে আমি দেখিনি। বাড়ির প্রত্যেকটি জিনিসে টোকা দিলে ধুলো গায়ে এসে লাগবে। কিন্তু মানুষগুলো খুব ভালো। আমাকে খুব যত্ন-আত্তি করেছে। পিসির ছেলের দুই বৌ। এক বৌ বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছে। আরেক বৌ বাড়িতে আছে। দ্বিতীয় বৌয়ের আগের স্বামী মারা গেছে। তারপর স্বামীর ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে আবার বিয়ে হয়েছে। এই পিসির কাছে বলেছি, আমি বাবার বাড়ি কাবুলে গিয়েছিলাম। এখন পাকিস্তানে শ্বশুর বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। পিসির পাশের বাড়িতে যে কাবুলের লোক আছে তা কী করে জানবো? তারা যখন শুনলো, কাবুলের থেকে একটা মেয়ে এসেছে, তখন আলাপ করতে এল আমার সঙ্গে। আমাকে বলল, কাবুলে আপনার বাবার বাড়ি কোথায়?
-বরিসাত সিনেমা হলের ঠিক পিছনে।ভাগ্যিস হলটার নাম জানা ছিল! আমার এক জায়ের কাকিমার বাবার বাড়ি ওখানে। তাই কয়েক বার হলের নামটা শুনেছি।
-আমাদের বাড়ি ছিল, সাড়ানাও-তে।
-সারানা তো গজনীর পুবে?
–সেটা সারানা, আর এটা সাড়ানাও।
কি বুঝলাম কে জানে। বলে দিলাম–ও।
সবাই চলে যাওয়ার পর আমিও শুয়ে পড়লাম। বিছানা ওরা করে দিয়েছিলো। খাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছে।
মিরামসার বাসস্ট্যান্ডে গাড়ি এসে দাঁড়াল। এখন বাজে এগারোটা। খোস্ত থেকে ভোরে মিরামসার গাড়ি ধরেছিলাম। এবার মিরামসার থেকে যাবো ব বলে আরো একটা শহরে। সেখান থেকে একটা গাড়ি ধরে পৌঁছাবো পুন্ডি। হয়তো এই পুন্ডিতেই আমার যাত্রা শেষ হবে।
পুন্ডিতে যখন পৌঁছলাম তখন সূর্য অস্তাচলে। এবার আমি কোথায় যাবো? আগে আলিপুরে গুনচারা থাকত; সেও তো কবেই দেশে ফিরে গেছে। ইসলামাবাদে জেঠতুতো ভাসুর থাকে। কিন্তু তার ঠিকানা তো জানি না! আর গুজারহাট বলে একটা শহরে দ্রানাইচাচার মেজো ছেলে মিরাউজাল এবং ভাইপো সাওমদ ও জরিপ থাকে। সেখানে তারা একটা টি.ভি ও ফ্রিজের দোকান করেছে। ওদের ঠিকানাও তো জানি না? শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্তে এলাম। গুজারহাট শুনেছি ছোটো জায়গা। সুতরাং ছোটো জায়গায় সবাই সবাইকে চেনে। হয়তো কোনও দোকানে জিজ্ঞেস করলেই পেয়ে যাব। একা, সম্পূর্ণ একা একটা ভিন দেশে ঢুকে পড়েছি। এ দেশের একটা ইট পাথরের সঙ্গেও আমার সামান্যতম পরিচয় নেই। শুধু নিজের বুদ্ধি, সাহস ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে এগিয়ে চলেছি। শেষ কোথায় জানি না। ভালোও হতে পারে, আবার চরম মন্দও হতে পারে। সাহস আমার বরাবরই একটু বেশি। ভয়ের সঙ্গে আমার দোস্তি নেই। যারা ভয় পায় তারা জীবনে কোনও কাজেই জয়ী হতে পারে না। আসলে, আমার ঠাকুরদাদা ও দাদাঠাকুরদুজনেই দুর্জয় সাহসী ও বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। অন্যায় তারা করতেন না এবং অন্যায়কে প্রশ্রয়ও দিতেন না। আমার প্রকৃতিও খানিকটা তাঁদের মতো।
পুন্ডি বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে দাদুর সাহসের কথা রোমন্থন করতে গেলে সারারাত এই বাসস্ট্যান্ডেই থাকতে হবে। তাই ভাবনা ছেড়ে গুজারহাট যাওয়ার বাসে উঠে বসলাম। একদিকে ভয়, ভাবনা, সংশয়। অন্যদিকে নতুন করে বাঁচার একটা ক্ষীণ আশা। সব মিলিয়ে একটা ভীষণ উন্মাদনা মনে ছেয়ে আছে।
হঠাৎ সন্দেহ হল, বাসটা আদৌ গুজারহাট যাবে তো? এমনও তো হতে পারে বাসটা অন্য জায়গায় যাবে? আমার কৌতূহলের অবসান ঘটলো। কারণ, একটু বাদেই শুনলাম, কন্ডাক্টারটা গুজারহাট গুজারহাট বলে চেঁচিয়ে লোক তুলছে। অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলাম, হুট করে বাড়ি থেকে অমনভাবে চলে আসাটা উচিত হয়নি। অন্ধকার ইতিমধ্যেই চারদিকে ঘনিয়ে এসেছে। একটা অজানা ভয় মস্তিষ্কের প্রতিটি স্নায়ুতে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে। যদি আমি সাওমদদের দোকান খুঁজে পাই তাহলে? কি করবো তখন আমি? কোথায় যাবো? কে দেবে আমাকে রাতের আশ্রয়? এই সব নানা রকম চিন্তা করতে করতে সন্ধে সাতটা নাগাদ গুজারহাটে পৌঁছে গেলাম। বাস থেকে নেমে রাস্তা পার হয়েই একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস-এর দোকান। সেখানে গিয়ে একটা কোকাকোলা নিলাম। খাওয়ার আমার মোটেও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু হুট করে একটা অচেনা লোককে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করা যায় না কিছু। ভূমিকার প্রয়োজন। কোকটা খেতে খেতেই দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলাম দাদা, বলতে পারবেন, কাবুল থেকে যিনি এসে এখানে টি.ভি. ও ফ্রিজের দোকান দিয়েছেন তার দোকানটা কোথায়? আমার কথা শুনে ভদ্রলোক আমাকে একবার দেখে নিলেন। এতক্ষণ দেখার তো প্রয়োজন হয়নি। রোজ কত মানুষ তো দোকানে আসে। সবাইকে কি খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব। কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনে উনি আমাকে না দেখে পারলেন না। হয়ত ভাবলেন মেয়েটা নির্ঘাত পাগল। নতুবা এই ভাবে কেউ প্রশ্ন করে।
একটা গা-শিরশিরে আওয়াজে ফিরে তাকালাম। কোলড্রিংক-এর দোকানদার আমাকে কি যেন অনেকক্ষণ ধরে বলে চলেছেন। খেয়াল হতেই বুঝলাম যে উনি একজন মোটা বেঁটে খানসাহেবকে ডেকে এনে আমাকে জিজ্ঞেস করতে বলছেন আমি কাকে খুঁজছি।
আমি বেঁটে খানসাহেবের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, তুমি হচ্ছো খানজাতের কলঙ্ক। কোনও আফগানের এমন তো চেহারা হওয়ার কথা নয়? আফগানিস্তানের জল হাওয়া এমন যে, জন্মেই সবাই বড়, লম্বা হয়ে যায়। আফগানী আপেলের মতোই ছোটোখাটো হয়েছে দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা খানসাহেব। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম সাওমদের টিভি-র দোকান চেনে কিনা। খান আমাকে বলল-আমি চিনি না, তবে খুঁজে বার করতে পারব। আপনি এখানে দাঁড়ান। আমি দেখে আসছি। গুজারহাটের এই বাজারটা মুম্বাই-এর সবজি ও মুরগী বিক্রির বাজারের মতো। দুত্তোর মরুক গিয়ে যাক মুরগী বাজার।
নির্মম ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে এখন কিনা মুম্বাই বাজারের কথা ভাবছি। আমার সামনে রুদ্ধদ্বার, ক্ষমতা চাই এখন। বাস্তব পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে একজন মোক্ষম অতি সক্রিয় কাউকে প্রয়োজন।
এই খানের কথায় আমি খুব সন্দিহান হয়ে পড়লাম আমাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে সে চলে গেছে। কি জানি কি হয়। বড় রাস্তা দিয়ে ক্রমাগত গাড়ি যাচ্ছে আর সেই গাড়ির কর্কশ আওয়াজ আমার কানে এসে ধাক্কা মারছে। স্বপ্নেজ্জ্বল গুমটি দোকানের লোকগুলো হাঁকাহাঁকি করে তাদের পসারের বিজ্ঞাপন করছে। অনেক মানুষের পদপাতের শব্দে মুখরিত এই জায়গাটা। ধোঁয়া দুর্গন্ধে ভরা গুমোট আবহাওয়া।
আমার সমস্ত চিন্তার সমাধান করবে ওই খানটা কিন্তু সে এখনো আসছে না কেন? তবে কি সাওমদকে বা তার দোকান খুঁজে পাইনি? এদিকে রাত ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। দুর্বিষহ এক যন্ত্রণা আমার মাথাটা যেন ফাটিয়ে দিচ্ছে। চূড়ান্ত এক বিপদের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে যখন ভাবছি অতঃপর কর্তব্য, তখন বেঁটে খানটা ফিরে এসে বলল–পেয়েছি, দোকান। শান্তি, চিরস্থায়ী শান্তির মতো করে শান্তি ফিরে এল। সর্ববিধ শোষণ থেকে মুক্তি।
পেয়েছি। সাওমদ খানের টিভির দোকান খুঁজে পেয়েছি। আসুন আমার সঙ্গে। বেঁটে খান সাহেবের সঙ্গে যেতে লাগলাম। একটা সরু গলির মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার দুধারে সারি সারি নানা রকমের দোকান। অনেকগুলো দোকান পার হয়ে একটা অন্ধকার দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বেঁটে খান কাকে যেন ডেকে নিয়ে এল।
এই যে ইনিই সাওমদ খান। এ কি? এ লোকটা বলে কি? একটা অন্য লোককে বলে কিনা–
-না, না, ইনি নন। ইনি কেন সাওমদ হতে যাবে? এঁকে আমি চিনিই না।
-তবে আমি আর বলতে পারব না।
সর্বনাশ! এ কি বলে? বলতে পারবে না? তবে? কী হবে এখন? এদিকে রাত নটা বাজে। আমি এখন কোথায় যাবো? আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। গলার কাছটা যেন কেমন কেমন করছে। আওয়াজও বেরুচ্ছে না। তখন ওই দ্বিতীয় খানটা বলল,
-ও না পারুক, আমি দেখছি। আপনি একবার তার পুরো কথাটা বলুন তো? কোথায় বাড়ি? কবে এসেছে?
আমি বলব কী করে? গলার কাছটা কে যেন খুব জোরে চেপে ধরে রেখেছে। তবুও ফাঁসফেঁসে গলায় তাকে আবার সব বললাম। এবার লোকটা বলল-বুঝেছি, আসুন আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি সাওমদের কাছে। আমি চিনি তাকে। লোকটা একটা টয়েটো ভ্যানকে ডাকল। তারপর আমাকে উঠে বসতে বলল। এখন আমি মরিয়া হয়ে গিয়েছি তাই লোকটাকে আর ভয় না পেয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। সে নিজেও উঠে বসল। দুটো তিনটে গলির মুখ পেরিয়ে একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। আগের জায়গাটা থেকে এই জায়গাটা বেশ জমজমাট। আলো ঝলমলে। অনেক লোক যাতায়াত করছে। আমি যখন এই সব দেখতে ব্যস্ত, তখন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সাওমদ। ওকে দেখে আমার মন আনন্দে নেচে উঠল। বুকের ওপর থেকে একটা পাথর যেন নেমে গেল। আমি সাওমদের হাত ধরে কেঁদে ফেললাম। সাওমদ আমাকে চুপ করিয়ে দোকানের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালো। সাওমদের সঙ্গে বরাবরই আমার খুব ভাব। আর ভাব ছিল সাওমদের কাকার ছেলে রোসেন্দারের সঙ্গে। রোসন বলে আমি ওকে ডাকতাম। আমার বিয়ের আগেও রোসন আমাদের বাড়িতে এসেছে। দেখতে খুব সুন্দর ছিল। বয়স বেশি নয়। আমার বিয়ের দুবছর বাদে ওর দাড়ি গোঁফ গজিয়েছে। যখন সবে দাড়ি উঠছে তখন ওর বিয়ে দিল নাদির চাচা। মেয়ে দেখতে খুব সুন্দরী। নাম বাবান। সর্দারখানের মেয়ে।
সাওমদ জাম্বাজকে কলকাতায় টেলিফোন করে কথা বলল। কিন্তু আমি যখন কথা বলতে চাইলাম তখন লাইনটা কেটে দিল। কেমন যেন একটা বিপদের গন্ধ পেলাম আমি। কিন্তু মুখে কিছু বললাম না। দেখাই যাক না কী করে? সাওমদ আমাদের সঙ্গে নিয়ে এবার বাসার দিকে রওনা দিল। একটা গলির ভিতর দিয়ে এসে ডানদিকে ঘুরে বাঁ হাতে বাড়ি। বেশ বড় বাড়ি। দোতলা। এক তলার তিনটে ঘর নিয়ে সাওমদের বাসা। সাওমদ একটা ঘরে নিয়ে বসাল। ঘর থেকে একটা গন্ধ বেরুচ্ছে। তবে গন্ধটা সেন্টের মতো মাতোয়ারা নয়। একটা গা বমি করা আঁঝালো গন্ধ। উপায় নেই। এই বমি-বমি করা গন্ধের মধ্যে আমাকে ও তিন্নিকে থাকতে হবে।
রাতটা কোনরকম কাটিয়ে ভোরে উঠে বসলাম। তারপর ভাবলাম, যাই বাথরুমে গিয়ে স্নান করি। এমনিতেই আমার অভ্যেস, ঘুম থেকে উঠে আগে বাথরুমে যাওয়া, ল্যাট্রিন থেকে এসে দাঁত ব্রাশ করা, তারপর চা খাওয়া। এই ঘরটাতে আমি ও তিন্নি শুয়েছিলাম। পালিয়ে আসার সময় আমি নিজের বলতে কিছুই আনিনি, শুধু তিন্নিকে ছাড়া। কী করে তিন্নিকে ছেড়ে আসবো? তিন্নি যে আমার সন্তান। আমার মনের সবটুকু দিয়ে আমি তিন্নিকে পেয়েছি। তিন্নি ছাড়া আমার জগৎ অন্ধকার। তিনি আমার জীবন। তিন্নি যখন মা বলে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে আমার দুগালে দুটো চুমা দেয়, তখন পৃথিবীর সব দুঃখ ভুলে যাই। তিন্নির ভালোবাসার রং-এ আমি রঙিন হয়ে উঠেছি। আমার মনেপ্রাণে শুধু তিন্নি, তিন্নি, আর তিন্নি। আমি দেখলাম তিন্নি অঘঘারে ঘুমাচ্ছে। আস্তে আস্তে দরজার খিল খুলে পাল্লা ধরে টান দিলাম। কিন্তু দরজা খুলল না। বুঝলাম সাওমদ বাইরে থেকে শেকল দিয়ে রেখেছে। হঠাৎ মাথাটা গরম হয়ে উঠলো। এখানেও আমাকে এরা বন্দী করতে চাইছে? পাকিস্তানের মতো দেশেও দরজায় শেকল দিয়েছে? হঠাৎ একটা চিন্তা আমাকে ভীষণ ভাবে দুমড়ে মুচড়ে দিল।
আমার ননদ গুনচার ছোটো জায়ের বোনকে একটা আফগান ছেলে এই পাকিস্তান থেকেই কিডন্যাপ করে আফগানিস্তানে নিয়ে চলে গেছে। গুনচার ছোটো জায়ের নাম রসিদ। রসিদার মার নাম বিবিসা। বিবিসার অনেকগুলো বিয়ে। বিবিসার বাড়ি পন্ডিতে। প্রথম স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে। প্রথম পক্ষের একটি মেয়ে ও একটি ছেলে। বছর দুয়েক যাওয়ার পর আরো দুই মেয়ে হল সেই সঙ্গে স্বামীও বদল হল। এবার তৃতীয় বিয়ে। বছর দুয়েক যাওয়ার পর ফের স্বামী বদল। একটা মেয়েও হল। এবার বিয়ে করল এক পাঠানকে। কাবুলে তার বৌ আছে। সেই বৌয়ের এক ছেলে। স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে শুনে প্রথম বৌও পাকিস্তানে স্বামীর কাছে এসে হাজির হল। এবার বিবিসা সতীনের ওপর অত্যাচার শুরু করল। অত্যাচার, অনাহার সহ্য করতে না পেরে বিবিসার সতীনের ছেলেটা মরে গেল। স্বামীকে এখন এমন তুকতাক করেছে যে স্বামী তার প্রথম সন্তানের দিকে ফিরেও তাকায় না।
এক ঝড় জলের রাতে, বিবিসার সতীন ইহ জগতের মায়া কাটিয়ে পরপারে পাড়ি দিল। এবার আর দুবছর নয়, পাক্কা চারবছর ঘর করে, একটা ছেলে ও মেয়েকে জন্ম দিয়ে বিবিসা স্বামী বদল করল। এই বিবিসার বড় মেয়েই হচ্ছে রসিদা– গুনচার ছোটো জা। রসিদার পরের বোন রোসেনা। রোসেনাকে বিবিসা বিয়ে দিয়েছিল আফগানিস্তানের পাঠান ছেলের সঙ্গে। ছেলের বাড়ি ছিল সুরদেওয়ালে পাহাড়ের গায়ে। স্বামী তার স্ত্রী রোসেনাকে দেশে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু বিবিসা যেতে দেয় না। এই ভাবে ঠাণ্ডা লড়াই চলতে চলতে একদিন রোসেনাকে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ খাইয়ে, একটা টয়েটো ভাড়া করে, আটক দরিয়া বর্ডার পাস করে একেবারে সুরদেওয়াল নিজের গ্রামে নিয়ে চলে গিয়েছিল।
আমার ভাবনাটা ঠিক এখানে এসেই থেমে গেল। আমাকেও যদি তাই করে? অতএব ঠিক করলাম, সাওমদের দেওয়া কিছুই আমি খাব না, আমি দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলাম। তিন্নির ঘুম ভেঙে গেল। ও হকচকিয়ে ঘুম চোখে মা বলে কেঁদে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি তিন্নিকে কোলে তুলে নিলাম। ও ভয় পেয়েছে দেখে আমি ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। ততক্ষণে সাওমদ এসে দরজা খুলে দিয়েছে। আমি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সাওমদকে বললাম-তুই যদি মনে করে থাকি, শিকল দিয়ে আমাকে ধরে রাখবি তবে খুব ভুল করেছিস।
-না না আমি সেজন্যে শিকল দিইনি। সাওমদ বেশ ঘাবড়ে গেছে।
আমি আর কথা না বাড়িয়ে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। তিন্নিকে মুখ ধুইয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে স্নানের জন্যে প্রস্তুতি নিলাম। মাথার ওপরে ঝরনার জল এসে আমার গায়ে পড়ছে। মনে হল আমার সমস্ত গ্লানি, আমার সাত বছরের সব দুঃখকষ্ট এই নকল ঝরনার জলে ধুয়ে যাচ্ছে। তবু সবটাই কি ধুয়ে যায়? ক্লান্তির কিছুটা উপশম হলেও হতে পারে, কিন্তু জীবন? বাস্তব? বাস্তবকে কি করে আমি এই ভাবে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারি?
জাম্বাজ অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মতো কাজ করেছে। প্রথমত, আমাকে এইভাবে এখানে রেখে চলে গেছে। তারপর গতকাল রাতে সাওমদ যখন তাকে ফোনে জানালো যে আমি আফগানিস্তান থেকে অতি কষ্টে পাকিস্তানে এসে পৌঁছেছি, তখন আমার সঙ্গে ওর কথা বলা কি উচিত ছিল না?
স্নান সেরে আমি একটা পরিষ্কার সালোয়ার কামিজ পরে নিলাম। যেটা পরে এসেছিলাম সেটা ছাড়া একজোড়া করে সালোয়ার কামিজ এনেছি। তিন্নির জন্যেও এনেছি। চুলে শ্যাম্পু করেছি শরীরটা এখন বেশ হাল্কা লাগছে। সাওমদ আমার ও তিন্নির জন্যে নাস্তা নিয়ে এসেছে। কিছু না খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাই লুকিয়ে নাস্তা ফেলে দিলাম। এমন সময় এক ভদ্রলোক ও একটি বছর পনেরোর মেয়ে ঘরে ঢুকল। আমি এতক্ষণ খালি মাথায় বসেছিলাম। লোকটাকে দেখে মাথায় দোপাট্টা দিলাম। সাওমদ লোকটার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলসাহেব কামাল, এ হচ্ছে আমার মামা। আর এই মেয়েটা আমার মামাতো বোন। তোমাকে দেখতে এসেছে। তোমার কথা অনেক শুনেছে তাই এসেছে।
আমার আর বুঝতে বাকি রইলো না, ওরা আমাকে ধরে আফগানিস্তানে নিয়ে। যেতে এসেছে? ওই মামাটা আমাকে বলল,
-বেটি, তুমি ঠিক কাজ করোনি।
-কী ঠিক কাজ করিনি? আফগানিস্তান থেকে চলে এসে?
-হ্যাঁ, এতে তোমার বদনাম হবে। ঘাড় নাড়া বুড়োর মতো তার ঘাড়টা নড়ছে।
-হোক বদনাম। বদনামের ভয়ে তো আমার জীবনকে নষ্ট করে দিতে পারি। বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই আমি বললাম।
-জীবন নষ্ট হবে কেন? ওখানে সবাই কত ভালবাসে তোমাকে।
-ভালবাসে? ভালবাসার মানে আপনারা বোঝেন? একটা মানুষকে দুবেলা অন্ন দিলেই কি ভালবাসা হয়ে যায়? মাথা গোঁজার একটু জায়গা দিলেই কি সব কর্তব্য শেষ হয়ে যায়? বিয়ে করে ঘরে এনে ভাইদের কাছে বৌকে ফেলে রেখে গেলেই কি স্বামীর সব দায়িত্ব পালন করা হয়ে যায়?
-না, না, তা কেন? সংসারে রোজগার করার আর কেউ নেই বলেই জাম্বাজ হিন্দুস্তানে পড়ে আছে। কিন্তু তা বলে তোমাকে তো কোন রকম অসম্মান করেনি।
-অসম্মান হতে আর কি বাকি আছে? দিনের পর দিন ওর ভাইরা আমার ওপর অত্যাচার করেছে। গায়ে হাত তুলেছে। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। আমার বাবা মাকে পর্যন্ত গালি দিয়েছে। আমার সামনে বসে ওদের বিবির মুখে দামি দামি মেওয়া তুলে দিয়েছে। আর আমাকে শুধু রুটি আর আলুর তরকারি খেতে দিয়েছে। ওদের বিবিরা আমার সঙ্গে কুকুরের মতো ব্যবহার করেছে। ওর ভাইদের ভয়ে আমি ইঁদুরের গর্তে ঢোকার মতো করে ঘরে ঢুকে পড়তাম। দারুণ ঠাণ্ডায় কেঁপে মরেছি। তবুও একটার বেশি কাঠ আমাকে দেয়নি একটু বেশি আগুন জ্বালাতে মুশাখানের বিবি আমাকে গুনে গুনে চারখানা করে কাঠ দিয়েছে। কালাখারে বৌ মেপে আঙুর খেতে দিয়েছে। বাগানে তালা দিয়ে রেখেছে যাতে আমি নিজের ইচ্ছেয় বাগান থেকে আঙুর আনতে না পারি। ওই দেশে এর থেকে বেশি কিছু পাওয়ার থাকে না। তাই এই কথাগুলোই জরুরি কথা।
-সবই তো বুঝলাম। কিন্তু তবুও তোমার আবার কাবুলেই ফিরে যাওয়া উচিত। লোকটা একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।
-আপনার কথাটা কানে রাখলাম, মনে নয়।
-তুমি এখন রেস্ট নাও, আমি পরে আসব। আপাতত, তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমি আমার মেয়েকে রেখে গেলাম।
লোকটা চলে গেল। আমিও ঠিক করে ফেললাম এখান থেকেও পালাতে হবে। নইলে এরা সবাই আমাকে আবার জোর করে নিয়ে যাবে বাড়িতে। আবার সেই আফগানিস্তান, সেই শরিয়তি, মৌলবাদী শাসন, সেই জঘন্য তালিবান।
দশম অধ্যায়
১৯৯৩-তে তালিবান গোষ্ঠি প্রথমে গজনী এলাকায় মাথা চাড়া দেয়। পেশোয়ার। থেকে কয়েকটা রাস্তা বিভক্ত হয়েছে। একটা রাস্তা কাবুল শহরের দিকে গিয়েছে। কাবুল তখন রাব্বানি তথা আরাকাত পার্টির দখলে। সে রাস্তা দিয়ে তালিবানরা ভেতরে ঢোকার সুযোগ পায়নি। দ্বিতীয় রাস্তা গেছে গড়দেশ শহরের দিকে। গড়দেশ তখন ইঞ্জিনীয়ার গুলবদিনের এক্তিয়ারে। এদিক দিয়েও তালিবানের ঢোকার রাস্তা বন্ধ। বাকি রইল গজনী। এই গজনীর মধ্যেই প্রথম তালিবানদের দেখা গেল।
গজনীর অনতিদূরে উরগুন বলে একটা গ্রাম আছে। এই উরগুনে তালিবানরা অতর্কিতে হানা দেয়। ফলে উরগুনে তালিবানরা জয়ী হয়। এই জয়ের ঘটনা এমন ব্যাপকভাবে রটনা হল যে বিনা বাধায় তালিবানরা গজনীতে দলে দলে প্রবেশ করতে লাগল। গ্রামেগঞ্জে সবাই বেশ গর্বের সঙ্গে বলতে লাগল-তালিবানরা খোদ আল্লারসুলের প্রেরিত দূত। যতবার মুসলিমদের ওপর অত্যাচার হয়েছে ততবার আল্লা তাঁর দূত পাঠিয়ে মুসলিমদের রক্ষা করেছেন। আর কাউকেই জান খোয়াতে হবে না। তালিবানরা এসে গেছে। এরাই এবার দেশকে বাঁচাবে।
গজনী শহরের পুবদিকে যে সমস্ত গ্রাম আছে, সেগুলোর মধ্যে প্রধান ভূমিকায় আছে মাদালি। চিফ মিনিস্টার। এখানে বলে কোমান্দান। এই কোমান্দানের পরে আছে–আসাম, রফিক, ফরিদ ও আরো অনেকে। এরা সবাই আরাকাত পার্টির লোক। তালিবান মাদালিকে যুদ্ধে আহ্বান জানাল।
কিন্তু মাদালি ঘোষণা করল–যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। যদি আমরা তালিবানের সঙ্গে যুদ্ধ করি, তবে আমাদের থেকে বেশি মারা যাবে সাধারণ মানুষ। যুদ্ধ করতে আমরা ভয় পাচ্ছি না, কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই আমরা আত্মসমর্পণ করবো। তালিবানরা এবার গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে যেতে লাগল। মমদখেল, মমদখেলের পুবে বাঁদিকে শালাং, ডান দিকে মুশখেল, মুশখেলের দক্ষিণে কাটোয়াজ, উত্তরে ডান দিকে কটুয়াল, সেখান থেকে চারদা, সারানা, জাওলি। চারাদার পুবে মক্তাব। এই মক্তাব হচ্ছে চিফ মিনিস্টার অথবা কোমান্দানের কর্মকেন্দ্র রাইটার্স বিল্ডিং। মক্তাব থেকে একটু উত্তরে পাতানা। পাতানার কথা আগেই লিখেছি। পাতানার পুবদিকে আমার শ্বশুরবাড়ি- শ্ৰাকালা। শ্রীকালার উত্তরে রস্তুলখেল, আন্দার, ফকিরকালা, আলেকদারি। আলেকদারির উত্তরদিকে তামির ও গড়দেশ। গড়দেশের উত্তরে কাবুল, আর দক্ষিণ-পুবে খোস্ত। এই সমস্ত এলাকাই তালিবান অধিকৃত হয়ে গেল। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র তালিবানদের হাতে তুলে দিল। সমস্ত মসজিদের সদর দরজা খুলে দিল। জনগণ ভাবলো এটা একটা ঐতিহাসিক ক্রান্তিকাল। একটা যুগান্তর। আফগানিস্তানের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। তালিবানের সঙ্গে আফগানিস্তানের মৌলানারাও যোগ দিল। জনগণ আনন্দের সঙ্গে বলতে লাগল এবার স্বৈরাচারীরা বিতাড়িত হতে বাধ্য। স্বাধীনতার সূর্য আবার উঠবে আফগানিস্তানের দিগন্তে। তালিবানরা জনগণের এই স্বপ্নবিড়ভরতার সদ্ব্যবহার করতে লাগল। যে মুহূর্তে সমস্ত গ্রাম ও থানা তাদের হাতের মুঠোয় এসে গেল তখন থেকেই তারা নিজ মূর্তি ধারণ করল। হুকুম জারি হল–কোনও লোক নামাজ না পড়লে তার মাথা কেটে ফেলা হবে। দাড়ি না রাখলে ধরে প্রহার করা হবে। মেয়েদের সবাইকে বোরখা পরতে হবে। কোনও মহিলা বাড়ির বাইরে বেরতে পারবে না। কারো বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানে ঢোল বাজবে না। কেউ নাচ, গান করতে পারবে না। প্রতিটি পুরুষকে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে হবে, নইলে ধরে নিয়ে গিয়ে নেড়া করে মুখে কালি মাখিয়ে গ্রামে ঘোরাবে। এমনকি মৃত্যুশয্যায় থাকলেও পুরুষ ডাক্তারকে ডাকতে পারবে না কোনও মহিলার চিকিৎসার জন্যে। এই সমস্ত অত্যাচার নাকি কোরানে লেখা আছে। তালিবান পবিত্র কোরান শরীফের দোহাই দিয়ে যাবতীয় নোংরা, জঘন্য, অমানুষিক অত্যাচার করে। আর সেই সঙ্গে অবমাননা করেছে কোরান শরীফ ও ইসলাম ধর্মেরও। তালিবানের অত্যাচারের পর সমস্ত মানুষ কি ইসলাম ধর্মকে ভয় পাবে না? ভাববে, কোরান মানেই ভয়ঙ্কর, পৈশাচিক? শরিয়ত মানেই কেবল শাসন ও শোষণ? কোরানের দোহাই দিয়ে, নামাজের দোহাই দিয়ে তালিবানরা যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করছে এমনকি মেয়েদের গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করছে না, তার পরিণাম কি কেউ ভেবে দেখেছে? কেউ কি বলবে–
আ-তিনা পিত দুনিয়াস্নাতমপিল, আখেরাতে স্নাতন ওয়াকিনাজাবনার। এর অর্থ আল্লা এক ও অদ্বিতীয় এবং নরকের যন্ত্রণা থেকে তিনিই বাঁচাবেন।
উচ্চারণ করবে কি?–সুকুর আলাদা লিল্লায়ে? এর অর্থ খুব সুন্দর, খুব ভালো ইসলাম মানেই সুন্দর। যে নামাজের দোহাই দিয়ে তালিবানরা মানুষ খুন করছে, চুল কেটে দিচ্ছে, পুরুষদের দাড়ি রাখতে বাধ্য করছে, সেই নামাজ পড়ার আন্তরিক ইচ্ছে কি মানুষের মনে থাকবে? সুন্নত তো দূরের কথা, ফরজও কেউ আদায় করবে কি? আল্লার নাম করা জোর করে কারুর ঘাড়ে চাপানো যায় কি? আসলে তা নয়। তালিবানরা দেশে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করতে চাইছে যদিও আফগানিস্তানে গণতন্ত্র কোনদিন ছিল না, আজও নেই।
সত্যি বলতে কি, তালিবানদের ওপর প্রথম দিকে আমারও একটা আস্থা জন্মেছিল। আমাদের পাড়ার মসজিদে যখন রোজার সময় কিছু তালিবান এসে আশ্রয় নিয়েছিল, তখন পাড়ার সব বাড়ি থেকে পালা করে তাদের খাবার দিত।
একদিন আমাদের বাড়ির পালা এল। ১৯৯৪-এর রোজার সময়কার ঘটনা। আমি খুব যত্ন করে রান্না করলাম দুম্বার মাংসের কোরমা ও আলুবোখারার মোরব্বা। এখানে চাটনিকে মোরব্বা বলে। এছাড়া টমেটো দিয়ে শশা কুঁচিয়ে সালাডও বানিয়েছি।
আমি তো কত যত্ন করে তালিবানদের জন্যে খাবার করে পাঠালাম মসজিদে। মনে মনে ভাবলাম আহাঃ, বেচারা তালিবানরা সারা দিন রাত দেশের লোকেদের মঙ্গলের জন্যেই তো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের ভালোমন্দ খাওয়াবো না তো কাদের খাওয়াবো? পরের দিন সকালে ওদের দেখার ইচ্ছেতে মসজিদের সামনে গেলাম। দেখলাম। ওরাও আমাকে দেখল। আমার পোশাক দেখে কার কাছে যেন কী জিজ্ঞেস করল। তারপর আমাকে অবাক হয়ে দেখতে লাগল। আমি ওদের দেশের ড্রেস পরি না। শালোয়ার কামিজ পরতাম। সবাই বলেছে ওদের দশ মিটারের তৈরি ঘাঘরা পরতে। কিন্তু আমি সাফ বলে দিয়েছি, আমার দেশের পোশাক ছাড়া আমি কিছুই পরব না। তখন যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতাম তালিবানরা কেঁচো হয়ে ঢুকে সাপ হয়ে বেরোবে তবে নিশ্চয়ই সেদিন তাদের অত যত্ন করে খাওয়াতাম না। অবশেষে ১৯৯৪-এ তালিবানরা যখন কাবুলের দিকে যেতে লাগল, তখন প্রথম বাধা পেল। এই প্রথম তালিবানরা বাধা পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। আবার যুদ্ধ। যুদ্ধ আস্তে আস্তে তালিবানের অনুকূলে যেতে লাগল। তখন মাত্র ইসবি-ইসলামি আফগানিস্তান পার্টির সঙ্গে যুদ্ধ ছিলো। তারা সবাই সেই সঙ্কটজনক মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে যে, যে দিকে পারল, পালিয়ে গেল। তালিবানরা ঘরে ঘরে লুটপাট শুরু করল। লুঠ করার পর ইসবি-ইসলামি পার্টির নামে অপবাদ দিতে লাগল লুঠ, রাহাজানি, খুনোখুনি, নিয়েই তালিবান এগিয়ে গেল কাবুলের দিকে। এহেন অবস্থায় গুলবুদ্দিনও তাঁর ঘাঁটি চারাশিয়া ছেড়ে পালালেন। তালিবানরা আবার জয়পতাকা ওড়াল। কিন্তু তাই বলে যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। তারা এবার রাব্বানিকে যুদ্ধে আহ্বান জানাল। ঘোষণা করল রাব্বানি যদি তার দলবল ও অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ না করেন, তবে আবার যুদ্ধ অনিবার্য। কিন্তু রাব্বানি বা সৈন্যপ্রধান মাসুদ-আহমেদশাহ আর হাজিরুস্তম এঁরা কেউই শাসন ক্ষমতা বিদেশী তালিবানদের হাতে তুলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে চাইলেন না। রাব্বানি সরকারের বক্তব্য জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি যুদ্ধের মাধ্যমেই হবে।
অতএব রাব্বানি তালিবানদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। সর্বত্র যুদ্ধের রং একই। আবার জনগণ ভিটেমাটি ছাড়া হল। আমেরিকা থেকে মোজাদ্দিদি সাহেব এলেন। রাব্বানিকে অস্ত্র সমর্পণ করতে বললেন। তালিবানদেরও থামতে বললেন। কিন্তু ক্ষমতালোভী তালিবানরা থামার মন্ত্রে দীক্ষিত নয়। তারা সমগ্র দেশে ইসলামি শাসন কায়েম করতে আগ্রহী।
ততদিনে জনগণের মন থেকে তালিবানের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা দূর হয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রের বিশিষ্টতম ব্যক্তিদের তথা রাষ্ট্র পরিষদের প্রতিনিধিদের অনুরোধও তালিবানরা প্রত্যাখ্যান করল। তালিবানদের একগুঁয়েমি মনোভাব দেখে সবাই চুপ হয়ে গেল। আর করারই বা কী ছিল? এমনকি তালিবানদের সামনে কোরান শরীফ রাখা সত্ত্বেও ওরা কোরানের দোহাই পর্যন্ত রাখেনি। মানেনি। সুতরাং সবাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে হাল ছেড়ে দিল।
যারা কোরানের দোহাই মানে না সেই তালিবানরা নাকি দেশে মুসলিম শাসন কায়েম করতে চাইছে। আশ্চর্য! এরাই নাকি ছাত্র তথা তালিব তথা মৌলবী তথা ইসলামের প্রতীক। এর চেয়ে অবাক করা ঘটনা আর কী হতে পারে?
কোন প্রসঙ্গ থেকে কোথায় চলে গিয়েছিলাম। এই জন্যেই বলে ভাবনা মানুষকে নিমেষে সমগ্র পৃথিবী ঘুরিয়ে আনে। যাই হোক, আগে যা বলছিলাম সেই প্রসঙ্গে অর্থাৎ গুজারহাটেই ফিরে আসা যাক। সাওমদের মামার মেয়েকে যে পাহারা দিতে রেখে গেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হাসি পেল আমার পাহারাদারের ছিরি দেখে। যার নিজেকে পাহারা দেওয়ার ক্ষমতা নেই সে কিনা আমাকে পাহারা দেবে!
আমি আবার এখান থেকেও পালাবার জন্য তৈরি। তিন্নিকেও তৈরি করে নিলাম। তারপর মেয়েটাকে বললাম
-তুমি সকালে উঠে স্নান করো না? ওকে স্নানের জন্যে পাঠাবার উদ্দেশ্যে বললাম।
-না, আমি মাঝে মাঝে স্নান করি। শুধু আমি নই; আমরা সবাই।
-সেই জন্যে তোমার চুল এত নোংরা, গায়ে এত গন্ধ। এতে তো চুল খারাপ হয়ে যায়। চুলের মায়া সব মেয়েদের।
-তাই? তবে আমাকে বল না কিসে চুল ভালো হবে?
-তুমি মাথায় শ্যাম্পু করে সাবান মেখে স্নান করে এসো। তোমার চুল আমি এমন করে বেঁধে দেবো যে দুমাস তোমার চুল খোলার দরকার পড়বে না। দুমাস বাদে খুলে দেখবে, কোমর পর্যন্ত চুল হয়ে গেছে।
মেয়েটা সাবান ও শ্যাম্পু নিয়ে বাথরুমে চলে গেল। আমি সময় নষ্ট না করে তিন্নিকে নিয়ে আবার অজানার পথে পা বাড়ালাম।
তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বড় রাস্তায় এলাম। একটা লোককে জিজ্ঞেস করলাম পোস্ট অফিস কোথায় বলতে পারেন? আমি রাতে একটা চিঠি লিখে রেখেছিলাম শ্যামলদার উদ্দেশ্যে। আর একটা লিখেছিলাম আমার ছোটো ভাই অভিষেকের ঠিকানায়। যে করেই হোক চিঠিগুলো পোস্ট করে দিতে হবে। দুটো চিঠিতেই আমার সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে লিখেছি। কী করে আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করবে তাও বলে দিয়েছি। লাল বাজারের পুলিস দিয়ে জাম্বাজের চাচাকে পাকিস্তানের যাসুস বলে যেন ধরিয়ে দেয়। অভিষেককে এও বলেছি ও যেন পুলিসকে জানায় ওর দিদিকে আফগানিস্তানে আটকে রেখেছে। অতএব দিদিকে মুক্তি দিলে তবেই যেন আসাম খান মুক্তি পায়।
রাস্তা পার হয়ে তিন্নির হাত ধরে হন্ হন্ করে টেনে নিয়ে লোকটার দেখিয়ে দেওয়া দিক ধরে এগিয়ে গেলাম। কিছু দূর গিয়ে দেখলাম ডান দিকে একটা বাড়ির গায়ে পোস্টবক্স লাগানো আর উর্দুতে যেন কী লেখা। আমি তো পড়তে পারলাম না। অনুমানেই বুঝে নিলাম এটাই পোস্ট অফিস। ভেতরে ঢুকে একটা লোককে জিজ্ঞেস করলাম, রেজিষ্ট্রি চিঠির কাউন্টার কোনটা?
-ওই বাঁ দিকে গিয়ে ডান হাতের দুটো কাউন্টার ছেড়ে তৃতীয়টা।
আমি সেই কাউন্টারে গেলাম। কাউন্টারের লোকটাকে বললাম, আমি ইন্ডিয়াতে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠাবো। তখন লোকটা সব ব্যবস্থা করে দিল। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি ইন্ডিয়ার কোথায় থাকেন?
-কলকাতায়।
লোকটা বুঝেই নিয়েছে আমি ইন্ডিয়ান। তাই সোজাসুজি প্রশ্ন করল। আমি তারপর লোকটার থেকে জেনে নিলাম, ইন্ডিয়ার অ্যামব্যাসি কোথায়। সব জানার পর ওখানে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। ভাবলাম সাওমদ যদি এখন আমাকে খোঁজে। তাই স্থির করলাম খোঁজার সময়টুকু পার করে বাইরে বেরোব। এখানে আমাকে না দেখতে পেলে অন্যত্র খুঁজতে যাবে। সেই ফাঁকে এখান থেকে বেরিয়ে সোজা অ্যামব্যাসিতে চলে যাবো। শুধু শুধু বসে থাকলে পাছে কেউ সন্দেহ করে, তাই একটা চিঠি লিখতে লাগলাম।
প্রায় আধ ঘণ্টা সময় পার করে এখান থেকে বেরোলাম। যাবো ইসলামাবাদে। সেখানেই আছে অ্যামব্যাসি। আবার রাস্তা পার হয়ে আপ-এর গাড়িতে ওঠার জন্যে এপারে এলাম। এখানকার গাড়িগুলো এত সুন্দর, এত ভালো যে প্রথম দর্শনেই মন কেড়ে নেয়। নরম আরামদায়ক গদিওয়ালা সিটগুলোয় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেলেও কষ্ট লাগে না। বাসের গায়ে গন্তব্যস্থলের নাম লেখা থাকলেও আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আগেই বলেছি কারণ উর্দু আমি বলতে পারি কিন্তু পড়তে পারি না। সুতরাং যে কোনও গাড়ি এলেই জিজ্ঞাসা করছি ইসলামাবাদে যাবে কিনা। একটা বাস এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। তার কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, এখান থেকে কোনও গাড়িই যায় না ইসলামাবাদে। আমাদের বাসে চলুন। আমি আপনাকে ইসলামাবাদের গাড়িতে উঠিয়ে দেব। আমি একটু দ্বিধা করলাম। যদি অন্য কোথাও নিয়ে চলে যায়? কিন্তু তারপরই ভাবলাম এখানকার ছেলেরা মেয়েদের ভীষণ সম্মান দেয়। তাছাড়া দিনের বেলায় এত লোকের মাঝে আবার ভয় কিসের? আমি বাসে উঠে বসলাম। বাস হর্ন বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলল। ডাইনে, বাঁয়ে অসংখ্য দোকান। অনেক লোক যাতায়াত করছে। তিন্নিকে জানালার ধারে বসিয়ে আমি ওর পাশে বসে বাইরের জগতে চোখ রাখলাম। বাসের জানালা দিয়ে বাইরে চোখ রেখেই আমি অতীত স্মৃতির ছবিগুলো দেখতে লাগলাম।
সেদিনও গাড়ি চড়েই যাচ্ছিলাম। বাসে নয়, ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সির জানালা দিয়ে সমানে বৃষ্টির জলের ছিটে আসছে, তবুও আমার সূক্ষেপ নেই। সূক্ষেপ থাকার কথাও নয়। জয়িতা যা বলল, তাতে আকাশটাও ভেঙে পড়লে বোধহয় আমি এত আশ্চর্য হতাম না। তবে কি সব কিছুই মিথ্যে?
তাই বা কী করে হয়? সবটা কি করে মিথ্যে হয়? এই তো সেদিন তমালদা বলল, জানো তত সুমি? সৌরভ যখন তোমাকে দেখতে পেল না, তখন আমাকে বলল, বিকেল চারটে পেরিয়ে রাত আটটা হল। না, সুমি আর আসবে না। আমার এত সুখের মুহূর্তে ও আমাকে তাচ্ছিল্য করল? কথা দিয়েও দেখা করতে এল না। কী হবে আমার ডক্টরেট উপাধি নিয়ে? কী হবে চাকরি পেয়ে? সুমি একবারও ভাবলো না আজ আমি প্রথম চাকরিতে জয়েন করেছি? তারপর নাকি তমালদাকে সঙ্গে নিয়ে একটা হোটেলে গিয়ে সারারাত ধরে মদ খেয়েছে, আর আমি না আসার জন্যে অভিযোগ, অনুযোগ করেছে। আমি তো দেখা করব বলেই ভেবে ছিলাম। কিন্তু সেইদিনই যে একটা নাটক করাবার জন্যে শ্যামলদা আমাকে সঙ্গে করে রিহার্শালে নিয়ে যাবে তা কেমন করে জানব? শ্যামলদাকে তো আর বলতে পারছি। না যে সৌরভের সঙ্গে আমার দেখা করার কথা পার্কস্ট্রিটে। তবে তো সর্বনাশ! ঠিক বাবার কানে উঠে যাবে কথাটা।
সেই সৌরভ? আমি দেখা করিনি বলে যে এত দুঃখ পেয়েছিল? সে কিনা আজ। ঘেন্না করছে। ভীষণ ঘেন্না করছে তার কথা ভাবতে। আরো ঘেন্না করছে এই কথা ভাবতে যে, তিল তিল করে আমি ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। সৌরভ এত নীচ এত জঘন্য? এত ঘৃণ্য? সৌরভের শিক্ষা সৌরভকে একটুও বাধা দিল না? বংশ মর্যাদার কথাও ভাবলো না? সৌরভকে সত্যিই কি আমি ভালবাসি? যদি নাই ভালবাসি তবে জয়িতার কাছে কথাটা শুনে, কেন আমি ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে চলেছি রনিতার বাড়ি? কিছু দেখার বা বোঝার জন্যে? নাকি সৌরভকে ফিরিয়ে আনার আশায়? জয়িতা নাকি রনিতার বাড়িতে গিয়েছিল একটা বই নিতে। রনিতার বাড়ির একটু কাছে যখন জয়িতা পৌঁছেছে ঠিক তখনই সৌরভের গলার আওয়াজ পাই। জয়িতা রনিতার বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে বন্ধ দরজায় কান রাখে।
-রনিতা, তুমি আমাকে সারা জীবন তোমার বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখতে পারো?
-সৌরভ, আমি কেমন করে তোমাকে ধরে রাখব? তোমার সুমিকে তো তোমার কাছ থেকে সরাতে পারব না?
–সুমিকে আমি ভালবাসি সেটা যেমন ঠিক; তোমাকেও চাই সেটাও ঠিক। তোমরা দুজনে আমার দুটো দিক।
-কিন্তু তুমি স্বীকৃতি দেবে সুমিকে। তবে আমি তোমার কাছে কী পাবো?
-তুমি আমাকে পাবে। সামাজিক স্বীকৃতিই কি জীবনের সব পরিপূর্ণতা আনে? সেই অর্থে সুমিই তো বেশি হারাবে। জয়িতা আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। লজ্জায় ঘেন্নায় ওখান থেকে সোজা চলে এসেছে আমার কাছে। সব খুলে বলেছে আমাকে।
রনিতা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। আমি কি কোনও দিন ভাবতে পেরেছি রনিতা আমাকে এমন আঘাত দেবে? রাতটা যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়ে সকালে আমি সৌরভের বাড়িতে গেলাম। একটা হেস্তনেস্ত করার জন্যে। বাড়িতে ঢুকেই সামনে সৌরভের বৌদিকে পেলাম।
-বৌদি, সৌরভ কোথায়? ও কি বাড়িতে আছে?
-না রে নেই। গতকাল সকালে বলে গেছে কি একটা কাজে পটনায় যাচ্ছে। আজ রাতে ফিরবে।
আমি ভাবলাম–আর সময় নষ্ট নয়। বৌদিকে কিছু বলার বা বোঝার সুযোগ দিলাম না। হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে সোজা রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সি ধরলাম। ঘটনার আকস্মিকতায় বৌদি কিছু প্রতিবাদ করার সুযোগ পায়নি। অথবা আমার চোখমুখ দেখে বুঝে নিয়েছে কোনও একটা ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছে।
রনিতার সম্পর্কে আমি অনেক কিছু শুনেছি অনেকের কাছে। জনৈক বিবাহিত লোকের সঙ্গে ও প্রেম করত। লোকটা প্রায় ওর বাড়িতে আসত। রনিতার দাদা, বৌদি মা সবাই বারণ করল লোকটার সঙ্গে মিশতে। কিন্তু রনিতা শোনেনি। তখন ওর দাদা ওকে বলেছিল, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। তুমি যদি ভদ্রভাবে থাকতে পারো তো ভালোই, নইলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। এর পর থেকেই রনিতা সল্টলেকে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। একাই থাকে। লোকটাও আসে। আমার সঙ্গেও লোকটার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। লোকটা রনিতার অফিসের বস।
রনিতা লোকটাকে ভালবাসে। আমি একদিন প্রশ্ন করেছিলাম, এই ভালবাসার পরিণতি কী?
-জানি না, কী পরিণতি। তবুও বস্-কে আমি ছাড়তে পারবো না। ওকে আমি খুব ভালবেসে ফেলেছি।
-কিন্তু ওর তো বৌ আছে, ছেলেমেয়ে আছে?
-তাদের ক্ষতি করে তো আমি কিছু করছি না। বস্, সব দিক বজায় রেখেই আমার কাছে আসুক আমি তাতেই খুশি হব।
-এটাই কি জীবনের সার্থকতা? কী পাবি তুই বসের কাছে? যা একটা মেয়েকে পরিপূর্ণতা দেয়? তোর ভালবাসার মূল্য ও দিতে পারবে?
-ওই কেতাবি সার্থকতা আমার জন্যে নয়। আমি একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ পুরুষ পাওয়ার আশা করতে পারি না। কারণ একবার আমার নাম খারাপ হয়ে গেছে রায়কে নিয়ে। রায় শেষ পর্যন্ত আমাকে বিট্রে করল। তখন আমি রায়কে ভালবাসতাম। বিস্ আমাকে ভালবাসে।
আমাকে সবাই রনিতার সঙ্গে মিশতে বারণ করত। সবাই বলত, দেখবি একদিন এই রনিতার জন্যে তোর সর্বনাশ হবে। আমি কারো কথা শুনিনি। আমার ক্লাশমেট রনিতা। পড়াশুনায় ভালো ছিল। আমাকে প্রায় নোট লিখে দিত। মাঝে মাঝে আমি ক্লাশ না করে সৌরভের সঙ্গে যখন কলেজ স্কোয়ারের কোনও বেঞ্চে বসে আছি, তখন রনিতা আমার জন্যে নোট লিখে রেখেছে। তাকে আমি কী করে ভুলি? কিন্তু সেই রনিতাই কিনা আজ এত বছর পর……। অবশ্য রনিতারই বা কী দোষ? ও তো একটা নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া মেয়ে। খড় কুটো যাই পাক, তাকেই ধরে পাড়ে আসার চেষ্টা করবে, শুধু মাত্র বাঁচার একটা ক্ষীণ আশায়। কিন্তু সৌরভ?
ট্যাক্সি উল্টোডাঙা দিয়ে ডানদিকে টার্ন নিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সকাল আটটা বাজে। এখান থেকে রনিতার বাড়ি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাড়ির সব জানালা বন্ধ। আমার ডানদিকটা পুরো ভিজে গিয়েছে। বাঁ-পাশে বৌদি নিশ্চল পাথরের মতো বসে আছে। বৌদি বুদ্ধিমতী। সে নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছে এই মুহূর্তে কী ঘটতে চলেছে। এর আগেও আমি বৌদিকে একবার রনিতার বাড়ি বেড়াতে এনেছিলাম। সুতরাং ট্যাক্সি এই পথে আসা, সৌরভের খোঁজ করা, বৌদির হাত ধরে টেনে আনা, আমার চুপ করে থাকা, এই সমস্ত কিছুর কী অর্থ সেটা না বোঝার মতো মেয়ে বৌদি নয়। আর বুঝতে পেরেছে বলেই বৌদি পাথরের মূর্তির মতোই নীরব।
রনিতার ঘরের দরজার বেল বাজালাম। বুকের মধ্যে একটা ঢিপ ঢিপ করা আওয়াজ আমার কানে আসছে। বৌদি পাশে দাঁড়িয়ে। একটুক্ষণের মধ্যেই দরজা খোলার আওয়াজ শুনলাম। আমার সামনে দাঁড়িয়ে রনিতা। একটা নাইট গাউন পরা। পাতলা গাউন ভেদ করে ওর শরীরের সবটাই যেন বাইরে এসে পড়েছে। একটা নেভি ব্লু কালারের প্যান্টি পরেছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেটা। দেহে আর কোনও আবরণ নেই। সারা শরীরে রাতের অলসতা। চুল উস্কখুস্কো। গলার ঠিক বাঁ দিকে কণ্ঠির কাছে একটা গোল লাল দাগ। আমাকে দেখে রনিতা যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল! ওর মুখটা মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমি ওকে পাশ কাটিয়ে বৌদিকে হাত ধরে টেনে নিয়ে ঘরে ঢুকলাম।
-সুমি তুই? ওকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বললাম কেন আসতে
নেই?
-তা-না-কিন্তু–।
-আমি আর বৌদি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাই ভাবলাম একবার তোর সুখের বাসরটা দেখেই যাই।
আমি সোজা শোয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। আমার আওয়াজ পেয়ে ততক্ষণে সৌরভ উঠে দাঁড়িয়েছে। বিছানার চাদরটা কুঁকড়ে গেছে। একটা পাশ বালিশ নিচে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ওটার আর রাতে দরকার হয়নি। মাথার ওপর ফ্যানটা বন্ বন্ করে ঘুরছে।
আমি সৌরভের সঙ্গে একটিও কথা বলার প্রয়োজন বোধ করলাম না। শোয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রনিতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। রনিতার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, এই মুহূর্তে ওর কোন ক্ষমতাই নেই আমার চোখে চোখ মেলানোর।
-কী রে, কী হলো? চোখ নাবালি কেন? এইভাবে চোখ নাবিয়ে নেওয়ার খুব কি দরকার ছিল? ভালোই হল আমাকে সঠিক পথ চেনালি? বন্ধুর চরম সর্বনাশের আগেই তাকে বাঁচিয়ে দিলি? সৌরভ বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।
বৌদি এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সৌরভকে বলল, তোমাকে আমার স্বামীর ভাই বলে ভাবতে ঘেন্না করছে। এই কলঙ্ক থেকে আমি যদি মুক্তি পেতাম তো শান্তি পেতাম।
হঠাৎ সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। জানালার কাঁচটা তুলে দিলাম। কী জানি! হয়তো বজ্রপাতের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার একটা সামান্য চেষ্টা মাত্র।
বৌদি বলল, সুমি তোমাকে অনুরোধ করবার ধৃষ্টতা নিশ্চয়ই আমার নেই। আর সে চেষ্টাও আমি করব না। তবুও বলি যদি পারো আমাকে ও তোমার দাদাকে ক্ষমা করে দিও। আমি যদি আগে বুঝতাম……।
আমি সেদিন বৌদিকে আর কিছু বলতে না দিয়ে শুধু ওর হাতটা চেপে ধরে বলেছিলাম, থাক বৌদি আর কিছু বোলো না। আমার কিছু শুনতে ভালো লাগছে না। প্লিজ, ডোন্ট মাইন্ড।
ক্রমাগত বৃষ্টির ছিটে এসে পড়ছে ট্যাক্সির জানালায়। পৃথিবীটা যেন ঘন অন্ধকারে ডুবে গেছে। ট্যাক্সির ওয়াইপারটা সপার্ট সপাটু আওয়াজ তুলে ওপর থেকে নিচে নামছে আবার ওপরে উঠছে। মানিকতলার মোড়ে গাড়িটা সিগনালে দাঁড়িয়ে। একটা কাক গাছে বসে সমানে কর্কশ আওয়াজে ডেকে চলেছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম কী করবো? কাঁদব? এই সময়ে কান্নাই কি আমার একমাত্র উচিত কাজ?
কিন্তু কাঁদবোই বা কেন? কার জন্যে? সৌরভকে হারাবার জন্যে? কিন্তু কেন? সৌরভ কি কখনও আমার ছিল? যদি আমারই থাকবে তবে কেন এমন হল? আমার এমন কী নেই, যা রনিতার আছে? আবার ভাবি, আমি কোনদিন রনিতা হতে পারব না। সবাই তো সব কিছু পারে না। রনিতা অত্যন্ত সহজে যা করতে পারবে, আমি সারা জীবন তপস্যা করেও তা পারব না।
গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বাড়ি গিয়ে আগে জল খেতে হবে। গাড়ি এসে মেডিকেল কলেজের সামনে দাঁড়ালো। বৌদিকে পৌঁছে দিয়ে আমি বাড়ি চলে গেলাম।
জীবনের একটা অধ্যায় পিছনে ফেলে এলাম। কোনও অনুশোচনা নেই। দ্বিধা নেই। দুঃখ নেই। আছে শুধু একরাশ ঘেন্না। একটা অপবিত্র মানুষের প্রতি যেমন ঘেন্না হয় ঠিক তেমনি ঘেন্না। কন্ডাক্টারের ডাকে অতীতের চিন্তায় বাধা পড়ল।
নামুন বিবিজি। এখান থেকেই আপনি ইসলামাবাদের গাড়ি পেয়ে যাবেন। ওই যে একটা সাদা গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন, ওইটাই যাবে।
কন্ডাক্টার আমাকে একটা গাড়ি দেখিয়ে দিল। আমি তিন্নিকে নিয়ে বাস থেকে নেমে সাদা প্লাং কোচ গাড়িটার দিকে এগোলাম। বেলা একটা নাগাদ প্লাং কোচ থেকে নামলাম। এখানেই আছে অ্যামব্যাসি। কিছুটা যাওয়ার পর একটা রাস্তায় এলাম। রাস্তার ডান দিকে বড় বড় গাছ আর বাঁদিকে পরপর প্রায় সমস্ত দেশের অ্যামব্যাসি। আমি এই রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। আমেরিকা, ব্রিটেন, আরব, চীন, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের অ্যামব্যাসি ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম ইন্ডিয়া অ্যামব্যাসির সামনে। দেখতে পেলাম ভারতের পতাকা হাওয়ায় সগর্বে উড়ছে। বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। আমার দেশের পতাকা। আমার দেশের লোক এখানে আছে। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা। কতদিন, কত বছর পরে আমি আবার দেখতে পেলাম আমার দেশের পতাকাকে। ভীষণ ইচ্ছে করছে হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করতে। আমি অ্যামব্যাসির দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু একী? অ্যামব্যাসি যে বন্ধ! উপায়? আমি হতাশায় ভেঙে পড়লাম। সব কিছু ঝাপসা মনে হল। এবার কী হবে? মনে পড়ল আমি বাড়িতে থাকতেই শুনেছি কী একটা ঝামেলার পরিপ্রেক্ষিতে করাচিতে ভীষণ গন্ডগোল হয়েছে এবং করাচিতে ইন্ডিয়ান অ্যামব্যাসি বন্ধ করে দিয়েছে পাকিস্তান সরকার বেনেজির ভুট্টো। কিন্তু সে তো করাচির খবর। ইসলামাবাদেও কি ওই একই পরিণতি? তবে আমার পরিণতি কী হবে? আমি কোথায় যাবো? এখানে একা মেয়েকে হোটেল ভাড়া দেবে না। তবে কি সাওমদের বাড়িতেই আবার ফিরে যাবো? না। ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আজকের রাতটা কোনমতে যদি কোথাও কাটাতে পারি তবে কাল ভোরে কাবুলে যাওয়ার বাস ধরে সোজা কাবুল শহরে যাবো। যুদ্ধে যদি মৃত্যু হয় হোক। তবুও শান্তি কিন্তু ওদের কারো কাছেই ফিরব না। গতকাল রাতে একটুখানি সময়ের জন্য সাওমদ টি.ভি. চালিয়েছিল তখন দেখলাম এবং শুনলাম যে পাকিস্তান থেকে ইন্ডিয়ান অ্যামব্যাসি নাকি তুলে দেওয়া হয়েছে। কে জানে কী হয়েছে। মাথার মধ্যে সবই যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। একজন পাকিস্তানি পুলিস আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি অনেকক্ষণ এখানে এই ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন দেখলাম। কাউকে খুঁজছেন?
-হ্যাঁ, আমি অ্যাম্বাসিতেই এসেছি। কিন্তু বুঝতে পারিনি যে…। আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে পুলিসটা বলল-আজ তো জুম্মাবার। সব বন্ধ। পাকিস্তানে শুক্রবারকে জুম্মাবার বলে। আজ বন্ধ? এখন তাহলে আমি কোথায় যাবো? কোনও উপায় না দেখে ভাবলাম এই পুলিসের কাছে সব বলে, এদের কাছেই যদি আশ্রয় চাই? কিন্তু এরা পাকিস্তানের পুলিস। যদি সাহায্য না করে? পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের একদম বনিবনা নেই। একটা তফাত আছে। তাছাড়া কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে আরো খারাপ.. যতই হোক নিজের দেশ তো নয়। তাই ভয় পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পুলিসটা আবার জিজ্ঞেস করল–আপনি কিছু বলবেন? আপনি কি ভিসা নিতে চান? নাকি এখানে। থাকার সময় বাড়াতে চান? পুলিশটা বুঝে নিয়েছে আমি পাকিস্তানি নই।
-আপনি কি করে বুঝলেন যে, আমি এখানকার মেয়ে নই?
-আপনার কথা শুনে, আর আপনার পোশাক দেখে।
-কেন? এখানকার মেয়েদের পোশাক আমার পোশাকের মতো নয়?
-না। এখানকার মেয়েরা এত টাইট পোশাক পরে না। আর মাথায় দোপাট্টা দিয়ে ঘোমটা দেওয়া থাকে। যা আপনার নেই। আমার সালোয়ার ওর কাছে টাইট বলে মনে হয়েছে–আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি ইন্ডিয়ান। কিন্তু আমি এক পাঠানের বিবি। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে সাত বছর আগে কাবুলে এসেছিলাম….। আমি সব কথা খুলে পুলিসটাকে বললাম। শুনে পুলিসটা আমাকে বলল দেখুন এই ব্যাপারে আমরা আপনাকে একটাই সাহায্য করতে পারি। সেটা হল এক রাতের জন্যে আপনার থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কাল আপনি আপনাদের অ্যামব্যাসিতে এসে দেখুন, ওরা কিছু ব্যবস্থা করে কিনা।
যে আমাকে সমূহ বিপদ থেকে বাঁচিয়ে একটা রাতের জন্যে মাথা গোঁজার ঠাই করে দিল তার নাম সিকান্দার। আমি সিকান্দার সাহেব বলে তাকে সম্বোধন করেছি। সিকান্দার সাহেব আমাকে যার সঙ্গে পাঠাল তার নাম জামিল। ইসলামাবাদের বড় মসজিদের পিছনে পাহাড়ের ওপর তার বাড়ি। পাহাড়ের উঁচু নিচু রাস্তা অনেকটা হেঁটে গিয়ে পৌঁছতে হয়। জামিলের বৌটি বেশ ভালো। আমরা যখন তার বাড়ি পৌঁছলাম তখন রাত হয়ে গিয়েছে। বৌটি আমাকে ঘরে বসাল। তিন্নির জল তেষ্টা পেয়েছিল। সারাদিন মেয়েটা আমার হাত ধরে ঘুরে বেড়িয়েছে। একবার দুপুরে সে বলেছিল-মা, আমার খিদে পেয়েছে। আমি তাকে বলেছি –সোনা, এখানে কোনও খাবারের দোকান নেই। তাই এখন খাবার চাইতে নেই।
পরে যখন সিকান্দারের একটু খাবার-দাবার দেখেছে, তখন আবার বলেছে মা এখানে খাবার আছে?
-না মা, আমাদের জন্যে খাবার নেই। যখন খাবার পাবো তখন আমি নিজেই তোমাকে কিনে দেব।
-তবে একটু জল দাও।
আমাদের কথা বোধহয় সিকান্দার শুনেছিল। তাই তার খাবারের প্লেটটা আমাদের দিকে এগিয়ে দিল। আমি যখন নানা করলাম তখন সিকান্দার আমাকে বলল,–খান, খেয়ে নিন। আপনার খিদে না পেলেও বাচ্চাটার তো খিদে পেয়েছে? আমার ঘরেও বিবি, বাচ্চা আছে। এই সমস্ত কথা হিন্দিতে হচ্ছে।
আমার চোখদুটো জলে ভরে উঠেছিল। কী ভালো মানুষ এরা। তারপর তিন্নিকে আমি পেট ভরে রুটি ডাল খাওয়ালাম। মাংস ছিল। কিন্তু খুব ঝাল। তিন্নি খেতে পারবে না। জামিলের বৌয়ের ডাকে দুপুরের চিন্তার ব্যাঘাত ঘটল বৌটি এক কাপ চা নিয়ে এসে আমার পাশে বসল। ঘরে আসবাব বলতে একটা লোহার খাট, আর দুটো দড়ির খাঁটিয়া। একটা সাদা কালো ছোটো টি.ভি। একটা চেয়ার, তার ওপর একটা টেবিল ফ্যান। ডান দিকে চওড়া দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে একটা স্টোভ। পাশে একটা সেলফে বাসন, মশলার কৌটো ইত্যাদি সুন্দর ভাবে সাজানো। ঘরের লম্বা দেওয়ালে একটা দেওয়াল আলমারিও আছে। সমস্ত ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বৌটার দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। তিনি পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এইটুকু বাচ্চা মাত্র চার বছর বয়স। সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। একবারও বলেনি যে কষ্ট হচ্ছে। আর তার মধ্যে যদি এক আধবার একটু আধটু খাবার চেয়েছে তখনি ধমক খেয়েছে। সারা দিনের ক্লান্তির পর মেয়েটা শোবার জায়গা পেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলাম। মায়ের স্নেহের ছোঁয়া পেয়ে একবার চোখ মেলে দেখে আবার ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল নিশ্চিন্তে, তার মা মাথায় হাত রেখেছে অন্য কেউ নয়।
এবার বৌটা আমাকে বলল- একটাই মেয়ে?
–হ্যাঁ, তোমার কটা?
–আমার বাচ্চা নেই।
–কত দিন বিয়ে হয়েছে?
–দশ বছর।
–এখনো বাচ্চা হয়নি? ডাক্তার দেখিয়েছ?
–দেখিয়েছি বিবিজি। কিন্তু কোনও ফল হয়নি।
–কেন? ডাক্তার কী বলছেন হবে না?
–না তেমন কিছু বলেননি। আবার হবেই, সে কথাও বলছেন না।
–তবে অপেক্ষা করো। নিশ্চয়ই হবে।
–অপেক্ষা? কিন্তু কী করে? সবই তো….।
বৌটি আর কিছু বলতে পারে না। তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো। ক্ষণিকের মধ্যে সে নিজেকে সামলে নিল। মুখটার মধ্যে একটা থমথমে ভাব নিয়ে সে আমার পাশে বসে আছে। আমি বৌটাকে দেখছি। তার কোথাও কোনও অসম্পূর্ণতা নেই। দেখতে সে বেশ সুন্দরী না হলেও ভালোই। কেন জানি না বৌটার জন্যে ভিতর থেকে একটা ব্যথা অনুভব করতে লাগলাম। বৌটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে একবার দেখে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল; দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে আবার ফিরে এসে আমার পাশ ঘেঁসে বসল। এক অস্বস্তির মধ্যে পড়লাম আমি। বৌটার চোখে একটা ভয় আর কী যেন একটা হারাবার যন্ত্রণা, একটা দুর্লভ পাওয়াকে যেন, না পাওয়ার কষ্ট ওর সমস্ত মনে। সেটাই ওর সমস্ত চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। বৌটা এবার আমাকে বলল-জানো বিবিজি। আমার স্বামী আবার একটা বিয়ে করছে। আর চারদিন পরে ওর বিয়ে।
-বিয়ে করছে? এখন আমি আর এই বিয়েটিয়ের ব্যাপারে অবাক হই না। কারণ আমি দেখেছি আফগানে প্রায় প্রতিটি লোকই দুটো তিনটে বিয়ে করে। কাল যদি শুনি আমার স্বামী আর একটা বিয়ে করেছে তবুও আমি একটুও আশ্চর্য হব না। আমি বৌটির দিকে চেয়ে দেখলাম। তার চোখে একটা ব্যাকুলতা। স্বামীর নিশ্চিত বন্ধনে হারিয়ে যাওয়ার দিন ওর শেষ হয়ে এসেছে। সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চের শিহরণের দিন গত হল। ঘরের নিয়ন আলো-আঁধারির মধ্যেই দাঁড়িয়ে বৌটা তার আশা আকাঙক্ষর প্রত্যাশার বিদায় সুর শুনছে। দুর্বোধ্য অস্বস্তির মধ্যে কয়েক মুহূর্ত কাটল আমার। অস্বাচ্ছন্দ্য, মনের মধ্যে বারকয়েক আনাগোনা করে থেমে গেছে। বন্ধ দরজায় টোকা পড়ল, বৌটা সচকিতে উঠে ছিটকিনিটা খুলে দিল, এই বাড়ির মালিক ঘরে ঢুকল। আমি একটু অপ্রস্তুত। হঠাৎ লোকটা এভাবে ঘরে ঢুকে আসতে পারে তা ভাবতে পারিনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নোকটা বৌটিকে বলল
–বিবিজির জন্যে কিছু খাবার বানিয়েছ?
-না, না, আমার জন্যে আলাদা করে কিছু বানাতে হবে না। যা বানানো আছে। তাতেই হবে। আর তাছাড়া আমার কিছু খেতেও ইচ্ছে করছে না।
লোকটা আমাকে আর বিব্রত করেনি। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল। আবার একটা অসহ্য যন্ত্রণা আমার মাথাটাকে কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে। যে যন্ত্রণার ভার কেউ নেবে না। বুঝবে না। আবার একটা বঞ্চনার কাহিনী। চেষ্টা করলেও এই বঞ্চনার কবল থেকে কোনও মেয়ের মুক্তি নেই। সব রকম অত্যাচার সহ্য করেও বজায় রাখতে হবে নির্দয় পুরুষটার প্রতি প্রীতির সম্পর্ক।
সকাল সাতটা। অ্যামব্যাসির সামনে লোকে লোকারণ্য। রাস্তা থেকে অনেকটা ওপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে তবেই অ্যামব্যাসির লবি। পর পর দুটো কাউন্টার। আর দুটো কাউন্টারেই লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভিসার জন্যে। রাত থাকতে সবাই এসে যে যার পজিশান নিয়ে নিয়েছে। ইন্ডিয়ান অ্যামবাসি ছাড়া অন্য অ্যামব্যাসিতে এত রাশ নেই। এই লোকগুলোকে সরিয়ে সরিয়ে ইনস্পেক্টর সিকান্দার আমাকে নিয়ে গেল একটা জানালার সামনে। জানালাটা শাটার দেওয়া। দুএকবার ধাক্কা লাগানোর পর একটা দারোয়ান শাটারটা খুলে মুখ বাড়িয়ে বলল–কি চাই? সিকান্দার তাকে আমার কথা বলল আর বলল যে বড় সাহেবের সঙ্গে বিবিজিকে কথা বলিয়ে দাও। দারোয়ানটা আমাকে দাঁড়াতে বলে ভেতরে চলে গেল। যথারীতি শাটারটা বন্ধ করে।
আমি যখন এই বন্ধ কাউন্টারের সামনে বড় সাহেবের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, তখন হঠাৎ দেখলাম আমার সেজো দেওর মুশা খানকে। তার একটু দূরে সাওমদ ও মিরাউজল দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকেই তাদের শ্যেন দৃষ্টি। ওদের দেখে এখন আমার আর একটুও ভয় করছে না। ভাবনা হচ্ছে! যদি সবাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাকে আবার আফগানিস্তানে নিয়ে যায়? একদম ভয় পাচ্ছি না তা কিন্তু নয়। একটা ভয় বুকের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারছে, তবে প্রকাশ পেতে দিচ্ছি না। আমি সিকান্দারবাবুকে ডেকে আমার দেওরদের দেখালাম। এও বললাম, ওরা আমাকে
জোর করে ধরে নিয়ে যাবে বলে এসেছে। নিয়ে যেতে না পারলে আমাকে হয়তো। খুন করে রেখে চলে যাবে। ওদের আপনি জানেন না। ওরা সব পারে। বদলা নেওয়ার ভাবনায় ওরা নিজের বাবা-দাদাকেও ছাড়ে না। আর এটাও ভাববেন না যে পাকিস্তানে ওরা কিছু করতে পারবে না। জানেন জলিলকে মেরে জলিলের চাচাতো ভাই করাচিতে আত্মগোপন করেছিল। জলিলের নিজের ভাই করাচিতে এসে তাকে খুঁজে বার করে হত্যা করে জলিলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে। ওরা এমন। ওদের আমি বিশ্বাস করি না।
সব শুনে সিকান্দার আমাকে বলল-আপনার কোনও ভয় নেই। এখানে সব বলুন। এরাই আপনাকে সব ব্যবস্থা করে দেবে। আমি এখানে আপনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি। ভয় পাচ্ছেন কেন? দরকার পড়লে আমি আপনাকে কমিশনারের কাছে নিয়ে যাবো।
আমাদের কথা বলার মাঝেই শাটারটা খুলে সেই দারোয়ানটা মুখ বাড়িয়ে বলল–আসুন কথা বলুন। এই সব কথা হিন্দিতেই হচ্ছে। আমি এবার কাউন্টারের কাছে গেলাম। দেখলাম এক ভদ্রলোককে। বুকের কাছ থেকে মুখ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। রোগা ছিপছিপে বলে মনে হলো। লোকটা আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করল
আপনি কি ইন্ডিয়ান?
–হ্যাঁ সার।
–কোনও প্রমাণপত্র আছে?
–আছে। আমার সমস্ত সার্টিফিকেট, রেশন কার্ড জেরক্স, বিয়ের কাগজ, যা ইন্ডিয়ার কোর্টের থেকে পাওয়া।
–আপনি ভিতরে আসুন।
আমাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে যেতে বলল জানালার দারোয়ানটাকে। দারোয়ান তখন বড় দরজার তালা খুলে আমাকে ডাকল। আমি ভিতরে ঢুকে গেলাম। তারপর আমার ক্যামেরা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করল। আমি না বললাম। শুধু হ্যান্ড ব্যাগটা চেক্ করে তাপর আমাকে সামনের বিশাল প্রশস্ত সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো লন পেরিয়ে, একটা খুব বড় ঝঙ্ককে পরিষ্কার অ্যামব্যাসির কার্যালয়ের হল ঘরের মধ্যে নিয়ে এল দারোয়ানটা। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়াবার পর, কাউন্টারে দেখা লোকটা এলেন। এবার তাকে স্পষ্ট দেখলাম। একটা বিস্কুট কালারের সাফারি স্যুট পরেছেন। আমার কাছে এসে আমার সমস্ত কাগজ তিনি দেখতে চাইলেন। আমি এক এক করে সব তাকে দেখালাম। তিনি সমস্ত কিছু দেখার পর আমার কাছে সব ফেরত দিলেন। আমার বুকের ধুকধুকানি বেশ দ্রুত। নিঃস্পলক চোখে উদ্বিগ্ন হৃদয়ে আমি তার দিকে অনেক পাওয়ার আশায় তাকিয়ে রইলাম। সে আমার অনেক আপন বলে মনে হতে লাগল।
কিন্তু, মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। লোকটা আমাকে বলল–ম্যাডাম, আমি তো আপনার জন্যে কিছুই করতে পারব না। আমার কিছুই করার নেই। আপনি যদি পাকিস্তানের রাস্তা দিয়ে আসতেন, তবে দেখতাম কী করতে পারতাম। আপনি বরং কাবুলেই ফিরে যান।
ভদ্রলোককে আমি আর কথা শেষ করতে দিলাম না। মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ধন্যবাদ। আপনি আমাকে ভিতরে ডেকে এনেছেন বা আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আপনার মূল্যবান সময়ের যে অপচয় করেছেন তাতে আমি ভীষণ দুঃখিত। আপনার পরামর্শটা আমি মনে রাখব। আমার কথা শেষ হওয়ার পর, তিনি আমাকে বললেন, দাঁড়ান দেখি কী করা যায়।
অফিসার দারোয়ানটিকে সেখান থেকে সরে যেতে বলল। তারপর আমাকে বলল–আপনার কেসটা খুব জটিল। এখানে এটা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। চলুন আমার কোয়ার্টারে, সেখানে গিয়ে ড্রিংক করতে করতে বিস্তারিত কথা বলা যাবে। আপনি ড্রিংক করেন তো?
কথাটা শুনে ঘৃণায় রি রি করে উঠল আমার শরীর। গলার স্বর শক্ত করে বলল–না, আমি ড্রিংক করি না। আপনার যা বলার আপনি এখানেই বলুন।
লোকটি আমার চোখের দৃষ্টি দেখেই আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছিল। একজন বিপদগ্রস্তা, বিপন্না ইন্ডিয়ান মানুষের প্রতি কি এইটুকুই কর্তব্য ছিল ইন্ডিয়ান অ্যামব্যাসির কর্ণধারের? এইটুকুই একজন ইন্ডিয়ানের পরিচয়? সে কোথা দিয়ে কোন রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করেছে? কিম্বা ড্রিংক করতে হবে তার সঙ্গে? বিনা পাসপোর্টে ঘুরে বেরবার দায়ে আমাকে তো পাকিস্তান গ্রেপ্তার করবে? পাকিস্তান আমাকে জেলে আটকে রাখবে। আমাকে শাস্তি দেবে। আমার প্রতি পাকিস্তান তো অত্যাচার কবে। ইন্ডিয়ান অ্যামব্যাসি তো আমাকে রেসকিউ করবে। একজন সরকারি গুরুত্বপূর্ণ অফিসারের কি এইটুকুই কর্তব্য? এই দায়সারা কর্তব্যের জন্যেই কি তাকে ওই পদে ওখানে পাঠানো হয়েছিল? নাকি তার বিছানায় শয্যা সঙ্গিনী হতে পারলাম না বলেই আমাকে পাকিস্তানিদের হাতে ঠেলে দিলেন? কিন্তু পাকিস্তানের সরকারি অফিসাররা ওঁর থেকে অনেক সভ্য, ভদ্র। অনেক বন্ধুসুলভ ব্যবহার করেছে। আমার সঙ্গে।
আমি বিনা পাসপোর্টে পাকিস্তানে আছি। আমাকে ধরে আমার প্রতি অত্যাচার করার পক্ষে এর থেকে সুন্দর মুহূর্ত আর কী হতে পারে? ছোটো থেকেই তো শুনে আসছি পাকিস্তানের লোক ভীষণ খারাপ। কিন্তু আজ এই খারাপরাই আমার পরম বন্ধু। শুনেছি পাকিস্তানিরা সব সময় হিন্দুস্থানিদের প্রতি অত্যাচার করে। কারণে অথবা অকারণে। আমি তো সেই হিন্দুস্থানেরই মেয়ে?
সেদিন মাসটা ছিল বোধহয় এপ্রিলের শেষ। যে সময় করাচি থেকে ইন্ডিয়ান অ্যামব্যাসি বন্ধ করা হয়েছিল। শনিবার। তারখিটা ঠিক ঠিক মনে নেই। তবে বকরি ঈদের ছয়দিন আগে। ১৯৯৫। এই পাকিস্তানের পুলিসরাই আমাকে স্থান দিয়েছে। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের হাতে নির্মম, নিষ্ঠুরের মত তুলে দেয়নি। আমাকে আন্তরিক স্নেহের সঙ্গে উপদেশ, নির্দেশ দিয়েছে। কমিশনার, এস পি থেকে নস্টেবল পর্যন্ত সবাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আর বলেছে–যদি এমন ঘটনা আমাদের দেশের কারো ঘটত, তবে প্রথমে তো তাকে বাঁচাতাম, তারপর সব বিচার হতো কার দোষ না দোষ।
পরের দিন সকালে আমি আফগানিস্তানের অ্যামব্যাসিতে গিয়েছি। সিকান্দারবাবুই আমাকে বলেছে যে ওখানে গিয়ে আফগান পরিচয় দিয়ে একটা পাসপোর্ট করুন, তারপর ভিসার ব্যবস্থা আমরা করে দেব। আমার দেওররা যখন আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে এসেছে, তখন সিকান্দার ওদের বসিয়ে রেখে এস. পি-কে খবর দিয়ে আনতে বলল অন্য একটা পুলিসকে। আমার দেওররা তখন সব ম্যাজিকের মতো ভ্যানিশ হয়ে গেল। ওদের পালিয়ে যাওয়া দেখে আমার বেশ আনন্দ হলো। একদিন এই মুশা খানই আমাকে তার ওই বিশাল হাতের মুষ্টি দিয়ে মুখে, মাথায়, পিঠে অসম্ভব জোরে জোরে ঘুসি মেরেছে। আজ সেই মুশা খান ভয়ে আত্মগোপন করল।
পাকিস্তানে শুক্রবারে সব বন্ধ থাকে, ছুটি থাকে সবার। রবিবারে সব খোলা। আমি সিকান্দারের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে আফগান অ্যামব্যাসিতে এসেছি। সিকান্দারই একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে তার নাম্বারটা নিজের নোট বইতে লিখে নিল। আর ড্রাইভারকে কুড়ি টাকা দিয়ে বলল, ব্যালেন্সটা বিবিজিকে দিয়ে দেবে। এই অ্যামব্যাসিটা ইন্ডিয়ান অ্যামব্যাসির মতো নয়। কাউন্টারের সামনে দুটো বেঞ্চ পাতা আছে। আমি তাতে বসে আছি। কোনও লোক নেই দারোয়ান ছাড়া। প্রায় একঘণ্টা পরে কাউন্টার খুলল। এই এক ঘণ্টার মধ্যে জনা দশেক লোক এখানে এসেছে। সবাই ফার্সিবান। আমিও উঠে কাউন্টারের সামনে গিয়ে একজনকে বললাম পুস্তুতে –আমার একটা পাসপোর্ট চাই।
লোকটা আমার কথা শুনে আমার মুখের দিকে তাকাল। সন্দেহের দৃষ্টি তার। সে বলল,-আপনি কি আফগানিস্তানি?
-হ্যাঁ।
লোকটার সন্দেহ যে তখনো যায়নি সেটা বুঝলাম।
-আফগানে আপনার বাড়ি কোথায়?
-সারানাতে।
লোকটা আমাকে দাঁড়াতে বলে কোথায় চলে গেল। আমি তিন্নির হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছি। আবার সেই ভয়টা যেন এক পা দুপা করে আমার কাছে এগিয়ে আসছে। শত চেষ্টা করেও ভয়টার কাছ থেকে নিজেকে লুকোতে পারছি না। একটু পরে কাউন্টারের দিকে তাকালাম তখন দেখলাম সেই লোকটা এসে কাকে যেন ফার্সিতে কি একটা বলল। তারপর আমাকে পস্তুতে বলল–এই গেট দিয়ে বেরিয়ে বাঁদিকে সোজা খানিকটা যান তারপর দেখবেন এইখানে ঢোকার বড় গেট। সেটা দিয়ে ভিতরে আসুন। আমি আপনাকে আমাদের বড়বাবুর কাছে নিয়ে যাব। তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।
আমি লোকটার কথামতো বাইরে এসে বাঁদিকে হাঁটতে লাগলাম। তারপর বাঁদিকের বড় গেট দিয়ে ভিতরে গিয়ে দেখলাম লোকটা আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার সঙ্গে আমি দোতলায় উঠে এলাম। উঠেই বাঁ হাতে একটা ঘরে লোকটা আমাকে যেতে বলল। আমি দুরু দুরু বুকে সেই ঘরে ঢুকলাম। বিশাল একটা ঘর। দরজা দিয়ে ঢুকে একটু এগিয়ে গিয়ে একটা বিশাল টেবিল। টেবিলের ওপারে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন একজন মোটাসোটা আফগানি ভদ্রলোক। আমাকে হাতের ইশারায় তার সামনের চেয়ারে বসতে বললেন। আমি যখন ঢুকলাম তখন তিনি টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন। সামান্য পরে, কথা বলা শেষ করে ফোনের রিসিভারটা রাখতে রাখতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,
–আপনি কোথা থেকে এসেছেন?
–আফগানিস্তান থেকে।
–ওখানে কোথায় আপনার বাড়ি?
–সারানার পাশে পাতানায়।
–আপনার বাবার বা আপনার স্বামীর নাম কি?
–বাবার নাম তোরানাই খান। স্বামীর নাম জাম্বাজ খান।
আমি আফগান মেয়ে পরিচয় দিচ্ছি বলেই বাবার নাম মিথ্যে বললাম। তোরানাই খান জাম্বাজের বাবার নাম।
–বর্তমানে সারানার কোমান্দান কে? আফগানে দারোগাকে বা এম.এল.এ.কে কোমান বলে।
আমি সত্যি সত্যিই আফগান বা সারানায় থাকি কিনা পরীক্ষা করছেন। কারণ এই প্রশ্নের উত্তর সারানার লোক ছাড়া কেউ বা কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।
–মাদালি, রফিক, ফরিদ, আসাম, এরাই এখন সারানা গ্রামের কোমান্দান।
উনি একজনের নাম জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি সবার নাম বলে দিলাম। উনি এরপর আমাকে আর কোনও প্রশ্ন করলেন না। একজনকে ডেকে বলে দিলেন যে আমাকে পাসপোর্ট দিয়ে দিতে।
আসন্ন মুক্তির আনন্দে বিভোর হয়ে পাসপোর্ট নেওয়ার জন্যে আমি নিচে নেমে এলাম। কিন্তু নেমে এসেই সামনে যেন ভূত দেখতে পেলাম। সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমার জ্যাঠতুতো ভাসুর আদ্রামান। এই আদ্রামান পয়লা নম্বরের মিথ্যাবাদী। আর কোরানের কসম ওর কাছে একটা ছেলেখেলা। স্বার্থস্য, জঘন্য প্রকৃতির মানুষ। আমাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে হাজির হয়েছে। আমাকে দেখে এগিয়ে এল, তারপর বোঝাতে লাগল। অনেক প্রতিশ্রুতি দিল, যে করেই হোক সে আমাকে ইন্ডিয়াতে পাঠাবে। তার ইসলামাবাদের বাড়িতে আমাকে যেতে বলল।
-আমি যাবো না। তোমাদের কারও কোনও কথা বিশ্বাস করি না। তোমরা সবাই মিথ্যাবাদী। খুব রাগের সঙ্গেই কথাগুলো বললাম।
-আমি জাম্বাজের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি, জাম্বাজ তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলেছে। বেশ অমায়িক হয়ে সে কথা বলছে।
–তোমাদের পাঠিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। আমি নিজেই চলে যেতে পারব।
-আমি বারণ করে দিলে এখান থেকে তোমাকে কেউ পাসপোর্ট দেবে না।
-না দিক। এখন আমি এমন একটা দেশে দাঁড়িয়ে আছি, যে দেশ থেকে তোমরা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারবে না।
-জোর করে কেন ধরবো? আমি তো বলছি, তোমাকে হিন্দুস্থানে পাঠাবোই আমার কথা তুমি বিশ্বাস করে ঘরে চলল।
আদ্রামান, ইসলামাবাদে একটা ফ্ল্যাট কিনেছে। এবং একটা টি.ভি, ফ্রিজের দোকান দিয়েছে। আমাকে সেই ফ্ল্যাটে নিয়ে যেতে চাইছে। আমি একটুক্ষণ চিন্তা করলাম, এই ভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর চাইতে, বরং আদ্রামানের ফ্ল্যাটে যাওয়াই ভালো। সেখান থেকে জাম্বাজের সঙ্গে ফোনে কথা বলে সব ঠিক করব। আর ভাই অভিষেককেও, সব ব্যাপারটা ফোনে জানাতে পারব। তাই আমি আর না বললাম না। আদ্রামানের সঙ্গে তার ফ্ল্যাটে গেলাম। আদ্রামানের বিবি এখানেই আছে। আর আছে আদ্রামানের সৎ ভাই আদম ও তার বিবি দানগি। দানগির গলায় একটা টিউমার হয়েছে। সেটা অপারেশান করতে এসেছে। এই আদমকেই, আদ্রামান ক্যাসেট পাঠিয়েছিল। তাতে পাকিস্তানে আসার সব রাস্তা বলেছিল। কোথায় নামতে হবে, তারপর আবার কোন বাসে উঠতে হবে। আর আমি সেই ডিরেক্শানেই আজ পাকিস্তানে এসে পৌঁছিয়েছি।
আজ বকরি ইদ। আদ্রামান বিশাল একটা খাসি এনেছে। সকাল থেকেই সেই খাসিকে জবাই করার তোড়জোড় চলছে। কাবুলে থাকতে থাকতে এখন আমি এই জবাই-টবাইতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। গতকাল রাতে জাম্বাজের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে, আজ আমার ছোটো ভাই, অভিষেককে সঙ্গেও কথা হবে। আকুল উৎকণ্ঠায় আমি অপেক্ষা করছি। রাত থেকেই ভেবে রেখেছি অভিষেককে কী বলব। সকালের নাস্তা করে আমি স্নান করে নিয়েছি। পাকিস্তানে ভীষণ গরম। স্নান করার সঙ্গে সঙ্গেই আবার গরম লাগে। আদ্রামানের ফ্ল্যাটের উপর ছাদ, তাই গরমটা বেশি লাগে। বেলা এগারোটার সময় ফোন বেজে উঠল। আদ্রামান ঘরেই ছিল, ফোনটা সেই ধরল। আমার অনুমান ঠিক, কলকাতার ফোন। আমি ফোনে অভিষেকে মোটামুটি সব বললাম। আজ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে। অভি আমাকে বলল, জাম্বাজের সঙ্গে কথা বলে আমাকে আবার ফোন করবে।
আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, কখন ফোন আসবে। সারা দিন আর ফোন এলো না। আমি যে সময় আশা ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের চিন্তায় সময় গুনছি ঠিক সেই সময় আবার ফোন এলো। আমি ছুটে গিয়ে রিসিভার তুললাম।
অভি আমাকে বলল যে, দিদি, তুই আবার কাবুলে জাম্বাজদের বাড়ি ফিরে যা। কারণ ও বলছে, তুই পালিয়ে এসেছিস, তাই যদি আবার বাড়িতে একবার ফিরে না যাস তবে ওদের ভীষণ বদনাম হবে। জাম্বাজ কথা দিয়েছে, এক মাসের মধ্যে তোকে কাবুলের রাস্তা দিয়ে ওর ভাই পাঠিয়ে দেবে।
আমি অভিকে বললাম, না রে অভি, ওদের কথা বিশ্বাস করবি না। ওরা তোকে ভুল বোঝাচ্ছে। আমি অনেক কষ্টে ওদের কবল থেকে পালাতে পেরেছি। দ্বিতীয়বার সম্ভব হবে না।
-তোকে পালাতে হবে না। জাম্বাজ আমাকে কথা দিয়েছে। যদি তুই এক মাসের মধ্যে না আসিস, তখন আমি জাম্বাজকে ছাড়বো না।
আমি বুঝলাম, অভিষ্কেকে জাম্বাজ মগজ ধোলাই করেছে। এখন আমার কোনও কথাই আর কাজে লাগবে না। ফোনে কতটুকুই বা বোঝানো যাবে? তাই হাল ছেড়ে দিলাম।
সুতরাং, আবার আমাকে ওদের বাড়িতে ফিরে যেতে হবে ফিরে না গেলে যাবো কোথায়? যখন বুঝলাম ফিরে আমাকে যেতেই হবে, তখন আমি আদ্রামানকে বললাম, আমার ইন্ডিয়াতে যাওয়ার পুরো খরচ না দিলে আমি কিছুতেই এখান থেকে যাবো না। নিরুপায় হয়ে আদ্রামান জাম্বাজের সঙ্গে কথা বলে আমাকে পাকিস্তানি টাকায় তিরিশ হাজার টাকা দিলো।
বলা বাহুল্য আমাকে খোঁজার জন্যে ওর ভাই মুশা, পাকিস্তানে আদ্রামানের বাড়ি এসেছে। ইদের দুদিন বাদে, আমি মুশার সঙ্গে আবার সেখানে ফিরে যাচ্ছি; যেখান থেকে মুক্তির সন্ধানে, নিজের জীবন বিপন্ন করে সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, পালিয়ে এসেছিলাম এই পাকিস্তানে। আজ সেই পাকিস্তানকে শেষ বারের মত মুগ্ধ নয়নে দেখে নিচ্ছি। আমার পরম বন্ধু পাকিস্তান।
পাঁচ দিন আমি সম্পূর্ণ একা। এই পাকিস্তানের বুকে ঘুরে বেড়িয়েছি। ভয় নেই, কোনও সংশয় ছিল না। পাকিস্তানের পুলিস, আমি ইন্ডিয়ান জেনেও অত্যাচার করেনি। পাসপোর্ট নেই বুঝেও বন্দী করেনি। ইন্ডিয়ান এমব্যাসি আমার জন্যে অনেক কিছু করতে পারতো, কিন্তু কিছুই করেনি। আর পাকিস্তানের কিছুই করার ছিল না, তবুও অনেকখানি করেছে।
বিপদের সময় ভাবি এখানে না এলে, এখানকার সম্পর্কে এমন দুর্লভ অভিজ্ঞতা কোনদিনও অর্জন করতে পারতাম না। এত আপন একটা দেশকে, আজ ছেড়ে যেতে গিয়ে আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যেতে লাগলাম। অতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যাগুলো, সমাধানের কোনও উৎসাহই নেই আমার মনে।
রাত দুটো। বাসের একটা সিঙ্গল সিটে আমি একা বসে আছি। পিছনের সিটে মুশা খান। দশটার সময় বাস ছেড়েছে। ভোর পাঁচটা আমরা মিরামসাতে পৌঁছাব। আমার সামনের সিটে একটা মুসলিম দম্পতি বসেছে। বৌটার মাথা স্বামীর কাঁধে। নিশ্চিন্তে সে ঘুমোচ্ছে। আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে ওদের লক্ষ করতে লাগলাম। এই অনুরাগের দৃশ্যপট তো আমারও হতে পারতো। কিন্তু হল না আজ থেকে আড়াই বছর আগেও তো, কত রাগ-অনুরাগে ভরা ছিল আমাদের জীবন। কখনো আনন্দ, কখনো নিরানন্দে একেবারেই অন্যরকম ছিলাম আমরা। আমার প্রভাব আমি সব সময় ওর ওপর বিস্তার করতাম। ও মেনেও নিত। আমি ভেবেই পাই না, অতীতের স্মৃতি কি ওকে তাড়া করে না? অনেক ভালোবাসার মুহূর্ত… একটুও ওর মনে পড়ে না? আবার নানা দুশ্চিন্তা এবং অনেক অনিশ্চয়তার মধ্যে ফিরে চললাম।
গাড়ি ক্রমশ এগিয়ে চলল আবার সেই আফগানিস্তানের বন্ধুহীন জীবনে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম জানালার বাইরের গভীর অন্ধকারের দিকে।
একাদশ অধ্যায়
আজ চারদিন হল। আমি সেই বাড়িতে ফিরে এসেছি। সবই ঠিক আছে। যেখানে যা, যে ভাবে ছেড়ে গিয়েছিলাম। শুধু আমি যেন কেমন পাল্টে গেছি। কারো সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমি সিঁটকে যাই, কোথা থেকে একটা লজ্জা, দ্বিধা, সংশয়, আমার মাথাটা নত করে রাখে। কিছুতেই বুঝতে পারি না, কেন এত সংশয়? আমার অন্যায় তো শুধু আমার অসহায়ার স্বীকৃতি মাত্র। আমি তো, আমার স্বামীকে ছেড়ে দেবার জন্যে পালাইনি, তার কাছে যাওয়ার জন্যেই তো গিয়েছিলাম।
পারি না, পারি না, –আমি কিছুতেই পারি না কারো সামনে দাঁড়াতে। ঘরের এক কোণে বসে থাকি। আমার দেওররা কড়া পাহারা দেয় আমাকে, যাতে আমি আর পালাতে না পারি। মেজো দেওর তার বিবিকে ছেড়ে, আমার ঘরের দরজার সামনে শোয়। আর জানালার সামনে ছোট দেওর।
দেখতে দেখতে কুড়ি দিন হয়ে গেছে। কিন্তু, আমার যাওয়ার কোনও উদ্যোগ দেখছি না। ইতিমধ্যে একদিন মুশা, আমার রাস্তা খরচের টাকা চাইলো। আমি দিতে অস্বীকার করলাম। তখন মুশা আমাকে শাসালো, বলল, যদি কাল সকালে আমি সব টাকা তাকে না দিই, তবে খুব খারাপ হবে।
আমি ভাবি, যে মুশা একদিন আমার পিছনে কুকুরে মতো ঘুরে বেড়াতো, আজ সে-ই আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। মনে হয় যদি ট্যাটনের কথা শুনে সেই ৭০ সালে আন্দোলন করতাম তবে বোধহয় আরো একটু সাহস সঞ্চয় হতো। অন্তত শুধু মনে মনে লড়াই না করে প্রকাশ্যে কিছু করতে পারতাম।
১৯৭০ সাল। কীই বা বুঝি? বয়সে ছোট হলেও বেশ মনে পড়ে কলকাতায় তখন নকশাল আন্দোলনের জোয়ার এসেছে। সেই সুবাদে আমাদের পাড়ার আনাচে কানাচে তখন নকশাল পার্টির লোকেদের আনাগোনা। পাড়ায় বেশি বেরোনো দূরের কথা, ছাদে ওঠাও বারণ হলো আমার। আমি বুঝতে পারতাম না নকশাল পাটির সঙ্গে আমার ছাদে ওঠার কী সম্পর্ক? কোন যোগসূত্র খুঁজে পাই না। নকশাল কী? বা কে? আমাদের বাড়ির দেওয়ালেই শুধু নকশালের অস্তিত্ব বুঝতে পারি। চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, বন্দুকের নলে বিপ্লবের জন্ম। এই সব কথাই হল নকশাল। আমার বন্ধু ট্যাটন একদিন বলেছিল–সুমি শ্রমিক আন্দোলন করবি?
-সেটা কী রে? কীভাবে করতে হয়?
-সেটা আন্দোলন। সারা বিশ্বে শ্রমিকের মধ্যে প্রতিবাদের আগুন জ্বালাবো। শ্রমিকের ব্যথায় আমরা ব্যথিত হবো। ট্যাটনের চোখ দুটো চিক্ চিক্ করছে।
-ধ্যুত তোর শ্রমিকের ব্যথা। আমার ব্যথা কে দেখে তার নেই ঠিক। তোর শ্রমিকের ব্যথায় আমার কাজ নেই। আর সারা বিশ্ব আগুনে পুড়ে গেলে আমরাও তো পুড়ে যাবো? না না, তা হয় না। তুই বরং অন্য কিছু কর। এই আন্দোলনটা আমার মোটেও ভালো লাগছে না।
-ধ্যুত। বোকা মেয়ে কোথাকার। অন্য আন্দোলন হয় নাকি?
-ওঃ! হয় না? তবে কী করবি?
-কী আবার করবো? তোর দ্বারা কিছু হবে না। তোর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমারো কিচ্ছু হবে না।
ট্যাটন চলে গেলো রেগেমেগে। তা যাক বাবা। ওই আগুন-টাগুনের ব্যাপারে আমি নেই।
ট্যাটনটা যেন কি! বারান্দায় বসে এইসব সাতপাঁচ ভাবছি, তখন দেখলাম একদল ছেলে হাতে বড় বড় চক্ েরামদায়ের মত কী সব নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। এদের সবার পিছনে আছে ট্যাটন। আমি চেঁচিয়ে ট্যাটনকে ডাকছি। এই ট্যাটন। কিন্তু ট্যাটন একবারের জন্যেও ফিরে তাকাল না। আমার ভীষণ রাগ হল। গ্রিলটা ধরে দাঁড়িয়ে ওদের ফেলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে আছি। দুম দুম করে গোটাকয়েক বোমা পড়লো পলকের মধ্যে রাস্তা কেমন নির্জন হয়ে গেল। ওরা গেল কোথায়? ট্যাটনই বা ওদের সঙ্গে কোথায় গেল? অনেকগুলো গেলর প্রশ্ন মাথার ঠিক মাঝখানে আনাগোনা করতে লাগল। চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করছে। বারান্দার রেলিং ছেড়ে ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেদিন যদি ট্যাটনকে ফিরিয়ে না দিতাম তবে আজ আমি আরো বেশি প্রতিবাদ করতে পারতাম। আবার ভাবি, প্রতিবাদ করার জন্যেই কি আমি তাকে বিয়ে করেছিলাম? এখন আমার দেওররা সবসময় কী সব বলাবলি করে। অবশ্যই তা আমার অগোচরে। বাড়ির বাইরে আমার যাওয়া বন্ধ। বাড়ির সবাই আমাকে পাহারা দেয়। শুধু গুলগুটি ছাড়া। আমি থেমে থাকি না। আমার মনে একই চিন্তা। যদি আমাকে ভালোভাবে পাঠাবে তো পাঠাও। নইলে আমি আবার পালাবো। আমাকে তোমরা ধরে রাখতে পারবে না। আমাকে ধরে রাখার শক্তি তোমাদের নেই। জোর করে আমাকে দিয়ে তোমরা কিছুই করাতে পারবে না। সে শক্তি বা বুদ্ধি আল্লা তোমাদের দেয়নি। সেই বুদ্ধিই যদি তোমাদের। থাকবে তবে কেন তালিবান তোমাদের দেশে প্রবেশাধিকার পেল? এক বিদেশি। গোষ্ঠী তোমাদের অভ্যন্তরে ঢুকে তোমাদের প্রতি অন্যায়ভাবে শাসনের গণ্ডি বেঁধে দিচ্ছে? তোমরা তা মেনে নিচ্ছো? তোমাদের মেয়েদের গোয়ে হাত তুলছে তোমরা তাও মেনে চিছো? অনিচ্ছা সত্ত্বেও তালিবানদের অত্যাচার সহ্য করছো। আসলে তোমরা, আফগানিবাসী তোমরা সবাই দুর্বল। যতই তোমরা মেয়েদের ইজ্জত, সম্মান, আছে বলে জাহির করো না কেন, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের দেশের মেয়েদের কোনই ইজ্জত নেই। তোমাদের দেশ ছাড়া অন্য কোনও দেশ দেখাতে পারবে? যে দেশে এক বিদেশি গোষ্ঠী এসে মেয়েদের এই ভাবে মারধোর করবে? শাসনের গণ্ডি বেঁধে দেবে? আর দেশের জনতা তা মুখ বুজে সহ্য করবে? সেই তোমরা কিনা ধরে রাখবে আমাকে? যতই পাহারা দাও, যতই বড় দরজায় তালা দাও। আমার যখন মনে হবে এবার পালানো দরকার তখন তোমাদের কোনও বন্ধনই আমাকে ধরে রাখতে পারবে না। আর তা আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো। এরা যতই তালা দিক দ্রানাইচাচার বাড়ি যাওয়া বন্ধ করতে পারেনি। দ্রানাইচাচাকে এরা। ভয় পায়। দ্রানাইচাচা খুব রাশভারী লোক। এদের অত্যাচারের সম্পর্কে সবই জানে। তাই এই বাড়িতে আমার যাওয়া বন্ধ করতে পারে না। আমাদের বাড়ির পিছনেই চাচার বাড়ি। হলে কি হবে? অনেকটা ঘুরে তবে যেতে হয়। কারণ দরজাটা ওই দিকেই। আবুদের বাড়ি ও আসাম চাচার বাড়ির। পাঁচিল ছাড়িয়ে ডান দিকে গিয়ে তবেই দ্রানাইচাচার বাড়ি, দ্রানাইচাচার বাড়ির সবাই আমাকে ভীষণ ভালবাসে। প্রায় রাতে আমি মন খারাপ করা রাত এই বাড়িতে এসে কাটাই। সাওমদের বিবি ঝুমঝুমা ও রোশনদারের বিবি বাবান, আমি গেলে খুব খুশি হয়। চাচিরা আমার জন্যে ভালো মন্দ খাবার বানায়। আমার সঙ্গে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করে। আমি ভালো সেলাই জানি বলে মেয়েদের আমার কাছে বসিয়ে সেলাই শেখায়। আমার খুব শান্তি লাগে এই বাড়িতে। কিন্তু দ্রানাইচাচার ও সেরিনা চাচির কোনও শান্তি নেই। ১৯৯২ সালে তাদের জীবনে এক বিপর্যয় ঘটে গেছে। কোনও যুদ্ধ নয়, কোনও শত্রুতা নয়। বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়ে তাদের আদরের ধনকে তাদের কাছ থেকে দূরে, অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। আজও আমার মনে ভেসে ওঠে সেই দিনটার কথা। আমার খুব রাগ হয়েছিলো দ্রানাইচাচার প্রতি। কারণ দ্রানাই চাচার শ্যালকের বিয়েতে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে চাচা যেন আমাকে চেনেই না; এমন ভাব করেছিল। তার পরের দিন সাওমদের বিয়ে। খুব আনন্দে সবাই মেতে উঠেছে। এখানে তো আর কিছু আনন্দের খোরাক নেই; তাই নিজেদের কারো বাড়িতে বিয়ে হলে প্রত্যেকে আসে। নাচে, গান গায়। এটাই এখানে আনন্দের খোরাক। সেদিনও সেই রকম আনন্দের দিন ছিলো।
রোসনের বিয়ের একবছর পরে সাওমদের বিয়ে হচ্ছে। বদল বিয়ে। সাওমদের পরের বোন সফিয়া। যেমন নাম তেমনি দেখতে। বয়স মাত্র চোদ্দ বছর। সাওমদের বৌয়ের নাম ঝুমঝুমা। ঝুমঝুমার দাদার সঙ্গে সফিয়ার বিয়ে হয়েছে।
সকাল থেকেই বাড়িতে অনুষ্ঠান চলছে। যত জায়গায় যত চেনা লোক আছে, সবাই এসে আকাশে গুলি ছুঁড়ছে। এটা এখানকার রেওয়াজ। বাড়িতে ছেলের বিয়ের ঠিক হলে অথবা ছেলে হলে, যদি কেউ না আসে এবং আকাশে গুলি না চালায় তার মানে সে আমার শত্রু বলেই খুশি হতে পারেনি। কারো ইচ্ছে না করলেও আসতে হবে। মরতে মরতে হলেও সবাইকে আসতে হবে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবো হবো। এমন সময় রোসন এলো আমার কাছে।
-সাহেবকামাল, আকা আমাকে তোমার কাছে পাঠালো। এখুনি চলো তুমি। সবাই এসেছে। নাচ-গান করছে। তুমি কেন যাচ্ছ না? চলল, আমার সঙ্গেই চলো।
-না, আমি যাবো না।
-কেন, যাবে না কেন?
-কাল তোরা মামার বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়ার জন্য গিয়েছিলি। তোর বাবাও ছিল সেখানে। কিন্তু আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। পোক্তানাও করেনি। পোক্তানা–অর্থাৎ হাত মেলানো।
-বেশ, আমি তবে আকাকে গিয়ে কী বলব?
-বলবি, তোমাদের মান আছে, সাহেব কামালের নেই! আমি রোসনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমাদের পালিজের দিকে গেলাম। পালিজে মানে ক্ষেত। আমার দেওররা শশা, তরমুজ ও তিরার গাছ লাগিয়েছে। এখানে শোকে বদরং বলে আর তরমুজকে ইন্দ্রোয়ানা ও খিরাকে তিরা বলে। খেত ভর্তি শশা, তিরা হয়েছে। তরমুজও হয়েছে, তবে কঁচা; এখনো পাকেনি। রোসন আমাকে বলল,-আমাকে দুটো শশা দেবে?
-না দেওয়ার কি আছে? আয়, এই দিকটায় এসে দাঁড়া। আমি শশা দিচ্ছি তোকে। ক্ষেতের দরজার ডানদিকে ওকে দাঁড় করিয়ে আমি শশা তুলতে গেলাম।
-সাহেব-কামাল, তোমাদের আঙুর পাকলে আমাকে দেবে তো।
-দেব। যখনই তোর খেতে ইচ্ছে হবে, আমার কাছে চলে আসবি।
-মুশা, শাওয়ালি, কালাখান এরা কিছু বলবে না তো?
-কী বলবে? কেন আঙুরে আমার অধিকার নেই? আমার থেকেই তোকে দেবো। ওদের কাছে চাইব না।
-সাহেব-কামাল এবার আমি যাই। আকা নইলে বকবে।
রোসন চলে যাওয়ার পর আমি দুচারটে শশা নিয়ে ঘরে চলে এলাম। পরের দিন সকাল থেকেই আমাকে একের পর এক সবাই ডাকতে আসছে। কিন্তু আমার ওই এক কথা যাবো না। মুখে যাবো না বললেও, মন যেতে চাইছে। ভাবলাম চেম্বার বন্ধ করে যাবো। আজ রুগীর বেশি চাপ নেই। মাত্র দশ পনেরো জন্য এসেছে। দুপুর একটার মধ্যেই তাদের বিদায় দিয়েছি। তারপর সাদগিকে বললাম খাবার দিতে। রোসনদের বাড়ির পুব দিকে একটা মাঠের মতো আছে। সেখানে ছেলেদের নাচ হচ্ছে। আর বাড়ির ভেতর উঠোনে হচ্ছে মেয়েদের নাচ।
বেলা তখন প্রায় দুটো বাজে। আমি একটা ভালো সালোয়ার কামিজ পরে দোপাট্টা মাথায় দিয়ে বেরোতে যাবো এমন সময় জাম্বাজের পিসতুতো ছোটোভাই সৈয়দ খান দৌড়তে দৌড়তে এসে আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে একেবারে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো।
-কি হয়েছে? এত ডাকাডাকি কিসের? আমি তো যাচ্ছি?
-সাহেব কামাল, লিক পুম্বা রায়কা, যার কাওয়া। মানে একটু তুলো দাও। তাড়াতাড়ি করে।
–তুলো কি হবে?
–রোসেন্দার, আকপল জান ইস্তালাই। মানে-রোসন নিজের মাথায় গুলি করেছে।
-কি করে? কেমন করে এমন ঘটনা ঘটল?
-কার বাইন বন্দুক নিয়ে রোসন আকাশে গুলি চালাচ্ছিল। যখন সব গুলি শেষ হয়ে গিয়েছে ভেবে ও পাঁচিলের ওপর বসেছে, তখন বন্দুকটা এমন ভাবে রাখল যে নলটা ওর কপালের দিকে তাক করা রইলো। হঠাৎ একটা গুলি বেরিয়ে রোসনের কপাল খুঁড়ে মাথার পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে।
সর্বনাশ! এ কি সর্বনাশ হয়ে গেলো? দ্রানাইচাচার প্রথম সন্তান। বাচ্চা মেয়ে, বাবানের স্বামী। আমি সৈয়দ খানের সঙ্গে দৌড়ে গেলাম। ময়দার মতো মিহি ধুলোর ওপর দিয়ে খালি পায়ে দৌড়চ্ছি। বরফ পড়ার পর তিনমাস, বরফ গলে যাওয়ার পর দুমাস এবং মে ও জুন মাসে বৃষ্টির সময়টুকু ছাড়া বাকি সময়টায় এই ময়দার মতো ধুলো এখানকার মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে।
বিকেল পাঁচটা বাজে। ১৯৯২-এর ১৬ই জুলাই। চারদিক রোদে ঝলমল করছে। সূর্যের তাপ প্রখর। কোথাও আর ঢোল বাজাবার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। নাচ গানও থেমে গেছে। ঘরের দেওয়ালে বুকফাটা কান্নার প্রতিধ্বনি। রোসনের মা হতভাগী ধুলোর ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগল–ওরে বোসন, তুই কোথায় গেলিরে? তোর কচি বৌ যে তোর সঙ্গে এখনও ভালো করে কথাও বলেনি। ওরে আমার বাছা, আমার কোলে ফিরে আয়রে, আজ পাঁচদিন তোকে ভালোমন্দ খেতেও দিইনি আমি। আমার কোলের বাছা, আমার মানিকরে, একবার এসে আমার কোলে মাথা রাখ সোনা। আয়রে ফিরে আয়।
এমন সময় রোসেন্দরকে একটা খাটের ওপর শুইয়ে সবাই মিলে বাড়ির ভেতর উঠোনে নিয়ে এল। সেরিনা চাচি, মরগালারা চাচি, আবু, আরো সবাই রোসনের ওপর আছড়ে পড়লো। আমিও গিয়ে রোসনের পাশে দাঁড়ালাম। মুখে বিলাপ নেই আমার। শুধু একটা অস্ফুট যন্ত্রণা। ভীষণ একটা কষ্ট কালবৈশাখী ঝড় হয়ে তছনছ করে দিচ্ছে আমার মনের ভেতরটা। যে ঝড় কোনও দিন থামবে না। রোসন শুয়ে আছে। কাফন দিয়ে সমস্ত শরীর ঢাকা। শুধু মুখটুকু খোলা। ঠিক কপালের মাঝখানটা তারই নিজস্ব কারাবাইন রাইফেলের গুলি এফেঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে গিয়েছে। অপার্থিব জগতে চলে গেল রোসন। রেখে গেলো পার্থিব জগতের হাসিকান্নায় মেশানো স্মৃতির বেদনা। আমার ও সবার জন্যে মন কেমন করা অনেক কথা। মায়ের জন্যে রেখে গেল অসংখ্য বাবলা কাটা-বেঁধানো একরাশ যন্ত্রণা। এত দুঃখের মধ্যেও আমি লক্ষ করলাম, রোসনের বিবিকে কেউ রোসনের কাছে নিয়ে এলো না। ভালোবাসা কি? তা বোঝার আগেই সে তার একান্ত আপন মানুষটাকে হারাল। শেষ দেখাটুকুও দেখতে পেল না। অসহ্য যন্ত্রণা আর অনেক টুকরো টুকরো স্মৃতি নিয়ে সে ঘরের কোণে, এক নির্জন কোণে বসে ঝাপসা নয়নে সমস্ত ঘরটাতে যেন কি খুঁজতে লাগলো। বোধহয় রোসনকেই খুঁজছে। সুখস্বপ্নের ঘরটা আজ তার কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন। কোনও দিন সে আর আসবে না তার ঘরে। বলবে না কথা তার সঙ্গে। তবুও সে সবাইকে যেন চুপিচুপি বলে, শুনবে তার কথা? সে আমার একান্ত আপন ছিল, সে ছিল আমার। এত কষ্টের অবসান বাবানের ঘটেছে কিনা জানি না, তার একান্ত আপন মানুষটা কতদিন আর তার ছিল তাও আমি বলতে পারব না। কিন্তু বছর ঘুরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোসনের বিবি হয়ে গেল রোসনের ভাই মিরাওজলের বিবি। মিরাওজল দ্রানাইচাচার মেজো ছেলে। বাবান অনেক কেঁদেছিল দ্বিতীয় বিয়ে করবে না বলে। আর কাউকে স্বামী বলে মেনে নিতে পারবে না। আছাড় খেয়ে বাবান বারান্দার নিচে পড়ে চোখের জলে বুক ভাসালো। তবুও বাবান বিয়ে করতে রাজি না হয়ে পারলো না। এখানেও সেই পরাধীনতা। বাবান যদি অন্য কাউকে বিয়ে করতে চায়, তা সে পারবে না। বাবানের জীবন পরনির্ভরশীল। শ্বশুরবাড়িতে, বাবার বাড়িতে, সর্বত্র মেয়েরা পরাধীন। কিন্তু কেন? কেন হবে মেয়েরা পরাধীন? কেন পাবে না মেয়েরা স্বাধীনতার সুখ? সমস্ত পরাজয়ের গ্লানি কেন শুধু মেয়েদের জন্যে? আমাদের দেশেও কমবেশি আছে এই পরাধীনতা। হিসেব করে দেখলে দেখা যাবে পুরুষদের থেকে মেয়েদের শক্তি সর্বক্ষেত্রে অনেক বেশি। বরং পুরুষরাই বেশি নির্ভরশীল। বাবা মারা গেলেও মা কিন্তু তার সন্তানকে যেমন করেই হোক মানুষ করে তোলেন। সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে মা শত সহস্র দুঃখকষ্ট নীরবে সহ্য করেন। নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ বিসর্জন দেয়। আর সেক্ষেত্রে একজন পিতা পারেন কি তার সন্তানকে ঠিক মায়ের যত্ন দিয়ে গড়ে তুলতে? নিজের সুখের জন্যে হয় দ্বিতীয় বিয়ে করেন; নতুবা রিপুর তাড়নায় বারবনিতার কাছে যান। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। কিন্তু ব্যতিক্রম নেহাত ব্যতিক্রমই। একটা পুরুষের যদি রিপুর তাড়না থাকে, তবে একটা মেয়ের কি তা নেই? নাকি মেয়েরা ক্লীবলিঙ্গ? পুরুষ যদি নিজের মতে বিয়ে করতে পারে তবে মেয়েরা কেন তা পারবে না? জোর করে বাবানের বিয়ে দেবে আবার। এই খবরটা শুনে সেদিন আমার শরীরে সমস্ত রক্ত যেন প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলেছে। কিন্তু আমার সীমিত ক্ষমতায় কতটুকুই বা করতে পারি? আবার ভাবি বিয়ে না দিয়েই বা কি করবে? বাবানের কিইবা বয়স? কিন্তু তা বলে জোর করে? ইচ্ছের দাম নেই।
বাসে, ট্রামে, হাটে, বাজারে সবখানেতেই পুরুষরা মেয়েদের ফার্স্ট প্রেফারেন্স দেয়। সিনেমার লাইন হোক, আর রেশনের লাইন হোক, সবাই বলে ছেড়ে দে ছেড়ে দে, মেয়ে মানুষ। আর মেয়েরাও খুশি হয়ে, বিগলিত হয়ে ছেলেদের কৃতজ্ঞতা জানায়। কিন্তু বুঝলো না যে পুরুষরা তাদের অবলা ভেবেই সুযোগ দিল। কেন নেব সেই সুযোগ? যে সুযোগ আমাদের অবলা, মেরুদণ্ডহীন করে দেয়? কেন জগতের সমস্ত মেয়েরা মাথা তুলে এসব অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে না? মাথা নত করে সব কিছু কেন মেনে নেয়?
ভারতে এই সব অত্যাচার কিছুটা শিথিল হয়েছে। কিন্তু আফগানিস্তানে এখনো সব মেয়েরা পরাধীন। তালিবানরা এসে আরো বেশি করে ঘরের কোণে মেয়েদের ঠেলে দিয়েছে।
কি জানি বাবানের দ্বিতীয় স্বামী কেমন হবে। হয়তো কিছু ভালবাসা, নয়তো বা অনেক অমিল। কিন্তু তবু মেয়েদের স্বামীর ঘর করতেই হবে। স্বামীই একটা মেয়ের যথার্থ ঠিকানা। মেয়েদের নিজের কোন ঠিকানা নেই। বিয়ের আগে বাবার ঠিকানা, বিয়ের পরে স্বামীর ঠিকানা, বৃদ্ধা হলে ছেলের ঠিকানা। কিন্তু একটা ছেলের ঠিকানা কেন মেয়ের ঠিকানার সাথে জোড়ে না? কেন বিয়ের পরে ছেলেরা
মেয়েদের বাড়ি আসে না? মেয়েদের বাড়ি আসা নাকি তাদের পৌরষত্বের অপমান। চমৎকার। সামান্য আসা যাওয়ার মধ্যেই কি পুরুষের পৌরষত্বের মান অপমান সীমাবদ্ধ? নাড়ির ওপর অত্যাচার অপমান নয়? এক নাড়িতে সীমাবদ্ধ না থাকা অপমান নয়? এক নয়, একাধিক মেয়েকে শয্যা সঙ্গী করা কি অপমান নয়? নাকি অপমানের ক্ষেত্রটা শুধু মেয়েদের বেলা প্রযোজ্য?
একটা মেয়ে এক ছেড়ে দ্বিতীয় গ্রহণ করলে সে হয়ে যায় বেশ্যা। খারাপ নামের পদবি তার নামের সাথে জড়িয়ে দেওয়া হয়। একটা পুরুষকে এই কলঙ্ক থেকে কেন মুক্ত রাখা হয়? আমার ছোটকাকার প্রথম স্ত্রী, একটি মেয়ে জন্ম দিয়ে। পরপারের টিকিট কাটলেন। আর এক বছর যেতে না যেতে ছোট কাকা দিব্যি বর সেজে আর একটা নতুন বৌকে ঘরে নিয়ে এলেন। আমার ঠাম্মা, মা, মেজো কাকিমা আবার উলুধ্বনি দিয়ে নতুন বৌকে বরণ করে ঘরে তুললেন। আর সেই সদ্যজাত কন্যা তখন আমার কোলে ঘুমে অচেতন। ছোটকাকার স্ত্রী বিয়োগে ঠাই বেশি ব্যস্ত হয়েছিল আবার বিয়ে দিতে। কিন্তু আমার ছোট পিসি! এক রাস রূপের ডালি নিয়ে সে মাত্র এগারো বছর বয়সে নতুন বৌ হয়ে, একটা তিরিশ বছর বয়সী স্বামীর ঘর করতে গেলো। বুরো স্বামীর সাথে সতীনও তার ভাগ্যে মিলেছিল।
তারপর? দুবছর বাদে পরপর তিন ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম হল। সবার ছোট ছেলে যখন জন্মালো তখন বিশ্বের পুরুষের মনকে পাগল করে দেওয়ার মতো রূপ নিয়ে পিসি বিধবা হল। আমি তখন মায়ের পেটে ছমাসের প্রণ। তখন কিন্তু আমার দাদু বা ঠামা ছোট পিসিকে পাত্রস্থ করার তাগিদ অনুভব করেনি। এই দিক দিয়ে আফগানবাসি অনেক উদার। ছোট পিসি চার ছেলে মেয়েকে নিয়ে ভাইদের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষের ঝুলি পেতে দাঁড়াতো। কিন্তু মাত্র পঁচিশ বছর বয়সের অপরূপা অসম্ভব ব্যক্তিত্বের মহিলা জীবনের সাথে আপস মীমাংসা করে নিয়েছিলেন। ভুলে গিয়েছিলেন যে তার জীবনেও কিছু চাওয়া-পাওয়া আছে। তার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান তখন ছেলেদের মানুষ করতে হবে। মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে। স্বামীর কাছে যথার্থ সুখ সে কি পেয়েছিল? এই প্রশ্ন একদিন আমি তাকে করেছিলাম।
পিসি বলেছিল-সুখ কি তা জানি না। তবে তোমার পিসেমশাই যখন রাতের অন্ধকারে আমাকে তার উষ্ণতার শিকার করত,-তখন হয়তো ছেলে কেঁদে উঠতো। তা বলে তোমার পিসেমশাই নিরস্ত হত না।
পিসির কথা শুনে এক অজ্ঞাত হিংস্রতা আমার মনের মধ্যে স্থান করে নিল। মনে হতো যদি পিসে বেঁচে থাকতো; তবে এক ঘুষিতে তার লম্বা নাকটা আমি ফাটিয়ে দিতাম। মেয়েরা এতই নগণ্য যে তাদের মনের ইচ্ছে অনিচ্ছার কোনও মূল্য নেই? তবে পিসি হেরে যায়নি। তিন ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করে তুলেছে। একটা পুরুষ যা না পারে পিসি তাই করেছে। একা, কারো সাহায্য ছাড়া, বাবা, ভাইদের দয়ার দান গ্রহণ করে সে বড় ছেলে, মেজো ছেলেকে রামকৃষ্ণ মিশনে রেখে পড়িয়েছে। মেয়েকে পি. ডব্লিউ. ডি-এর কন্ট্রাক্টরের সাথে বিয়ে দিয়েছে। ছোট ছেলেকে দেগঙ্গা হাইস্কুলে পড়িয়েছে। এখন, বড় ছেলে একটা উডেন ফ্যাক্টরি করেছে, মেজো ছেলে রামকৃষ্ণ মিশনেই টিচারি করে। ছোট ছেলে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিসে চাকরি করে। আজ সে সুখি! কি করে বলি সে সুখি? এত কষ্ট করে, জীবনের সব স্বার্থ, কামনা, বাসনা ত্যাগ করে যাদের সে মানুষ করে তুলেছে, আজ সবাই আলাদা। যে যার পথ দেখে নিয়েছে। পিসি একা, সম্পূর্ণ একা। সেই কার্তিকপুরের পুরনো ভিটে বাড়িতে সে একাই থাকে। চৈত্রের দুপুরে অথবা শীতের পরন্ত বিকেলে, বাড়ির বারান্দার কোনায় থামের গায়ে হেলান দিয়ে বসে, জীবনের হিসাবটা হয়তো মেলায়। অনেক অনেক দুঃখ হয়তো তার বুকের ভিতরের হৃৎপিণ্ডটাকে দীৰ্ণবিদীর্ণ করে দেয়। পচা গরমে হয়ত গল্ গল্ করে তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ঘাম ঝরে পড়ে। নতুবা শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীরের ভিতরের হারগুলোতে কাঁপুনি ধরায়। সামনের নারকেল গাছের একটা পাতা বিশাল ডাল শুদ্ধ দমাস আওয়াজে নিচে মাটিতে এসে পড়েছে হয়তো। পিসি হয়ত নির্বাক নয়নে বসে সেই ঝড়ে পরা পাতাটার দিকেই চেয়ে আছে।
এই ছোট পিসিকে আমি ভীষণ ভয় পেতাম। যতটা ভয় পেতাম তার অনেক বেশি ভালবাসতাম ও শ্রদ্ধা করতাম। প্রতিবাদের কথা ভাবতে গিয়ে যেন রামায়ণ রচনা করে ফেললাম। অথচ এখন আমার বিন্দুমাত্র সময় নেই। মুশা আমার কাছে টাকা চেয়েছে। যে টাকার ওপর ওর কোনও অধিকার নেই। টাকাগুলো সম্পূর্ণ আমার। হিন্দুস্থানে যাওয়ার খরচা। সেই টাকা চাইছে মানে ওরা মনস্থির করেছে যে আমাকে যেতে দেবে না। তার মানে টেলিফোনের সমস্ত কথাই মিথ্যে। আমার সামনে একরকম কথা হয়েছে, আর আমার অগোচরে আর একরকম। অভিষেককেও ওরা মিথ্যে বলেছে।
আবার ভাবি। অভি যখন দেখবে আমি দেড় মাসের মধ্যে গেলাম না তখন কি জাম্বাজকে ও কিছুই বলবে না? নাও বলতে পারে। অভি খুব শান্তিপ্রিয় ছেলে। সে কি কোনও ঝামেলায় যাবে? তার থেকে ভালো আবার এখান থেকে পালানো। পাকিস্তানে যাওয়ার পর মোটামুটি একটা সাহস নতুন করে পেয়েছি। বহু বছর একটা গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে সাহস হারিয়ে ফেলেছিলাম। হৃত সাহস পুনরুদ্ধার করেছি। সুতরাং আবার পথ হারাতে হবে। বাড়ি ছেড়ে অজানার পথে পা বাড়াতে হবে। কিন্তু এবার পালানো অত সহজ হবে না। এখন তিহার জেলের মতো পাহারায় সবাই মোতেয়ান।
সারারাত ঘুমোতে পারলাম না। ভাবতে লাগলাম কী করা যায়। জানালার ঠিক নিচে তো শাওয়ালি শোয়। ওকে ডিঙিয়ে পালালে কেমন হয়? তারপর আঙুর বাগানে গিয়ে ভাঙা দেওয়াল টপকে পালাবো। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলাম। জানালার কাছে গেলাম। শাওয়ালির শোওয়ার দূরত্বটা বোঝার চেষ্টা করলাম। না, পারবো না ডিঙ্গিয়ে যেতে। তারপর দরজার কাছে গিয়ে কালাখানের শোওয়ার পজিশানটা দেখলাম। আনন্দে মনটা নেচে উঠলো। কালা এমন ভাবে শুয়েছে যে আমি খুব সহজেই ডিঙিয়ে যেতে পারবো। শুধু ওর গভীর ঘুমের অপেক্ষা। আমাকে এখন থেকেই তৈরি হয়ে নিতে হবে। হঠাৎ কালার বিবি সাদগি বাইরে এসে কালার পাশে শুয়ে বলল,-জে. এও সাতকি ইলিয়ে সামালাম। মানে, আমি এখানে একটু শোবো। খোনেকে ডের গরমি দা। অর্থাৎ ঘরে খুব গরম।
প্রতিবার কেন এত আশাহত করছো আমাকে আল্লা? তথাকথিত হিন্দুর মেয়ে হয়েও আমি তোমাকে বারংবার ডেকেছি। মনে মনে তোমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি তাও কেন তুমি আমাকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিচ্ছ না? আজ আমি শেষ বারের মত তোমাকে অনুরোধ করছি আমার পালাবার পথ পরিষ্কার করে দাও। আল্লার কাছে অনুরোধ জানাবার পর ভাবলাম আমি তৈরি থাকবো। সাদগি উঠে গেলেই পালাবো। গুলগুটি নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমোচ্ছ। আমার চোখে ঘুম নেই। অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়ে হাতড়ে ভি আই পি বাক্সের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাতের অনুমানে লকে চাবি ঘোরালাম। যাতে আওয়াজ না হয় সেজন্যে ওকের ডান্টিটাতে হাত দিয়ে চেপে ধরে আস্তে আস্তে খুললাম। তারপর পাল্লাটা খুলেই, টাকাগুলো বার করলাম। পনেরো লাখ টাকা। ইন্ডিয়ান তিরিশ হাজার। এত টাকা কী ভাবে যে নেবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। একটা বড় ব্যাগ ছিলো আমার, তাতে টাকাগুলো নিলাম। দুটো চুড়িদার। জুতোটাও ভরে নিলাম। জুতো পায়ে থাকলে আওয়াজে ধরা পড়ে যাবো। তারপর কোরানশরীফ বুকে করে নিয়ে জানালায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন সাদগি উঠে যাবে। রাত কেটে গেল। পুব দিগন্তে ভোরের সূর্যের আগমন বার্তা বহন করে নিয়ে এলো পাখিরা। সাদগিও ওঠেনি। আমিও পালাতে পারিনি। ভোরে যখন শাওয়ালি ও কালা নামাজ পড়তে গেল; তখন দরজা খোলা পেয়ে আমি দৌড়ে দ্রানাই চাচার বাড়ি গিয়ে চাচিকে বললাম দিনটুকুর জন্যে একটু লুকোবার জায়গা দাও। আমি সব কথা বলে খুব কাঁদতে লাগলাম।
চাচিও আমার কান্নার সঙ্গে কাঁদতে লাগলো। তারপর বাড়ির বাচ্চাদের ছাড়া সবাইকে বলল সমস্ত ব্যাপার। চাচা বাড়িতে ছিল না। চাচি আমার লুকোনোর জায়গা ভাবতে লাগলো। যদি দেওররা সন্দেহ করে এখানে খুঁজতে আসে? এমন একটা জায়গায় লুকোতে হবে যেখানে কেউ খুঁজতে যাবে না।
পূর্বদিকের একটা ঘরের, ভিতর দিয়ে সিঁড়ির ছাদ অবধি উঠে গিয়েছে। সেই সিঁড়ির শেষ ধাপে, আমার লুকোবার ব্যবস্থা হলো।
চাচার বড় মেয়ে জরিনা, আর ভাইঝি বরি গিয়ে একটা তোষক সেখানে পেতে দিয়ে এলো। আমি তাড়াতাড়ি সেখানে চলে গেলাম। দশ মিনিট পরে, জরিনা আমার জন্যে একটা টি-পটে করে চা নিয়ে এলো, সঙ্গে দুটো পরোটা। আমি চায়ের সঙ্গে পরোটা খেতে লাগলাম। আর ভাবতে লাগলাম, এও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কেউ কি কখনও ভেবেছে–পালিয়ে গিয়ে তোষকের ওপর বসে, আরামে, নিশ্চিন্তে, চা আর পরোটা খাবে? এই কি জীবন? যে জীবনের স্থায়িত্ব আছে, নিশ্চিন্ত নেই। স্রোতহীন, গতিহীন, থেমে যাওয়া একটা জীবন।
আমি কি কোনদিন ভেবেছিলাম এসব?
একদিন আমাকে এই সব অনিশ্চয়তার সঙ্গে দোস্তি করতে হবে? আচ্ছা, অন্য ঘরের বৌদের কি আমার মতো অবস্থা হয়েছে কখনো? হয়তো হয়েছে কিংবা নয়। আর ভাবতে সময় দিল না অলস নয়ন। চোখের ওপরের পাতা দুটো যেন ভারী হয়ে নিচের সীমারেখার সঙ্গে মিলনে প্রবৃত্ত হতে চাইছে। হঠাৎ চমকে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি জরিনা আমার সামনে আতঙ্কের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। ঘুমের ঘোরে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না জরিনা আমার বিছানার সামনে কী করছে? তারপর জরিনার ঝাঁকুনিতে ঘোর কেটে গেলো। সম্বিৎ ফিরে পেলাম। আমি যে এখানে লুকিয়ে আছি!
–সাহেবকামাল! ওঠো-ওঠো। আর লুকিয়ে লাভ নেই। সব জানাজানি হয়ে গিয়েছে। আকাও বাড়ি এসেছে, বাবাকে কেউ কেউ আকা বলে।
সর্বনাশ। জানাজানি হয়ে গেছে? এবার তো আমাকে দেওররা মেরেই ফেলে দেবে! আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারলাম না। গলা শুকিয়ে এলো। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। ঘরের এ. কে ৪৭-এর কথা মনে পড়লো। সব জায়গায় খুঁজতে খুঁজতে ওরা নিশ্চয়ই রাগে মারমুখী হয়ে আছে। জরিনা বলল, আসাম চাচার একটা খোঁড়া ছেলে আছে। সে নাকি বলেছে, আমাকে দ্ৰানাই চাচার বাড়ি ঢুকতে দেখেছে। তখন চাচি নিরুপায় হয়ে একটু পরে ওদের কাছে বলেছে, ঝুমঝুমা চাচার ভাইপো সাওমদের বৌ আটার ঘরে আটা আনতে গিয়ে আমাকে দেখেছে। মুশা ও কালাখান বন্দুক নিয়ে ঘুরছে। আমাকে দেখলেই গুলি করে দেবে।
হায় ঈশ্বর ভাগ্যের এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস? বাবা-মায়ের সঙ্গে, ঠামার সঙ্গে, শেষ দেখাটুকুও করতে পারলাম না? মৃত্যু আজ আমার শিয়রে। কিন্তু আমি কাউকে ছাড়ব না।
সেই বিনাশহীন, অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াবো জাম্বাজের বাড়ির চার ধারে। বেঁচে থেকে আমি যা পারব না, মরে গিয়ে তা অনেক সহজ হয়ে যাবে। মারুক। আমাকে গুলি করেই মারুক। মৃত্যুই আজ আমার কাছে সঠিক পথ। আমার ভাবনার মাঝে জরিনা কখন যে উঠে চলে গেছে জানি না। যাবেই তো।
যাক আজ সব, সবাই, আমার সামনে থেকে চলে যাক। আমি উঠে দাঁড়ালাম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। হঠাৎ দেখলাম, সামনের দরজা দিয়ে সেরিনা চাচি ও মরগলরা চাচি ভেতরে ঢুকলো। মরগালারা দ্ৰানায়ের বড় বৌদি।
সেরিনা চাচি বলল,-হতভাগী, আজ চাচা তোক বাঁচিয়ে নিয়েছে।
-বঁচিয়েছে মানে? আমি ঠিক বুঝলাম না।
-কালাখান ও মুশাকে ডেকে বুঝিয়েছে যে, জাম্বাজ বদলা নিতে তোদর বৌদেরও মেরে ফেলবে। কারণ জাম্বাজ তোদের বলেছে সাহেবকামালকে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু তোরা আসাম খানের কথা শুনে, জাম্বাজের কথা উপেক্ষা করে তার বৌকে জোর করে ধরে রেখেছিস? তোরা কী বলবি? সাহেবকামালকে কেন মেরেছিস? বলবি পালিয়ে গিয়েছিল?
তখন জাম্বাজ জিজ্ঞেস করবে না–কেন পালিয়েছিল? কেন তোরা ওকে পাঠাসনি? নিজেদের সুন্দর সংসার এইভাবে নষ্ট করিস না।
একটা কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো। জাম্বাজ আমাকে ধরে রাখতে বলেনি। পাঠাতে বলেছিল। কিন্তু আসাম চাচা সবকলকাঠি নাড়ছে। নাটের গুরুমশাই তবে সে? যদি কোনদিন আমি হিন্দুস্থানে যেতে পারি তবে আসামখানকে আমি দেখে নেব। ফঁস করে দেবো, পাকিস্তানের রাস্তা দিয়ে, জাল পাসপোর্ট বানিয়ে দুমাসের নাম করে হিন্দুস্তানে গিয়েছে। কিন্তু আজ আড়াই বছর হয়ে গেল এখনও সে হিন্দুস্তানেই আছে। তারপর ইনকাম ট্যাক্স অফিসে খবর দেব যে, প্রতিমাসে অথবা তিনমাস অন্তর দুলাখ বা তিন লাখ টাকা সে চোরাপথে বাড়িতে পাঠায়। চাচির ডাকে আমার চিন্তার জাল ছিন্ন হলো।
-সাহেবকামাল চাচা এখুনি তোমার কাছে আসবে। এই বাবানের ঘরে তুমি বোস। চাচিরা চলে গেল। আমি ডানদিকের ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ঘরের এক কোনায় গিয়ে বসলাম। ভীষণ ভয় ও অনেক দুশ্চিন্তা থেকে আপাতত রেহাই। আর ভেবে নিলাম এই চাচিকে দিয়ে, চাচাকে বলে আমাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেই হবে।
কতক্ষণ এই ভাবে বসেছিলাম জানি না। হঠাৎ সামনের জানালা দিয়ে দেখলাম চাচা, কালা ও ছোট দেওর শাওয়ালি আসছে, এই ঘরে আমার কাছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। এত বিপদেও আমি আমার সৌজন্যতা ভুলিনি।
চাচা বড়, সুতরাং সম্মান তাঁর প্রাপ্য।
-কই সাহেবকামাল?
চাচা ভিতরে এসে আমার সামনাসামনি বসলো। কালা ও শালয়ালি দাঁড়িয়ে রইলো। চাচি, জরিনাও এলো, মরগালারা চাচি, বাবান, ঝুমঝুমা দরজার বাইরে দাঁড়ালো। চাচা বলল, এমন করে, আবার পালাতে যাচ্ছিলে কেন?
-আমাকে এক মাসের মধ্যে পাঠাতে বলেছে জাম্বাজ, কিন্তু ওরা পাঠাচ্ছে না। তাই পালানো ছাড়া আমি আর কী করতে পারি?
-পাঠাবে কী করে? আসাম তত বারণ করেছে পাঠাতে।
-আসাম কে? এখন তার বাড়ি আলাদা। আমার স্বামী বা গার্জেন জাম্বাজ। খুব উত্তেজিত হয়েই বললাম। তাছাড়া ভুলে গেছে ওরা–একদিন ভিখিরির মতো হাত পেতে দাঁড়াত আসামের বৌদের কাছে, একটু চিনি বা গুড়ের জন্যে। আজ তার কথা শুনে ওরা আমার প্রতি অত্যাচার করছে? আমার জন্যেই তো ওরা নিজেদের অবস্থান বুঝতে পেরেছে।
-আমি কালকেই মুশাকে পাকিস্তানে পাঠাবো। মুশা জাম্বাজের সঙ্গে ফোনে কথা বলে সব জেনে আসুক।
-ঠিক আছে। এতদিন অপেক্ষা করেছি। না হয় আরও দশদিন অপেক্ষা করবো। সব কথা শেষ হল। কথা হল কাল মুশা পাকিস্তান যাবে। আমি চাচাকে কথা দিলাম মুশা না আসা পর্যন্ত আমি আর পালাবার চেষ্টা করব না। আমি বাড়ি গেলাম না। চাচার বাড়িতেই থাকলাম। চাচা, খুব ভালো মানুষ। সবাই তাকে খুব ভালবাসে। চাচিরা আমাকে খুব যত্ন করত। চাচাও রোজ আমার জন্যে ভালো ভালো খাবার আনত। জিজ্ঞাসা করতে আমি কিছু খেতে চাই কিনা। অন্য কিছু চাই কিনা।
গজনি বাজার থেকে, শসা, জরদালু, কাঁচালঙ্কা, বেগুন কিনে আনতো। খেতে আমার ইচ্ছে করে না। কিন্তু চাচা অতদূর থেকে আমার জন্যে এনেছে, তাই না খাওয়া মানে তাকে অপমান করা। সেই জন্যে ইচ্ছে না থাকলেও খেতে হতো।
দ্বাদশ অধ্যায়
জুলাই মাসের পাঁচ। চাচার সঙ্গে মুশা কালা মিথ্যে বলেছিল পাকিস্তানে যাবে। ওরা যায়নি। আমার যাওয়ার ব্যবস্থাও করেনি। চাচাকে আমি বলেছিলাম, চাচা ওরা তো কোনও ব্যবস্থাই করছে না। এবার যদি আমি পালাই তবে আপনি কিন্তু আমাকে দোষ দেবেন না।
-না। আমি তোমাকে আর কোনও দোষ দেব না। ঈশ্বরের প্রতি আমার আর বিশ্বাস ছিল না। যাকেই সামনে পেতাম, তাকেই বলতাম, আমাকে একটা জিপ ঠিক করে দেবে? এক অতি দুঃস্থ মহিলাকে ধরলাম। তোমাকে দুলাখ টাকা দেবো। আমাকে একটা গাড়ি ঠিক করে দেবে? সে অস্বীকার করলো।
এদিকে চাচা আমাকে রাখতে আর সাহস পাচ্ছে না তার বাড়িতে। কারণ যদি চাচার বাড়ি থেকে পালাই, তবে দেওররা চাচাকে ছাড়বেনা। কী যে করবো? ভেবেই পাচ্ছিলাম না। বাড়ি থেকেও বেরোবার পথ বন্ধ। আমার দেওরদের আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম, পালিয়ে আমি যাবই। সোজা পথে আমাকে না পাঠালে, বাঁকা পথ ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই। কালা, মুশা, শাওয়ালির কোনও ভুক্ষেপ নেই। বদনামের তোয়াক্কা করে না। যথা রীতি খায় দায় আর ঘুরে বেড়ায়। অসহ্য, ভীষণ অসহ্য। কিছুতেই আমি সহ্য করতে পারি না, ওদের এই উদ্ধত ভাব। গুলগুটি আমার সব কাজ করে। তাকে সারাদিন আমাদের বাড়িতে কাজ করতে হয়। তাতেও সে কারো মন পায় না। অসুখ করলে এমনি এমনিই সারে। তার দুই মেয়ে। তাদের অসহায়ের মতো দিন কাটাতে হয়। কে দেখবে? স্বামী তো তাকে দেখে না। সে অন্য বিয়ে করে সুখে আছে। আমার দেওরদের জানোয়ার আখ্যা দিলে বোধহয় খুব কম বলা হবে। আমার সেজো দেওর মুশার জন্যেই আজ গুলগুটির এই অবস্থা। সামান্য একটু দৈহিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে আজ গুলগুটি সারা জীবনের জন্য তার স্বামীকে হারিয়েছে। মুশা কিন্তু ভালোই আছে। দিব্যি বিয়ে করে বিবি নিয়ে সুখে ঘর করছে। দৈহিক চাহিদার চাওয়া-পাওয়া কি শুধু মাত্র গুলগুটির ছিল? মুশার ছিল না? তবে কেন একজনের ঘর সংসার স্বামী হারিয়ে গেল? আর একজন পেল অপরিসীম সুখ, আনন্দ? পৃথিবীর সর্বত্র শুধু মেয়েদের পেতে হয় গরল, আর অমৃত নিয়ে যায় পুরুষরা! কিছুতেই আমি সহ্য করতে পারি না। মেয়ে বলে না, মানুষ হিসাবে।
আর কত দিন? কতদিন এই ভাবে মেয়েরা বঞ্চিত হবে? কিন্তু আমি কাবুলের বুকে দৃষ্টান্ত রেখে যাবো। যা এখানকার লোকে স্বপ্নেও দেখতে পায় না। আমি তা বাস্তবে দেখাব। আমি সওদাগরের থেকে তিরিশ মিটার খুব মোটা ইলাস্টিক কিনলাম। আগে আমার ঘরে ছিল কুড়ি মিটার। আমাদের বাইরের দেওয়াল হবে লম্বায় পনেরো মিটার। এবার ইলাস্টিকটা দুফেত্তা করে পাকালাম। উদ্দেশ্য ছাদে যাবো, তারপর অন্ধকারেই ইলাস্টিকের সাহায্যে দেওয়ালের ওপারে নেমে পালাবো। যে পথে ওরা খুঁজতে যেতে পারে, তার উল্টো পথে দৌড় লাগাব। আমার পরিকল্পনার কথা চাচিরা ও গুলগুটি জানতো।
একদিন যায় দুদিন যায়। অপারেশন সাকসেস হয় না। সুযোগই পাই না। অবসন্ন, অবসাদে দিন কাটে, কোনও কিছুতেই কিছু হয় না। এর মধ্যে একদিন দ্রানাইচাচার বাড়িতে, নিমন্ত্রিত অতিথিরা আসবে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করবে। চাচি আমাকে ডেকে পাঠালো। আগেই বলেছি, ওদের দেশের মেয়ে শুধু রুটিটাই ভালো করতে জানে। অন্য রান্না পারে না বললেই চলে। তাই চাচি আমাকে রান্না করতে বলল। আমি মাংসের কোরমা, আলু বোখারার চাটনি, চাল গুঁড়ো করে ফিরনি, চিকেন দোপিঁয়াজি, আর মাটন বিরিয়ানি রান্না করলাম। আমাকে বাবান ও ঝুমঝুমা সাহায্য করেছে। জরিনাও হাত লাগিয়েছে। এরা সবাই আমাকে ভীষণ ভালবাসে। আমি ওদের বাড়ি গেলে আমাকে মাথায় করে রাখে। আমার জামা পর্যন্ত বাবান ও ঝুমঝুমা কেচে দেয়। আমার শ্বশুর বাড়ির সবাই খারাপ না। আবু খুব ভালো। আবু ডাকাবুকো মহিলা। কারো তোয়াক্কা করে না। আর আমার ননদ গুনচা খুব ভালো। সে তার ভাইদের চিনতো, তাই তার স্বামীকে দিয়ে আমার জন্যে, সাবান, শ্যাম্পু, মুসুর ডাল, টাকা, পাঠিয়ে দিত। আসলে গুনচা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। গুনচার ছোট দেওর একবার গুনচাকে বালতি দিয়ে মেরেছিল। বালতির বাড়িটা পড়েছিল তার কোমরের পিছনের হাড়ে। তার প্রায় দুবছর বাদে ব্যথা হতে ডাক্তার দেখাল তার স্বামী রম্মাজান
ডাক্তার সব টেস্ট করার পর বুঝলো যে টি.বি হয়েছে। Myconex 800 mg. ওষুধ Ethambutal, ভিটামিন B.Com; ও আর দুটো যেন কী দিয়েছিল। রম্মাজানের যা রোজগার তাতে তার ক্ষমতার বাইরে এই সব ওষুধ পথ্য জোগাড় করা। তখন জাম্বাজকে খবর দিল। জাম্বাজ ভাবলো যাবে বোনকে দেখতে। আর কিছু টাকাও দেবে। আমিও জাম্বাজের সঙ্গে যাবো বলে তৈরি হতে লাগলাম। ঠিক হলো গুনচাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসবো। বাদ সাধলো আসাম চাচার বৌ পাবলু। নিজের ছাড়া কারো ভাল সে সহ্য করতে পারে না। বাপ মরা মেয়ে গুনচাকে, এক লাখ টাকা তখনকার দাম, এখানে পঞ্চাশ হাজার। পণ নিয়ে, এক কাপড়ে বিদেয় করেছিল। প্রতিবাদ করার কেউ ছিল না। আজ কোথা থেকে এত হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষরা এসে হাজির হল? সেটা পাবলুর চিন্তার বাইরে। তাই বাদ সাধা ছাড়া আর তার কাজ, কিই বা হতে পারে? কিন্তু পাবলু জানে না আমাকে চেনে না আমার দৃঢ়তাকে। জাম্বাজ রাতে ঘরে এসে আমাকে বলল,–পাগলি, চাচি বলছে, গুনচা নিজের শ্বশুর বাড়িতেই থাক, ওর স্বামীই ওকে চিকিৎসা করবে। তাছাড়া একবছরও তো হইনি এখনো, গুনচাকে এখানে এনে রেখেছিলাম আবার তার মানে? সব ঠিকঠাক, কাল আমরা যাবো, আর আজ তুমি এই কথা বলছ?–
-পাবলু আকিই সবাই পাবলুকে আকিই বলে, বলছে যে গুনচার এখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তার স্বামীই তাকে যা করার করবে। আর তাছাড়া, আমাদের এখন। নতুন ব্যবসা, সেখান থেকে টাকা চেয়ে পাঠালে মুশা কি দিতে পারবে?
-আজ দেড় বছর হয়ে গেল, মুশা কি একটা টাকাও বাড়িতে পাঠিয়েছে?
-না তা পাঠায়নি। তোমার ওষুধের দোকান থেকে বা তোমার ভিজিটের টাকা দিয়েই সব চলছে বলে, আমি মুশার কাছে টাকা চেয়ে পাঠাইনি।
-তবে? আজ যে আমি গুনচার কাছে যাচ্ছি, বা তাকে আনবো, সেও তো আমারই টাকা?
-কিন্তু ভেবে দেখ টাকাগুলো থাকলে, আমাদেরই তো থাকবে। খরচা করে কি লাভ?
-জাম্বাজ, আজ যদি তোমার মেয়ে হয় আর ঠিক এই রকম হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও কি তুমি এই কথাই বলবে? তাই যদি বলো–তবে আমি যেন কোনদিন মা না হই আর তুমি বাবা।
আজ তুমি যে ব্যবসার দোহাই দেখাচ্ছ? তাতে ওর অধিকার নেই? ও কি তোমার মায়ের জারজ সন্তান? তোমার বাবার ঔরসে জন্ম হয়নি? আমার কথার মধ্যে কী জ্বালা ছিল, কে জানে। জাম্বাজ আর অমত করল না। আমি ও জাম্বাজ গিয়ে গুনচাকে নিয়ে এসেছিলাম। তাকে পথ্য দিয়ে, ওষুধ দিয়ে, সেবা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছি। আজ সে সম্পূর্ণ সুস্থ।
থাক এবার ননদের কথা। আমার কথায় ফিরে আসি। আমি চাচার বাড়ি যে রান্না করেছিলাম তা খেয়ে সবাই ভালো বলল। তারা নাকি এমন রান্না, এর আগে কোথাও খায়নি। খাওয়া দাওয়ার পর সবাই চলে গেল। আমি বাবানের ঘরে গিয়ে শুয়ে রেস্ট নিচ্ছিলাম। এমন সময় ছোট দেওর শাওয়ালি এল। বলল, দশটা বাড়ির পরে, জায়েরসা বলে একজনের বাড়িতে যেতে। কারণ তার বিবিকে স্যালাইন লাগাতে হবে। এখানে কথায় কথায় সবাই স্যালাইন লাগায়। ভাবে এতে শরীরে জোর পাবে। আমি বললাম, এখন আমি কী করে স্যালাইন চালু করব? কম করেও এক ঘণ্টা সময় লাগবে। আমাকে সেখানে বসে থাকতে হবে সেই একঘণ্টা। এখন পাঁচটা বাজে। স্যালাইন শেষ হবে ছটা বা সাড়ে ছটা। তখন রাত হয়ে যাবে। একা আমি আসব কী করে? তুই যদি আমার সঙ্গে যা, বসে থাকি আমার জন্যে তবে আমি যাবো। নতুবা নয়।
-আমি কি তোমার চাকর যে বসে থাকব?
-তবে আমি যাবো না।
-জায়েরসা তোমাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবে।
এ কি কথা শাওয়ালি? লোকে কী বলবে? একটা অন্য লোকের সঙ্গে, রাতের অন্ধকারে সাহেবকামাল আসবে।
-যখন পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিলে? সেরিনা চাচি এবার বলল,-সে তো একা পালিয়েছিলো। কোনও লোকের সঙ্গে তো পালায়নি।
একটু বেশি তর্কাতর্কি হওয়ার পর, শাওয়ালি হঠাৎ আমার মুখে সজোরে একটা ঘুষি মারল। আমি মুখটা সরাবার সময় পাইনি। ঘুষিটা এসে আমার নাকে লাগল। নাক দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়তে শুরু করল। চাচিরা দৌড়ে আমার কাছে এসে, আমার মাথাটা নিজের কোলের মধ্যে করে নিয়ে বসে পড়ল। বাবান ছুটে গিয়ে জল নিয়ে এল। আমার নাকে, মুখে জল দিতে লাগল।
সেরিনা চাচি এবার শাওয়ালিকে বলল,-বেরিয়ে যা, চলে যা আমার বাড়ি থেকে। বিনা দোষে একটা মুশাফিরের উপর এত অত্যাচার আল্লা সহ্য করবে না। সর্বনাশ হবে তোদর। নাদির চাচা দ্রানাই চাচার বড়। তার ছোট ছেলে একটা বড় মাটির ঢেলা তুলে শাওয়ালিকে উদ্দেশ্য করে মারল। ওই চার বছর বয়সের ছেলেও বুঝতে পেরেছে যে, অন্যায়টা শাওয়ালির। জরিনা আমার জন্যে গরম চা করে নিয়ে এল। ঝুমঝুমা আমার গায়ে রক্তের দাগ মুছতে ব্যস্ত। বাচ্চারা সবাই আমার চারপাশে চুপ করে বসে আছে। এত দুরন্ত সব বাচ্চা মুহূর্তে কেমন যেন শান্ত হয়ে গেছে। বাচ্চাগুলোকে দেখে এত কষ্টেও আমার হাসি পাচ্ছিল।
-দেখলে তো চাচি? এই রকম অত্যাচার করে আমার ওপর। আজ আমি তোমাদের স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, এবার আমি যাবো। আর নয়। দেখি ওদের কোন পাহারা আমাকে ধরে রাখতে পারে?
-যাও। পালিয়েই যাও। যদি চাচার কাছে আসে তখন চাচা বলবে, আমার কথা তো তোমরা শোননি? তার উপর অত্যাচার করেছে। এখন আমার কাছে এসে কোনও লাভ নেই। আমি তোমাদের কোনও সাহায্যই করতে পারব না।
-চাচি, চাচা যদি আমাকে খুঁজতে না যায় তবে ওরাও খুঁজবেনা। আমি পালিয়ে সোজা গজনির পথ ধরব। তুমি চাচাকে বলবে চাচা যেন ওদের গড়দেশের পথে খুঁজতে পাঠায়।
রাত্রে চাচা বাড়ি এলে, চাচি সব ব্যাপারটা বলল। শুনে চাচা শাওয়ালির ওপর ভীষণ রেগে গেলো। তখুনি যেতে চাইছিলেন ওর কাছে। কিন্তু আমরা বারণ করলাম। আমি চাচাকে আমার বক্তব্য বললাম।
চাচা বলল, এবার তুমি যা ইচ্ছা করো, আমি আর বাধা দেব না।
মুশা পাকিস্তানে গেছে, আমাকে হিন্দুস্থানে পাঠাবার খবর আনতে নয় জম্বাজের কাছ থেকে টাকা আনতে। যত টাকাই হিন্দুস্তান থেকে আসুক না কেন, টাকা ঘরে থাকে না। থাকবে কী করে? বিবিকে রোজ, মেওয়া, আপেল, চুরি করে খাওয়ালে? আজ ঘড়ি, কাল কাপড় পরশু চটি আসছে। প্রচুর জিনিস বাপের বাড়ি পাঠাচ্ছে। অথচ বাড়ির অন্যান্য সবাই, আলুর তরকারি ও রুটি খেয়ে দিন কাটাচ্ছে।
মুশা ভাবে, সবাই বোকা। কেউ কিছু বোঝে না। আঙুর পাকলে, বস্তা ভর্তি করে শ্বশুর বাড়ি পাঠাচ্ছে। অথচ, আসাম চাচার বাচ্চাগুলো একটা দানা পায় না। আসাম চাচার ভাগে আঙুরের বাগান পড়েনি। আসাম চাচার সঙ্গে যত শত্রুতাই থাক তার বাচ্চাগুলো তো কোনও দোষ করেনি। তবে কেন ভাবব না তাদের জন্যে?
গুলগুটির মা ছিল জাম্বাজের নিজের পিসি। সে আজ বেঁচে নেই। কিন্তু তার ছেলেমেয়েরা তো আছে? মুশার ও কালা খানের শ্বশুরবাড়ির লোকেদের আঙুর খাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু পিসতুতো ভাই বোনেদের অধিকার নেই। আমি এই সব অন্যায় সহ্য করতে পারি না। অসহিষ্ণুতা বেড়ে যায়। প্রতিবাদ হয় না। ক্ষমতাহীন দায়িত্ব নিয়ে দিন কাটে। আবার টাকা আসবে, আবার তা পরের ঘরে ভর্তুকি দিতে শেষ হয়ে যাবে। যাক শেষ হয়ে, ধ্বংস হোক। এবার আমাকে যে করেই হোক পালাতে হবে।
মুশা বাড়ি নেই। এই সুযোগ। মুশার সাহসে শাওয়ালি, কালা সাহসী। আবু বলল মুশা পাকিস্তানে গিয়েছে নিশ্চই এবার এসে তোমাকে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু আমি আর বিশ্বাস করতে পারি না তার থেকে পালানোই ঠিক মনে হল। ভাবলাম এমন হতে পারে কেউ খুঁজতেও যাবে না। সুতরাং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। আর এখন না পালাতে পারলে আবার সাত মাস অপেক্ষা করতে হবে। ঠাণ্ডা পড়ে যাচ্ছে। এর পর বরফ পড়বে। তারপর আবার তা গলবে। না কিছুতেই নয়। যখন আমি এই সব সাত পাঁচ ভাবছি তখন হঠাৎ দেখলাম শাওয়ালি বাড়ির উঠোনের আপেল, পেস্তা, জায়ফল গাছে জল দেবে বলে বেলচা নিয়ে যাচ্ছে। উত্তম। পালাবার উৎকৃষ্ট জায়গা। যেখান দিয়ে শাওয়ালি বাড়ির ভেতরে জল প্রবেশ করায়; সেই জায়গাটা দিয়ে একটা মানুষ অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারে। জল ঢোকানো হয়ে গেলে ওই জায়গাটা আবার মাটি ও ঝোঁপঝাড় দিয়ে বন্ধ করে রাখে। আজ জল দেবে, তারপর মাটি দেবে। দুতিন দিন মাটিটা কঁচা থাকবে। কঁচা মাটি হাত দিয়ে খুঁড়ে সরানো যায়। মনের কোণে একটা আশা জাগলো। ওখান থেকেই আমাকে বেরোতে হবে। ইলাস্টিকের আর প্রয়োজন হবে না। একটা ভীষণ উত্তেজনায় আমার সমস্ত শরীর থিরথির করে কাঁপতে লাগল। দুপুরে খাওয়াটাও ঠিক যেন ভালো লাগলো না। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল। গুলগুটিকে আমি, আমার প্ল্যানের কথা সব বললাম। ও আমার সঙ্গে আমার ঘরে শোয়। তাই ওকে শিখিয়ে দিলাম যে, ভোরে যখন ও নামাজ পড়বার জন্যে উঠবে, তখন সবাইকে ডেকে তুলে বলবে, সাহেবকামাল ঘরে নেই। ভোরের আগে যেন কোনও মতেই কাউকে না ডাকে। ততক্ষণে আমি অনেক দূরে চলে যাবো।
–অত রাতে একা তুমি যাবে? তোমার ভয় করবে না?
-মানুষ যখন মরিয়া হয়ে যায়, তখন তার ভয়, ভাবনা, বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে না। বেশ প্রত্যয়ে সঙ্গেই আমি উত্তর দিলাম।
–সাহেবকামাল। ভেবে দেখো, গভীর রাতে তুমি যেতে পারবে তো? রাস্তা চিনবে তো? গুলগুটি সন্দিহান। আমি বুঝতে পারলাম। বললাম,
-তোমাদের বাড়ির রাস্তা ধরে যাবো। সোজা শালো বাজার পেরিয়ে মদখেল ছাড়িয়ে বন্ধের উপর দিয়ে গজনী যাবো। সোজা রাস্তায় ওরা খুঁজতে পারে তাই ঘুরের রাস্তায় যাবো।
-কিন্তু এই সব রাস্তায়, ধারে ধারে তো কবর আছে, যদি কিছু অঘটন ঘটে?
-অঘটন যদি ঘটেই, ঘটুক। আজ সাত বছর ধরেই তো আমার জীবনে অঘটন ঘটছে। নইলে মুশা, কালা, শাওয়ালির মতো লোক আমার গায়ে হাত তোলে? কোনও দিন কি আমি ভাবতে পেরেছিলাম–এদের মতো লোকও আমার পাহারাদার হবে? এদের ভয়ে আমি গুটিয়ে থাকব? আসলে ভয়ে নয়; লজ্জায় আমি ওদের থেকে দূরে থাকি। ওরা অত্যাচার করে তাতে ওদের লজ্জা করে না। আমার প্রতি অত্যাচার করে তাই আমার লজ্জা। বিকেল চারটে বাজে। কী যে এক অস্বস্তিতে সময় কাটছে, তা ঠিক আমিও বুঝতে পারছি না। এমন সময় খবর এল, পাড়ায় কার বাড়িতে একজনের ছেলে হয়েছে, তাই কালা ও শাওয়ালি সেখানেই রাতে খাওয়া-দাওয়া করবে, নাচ গান করবে। খবরটা পাওয়ার পর থেকেই আমার অবচেতন মন ভীষণ ভাবে যেন নৃত্য শুরু করল।
পাব, আমি আবার মুক্তি পাব। ঘড়ির কাটার টিক টিক শব্দ, আবার শুনতে পাব। এখানে মুষ্টিমেয় জনগণ আছে, তবে জনস্রোত নেই। নিষ্প্রাণ পাথরের পাহাড়ের নির্জনতা আছে, কিন্তু সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া নেই। আজ আমি আবার জনস্রোতে মিশে যাবো। উত্তাল তরঙ্গে ভেসে যাব। এখানে দিন আছে, দিনের উজ্জ্বলতা নেই। রাত আছে রাতের গভীরতা নেই। চাই আমি অনেক অনেক উজ্জ্বলতা। আরো, আরো গভীরতা দিয়ে আমার জীবনকে পরিপূর্ণ করতে।
ত্রয়োদশ অধ্যায়
রাত দশটা। আমি তৈরি। আমার সব টাকা মুশা নিয়ে নিয়েছিল। মাত্র তিন লাখ আফগানি আমার কাছে ছিল। আমি আমার বড় একটা হাত ব্যাগে টাকাটা নিলাম। একটা শালোয়ার কামিজ নিলাম। যেটা পরে আছি সেটা তো ওই ফোকর দিয়ে বেরোবার সময় কাদা মেখে যাবে। তাই সেটা ফেলে দিতে হবে। আর নিলাম বি.পি মেশিন ও স্টেথিস্কোপ ও একটা পেন। আর আমার ইন্ডিয়ার সব কাগজ, সার্টিফিকেট গুছিয়ে নিলাম। এখানে একমাত্র মহিলা ডাক্তাররা রুগী দেখার প্রয়োজনে একা যাতায়াত করতে পারে। সবই ওই হাতুড়ে ডাক্তার অর্থাৎ দাই। এবার গুলগুটিকে পাঠালাম, মুশার বিবি ও সাদগি শুয়ে পড়েছে কিনা দেখার জন্য। গুলগুটি দেখে এসে বলল, সুলতান বিবি শুয়ে পড়েছে। কিন্তু সাদগি জেগে আছে। মেয়েবে ঘুম পাড়াচ্ছে।
আমি ওকে বললাম, তুমি গিয়ে সাদগির সঙ্গে বসে গল্প করো। আমি এই ফাঁকে পালাবো। রাতে একবার সবাই শুয়ে পড়লে, কেউ কারো ঘরে যায় না বা আসে না। তবুও গুলগুটি আমার কথামতো সাদগির ঘরে গেল। আমি বেরিয়ে প্রথমে নিচে বাথরুম যাওয়ার নামে গিয়ে ওই ফোঁকর, যেখান থেকে বেরিয়ে আলোর সন্ধানে যাবো সেখানে আমার ব্যাগটা রেখে এলাম। বারান্দায় উঠে একবার সাদগির ঘরে ঢুকলাম। যাতে সাদগি নিশ্চিন্তে শুয়ে গুটির সঙ্গে গল্প করে। গুলগুটিকে সংক্ষেপে গুটি বলি। বললাম, কিরে? তোরা এখনো বসে গল্প করছিস? শুবি কখন?
-এই শোব। সারাদিন তো কাজে ব্যস্ত থাকি। তাই এখন একটু কথা বলছি।
-গুলগুটি, আমি শুয়ে পড়ছি। যখন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করবি তখন আস্তে বন্ধ করিস। আমার যাতে ঘুম না ভাঙে।
আমি অন্ধকারে গুলগুটির সঙ্গে হাত মেলালাম। এবার ঘরে এসে পাশ বালিশ রেখে আর একটা অন্য বালিশ রেখে লেপ চাপা দিলাম। রাতে এখানে সবসময় লেপ গায়ে দিতে হয়। এবার বারান্দার নিচে নামলাম। সিঁড়ি দিয়ে নয়। আমার ঘরের সামনে বারান্দার কার্নিশ ধরে। বারান্দার শেষ প্রান্তে আমার ঘর। তারপর দেওয়াল। আমার ঘরের আগে কালার ঘর। তার আগে শাওয়ালির। তারও আগে মুশার ঘর। মানে, মেইন দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথমেই সামনে পড়বে মেহমান ঘর। সেটা প্রদক্ষিণ করে এসে, সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে সামনেই পড়বে মুশার ঘর। আর ও প্রান্তের সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথমে পড়বে কালার, তারপর আমার। আর আমাদের ঘরের ঠিক সোজা দক্ষিণ দিকে অন্তত কুড়ি মিটার দূরে গেলে, বাঁ দিকে কোনায় আছে দালান। এখানে রান্নাঘরকে চেসখানা বা দালান বলে। আর দালানে ঢোকার দশ হাত আগে, দালানের ডানদিকে কোনা বরাবর আছে পাতকুয়া আর পাতকুয়ার ডান দিকে দশ হাত এগিয়ে গেলে আছে ফোকরটা। রান্নাঘর থেকে মাঝের ফারাক অন্তত পনেরো হাত। আমি বারান্দার নিচে বসে বসে, দেওয়াল ঘেঁষে যেতে লাগলাম। নইলে জানালা দিয়ে সাদগি আমাকে দেখতে পাবে। মেহমান ঘর পর্যন্ত, এই ভাবে গেলাম। তারপর মেহমান ঘর ক্রশ করে পশ্চিমের দিকে। মেহমান ঘরের সামনা সামনি পশ্চিমের দিকেই মেন দরজা। তাতে তালা দেওয়া।
এবার আমি পশ্চিমের দেওয়াল ঘেঁষে দক্ষিণে যেতে লাগলাম। অন্ধকারে যদিও কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবুও বিপদ এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। এতক্ষণে বহু আকাঙ্ক্ষিত ফোকরের সামনে পৌঁছালাম। আমি এবার দুহাত দিয়ে পাগলের মতো মাটি আঁচড়ে আঁচড়ে খুঁড়ে সরাতে লাগলাম। আমি যেন উন্মাদ। মাটি সরাচ্ছি তো সরাচ্ছি। ওপারের আলো আমার চাই–চাই। যেমন করে হোক, যে ভাবে হোক, দেওয়ালের ওপারে আমাকে যেতে হবেই। থামলে চলবে না। আরো আরো মাটি খুঁড়ছি। সমস্ত হাতে গায়ে কাঁটা ফুটে গিয়েছে। যাক। যত ইচ্ছা কাঁটা ফুটুক। হাত দুটো কেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাক। রক্তের স্রোত বয়ে যাক। সচল হৃৎপিণ্ডটা নিশ্বাস চেপে চেপে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। আর একটুখানি, আর হাফ মিটারের মতো খুঁড়তে পারলেই এ পারের মুক্তি। পুরো দেড় মিটার চওড়া দেওয়াল আর ফোকরটা। হঠাৎ বাতাস লাগল মুখে। পেরেছি, আমি পেরেছি নিজেকে অর্গল মুক্ত করতে। একটুখানি খুঁড়লেই বেরিয়ে যাবো। আমি লম্বায় পুরো উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে এগোচ্ছি।
আলো-আলো। কত আলো। অন্ধকার গুহার থেকে এবার আমি আলোয়। তাড়াতাড়ি শালোয়ার কামিজ ছেড়ে, পরিষ্কার শালোয়ার কামিজ পরে নিলাম। ছাড়া জামাতে মাথা, হাত, মুখ সব মুছে নিলাম। এবার ব্যাগটা নিয়ে সোজা পশ্চিমের রাস্তা ধরে পঞ্চাশ হাত দূরে গিয়ে উত্তরের রাস্তা ধরলাম। অন্ধকার রাস্তা। সামনের মানুষ দেখা যায় না। আমি চলেছি, আমার ভয় নেই আজ। গমের ক্ষেত একটার পর একটা পেরিয়ে চলেছি। সবাই, পৃথিবীর সবাই এই মুহূর্তে ঘরে নিশ্চিন্তের ঘুম ঘুমোচ্ছে। কোথায় এই চলা শেষ হবে, তাও জানি না। নির্জন রাতের ঘন কালো অন্ধকারে অশরীরিরাও বোধহয় একবার থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু আমার দাঁড়ালে চলবে না। দূরে কোথাও শেয়াল ডাকছে, পাল্লা দিয়ে কুকুরগুলোও ডেকে উঠছে। একমাত্র আকাশের তারাগুলো ছাড়া আজ আমার সাথী কেউ নেই। হঠাৎ সামনে দেখতে পেলাম যুদ্ধে বিধ্বস্ত একটা গ্রাম। একদা শালো বাজারে জাম্বাজের সঙ্গে যাওয়ার সময় এই বিধ্বস্ত গ্রামটা দেখিয়ে জাম্বাজ আমাকে বলেছিল-এই গ্রামের লোক সবাই একই দিনে বোমার আঘাতে মারা গেছে। এখনো এই গ্রামে সেই সব মানুষের আত্মা ঘুরে বেড়ায়। কথাটা মনে পড়তে বুকের ভিতরটা কেমন খালি হয়ে গেল। তারপর ভাবলাম ভয় কি? আত্মা কখনো কারো অনিষ্ট করে না। আর ভাবলাম, যদি এমন হয়? যেমন ভূতের রাজা বর দিয়েছিল গুপি ও বাঘাকে? তেমনি যদি আমাকেও দেয়? তবে এখুনি আমি একবার জাম্বাজদের বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়াব। তারপর চিৎকার করে বলব, কালা শাওয়ালি, সাদগি, সুলতানবিবি, দেখ আমি চলে যাচ্ছি। তোদর ক্ষমতা থাকে তো আমাকে ধর। তারপর যেই ধরতে আসবে, অমনি হুস করে উড়ে চলে যাবো।
কিন্তু ভাবনা আর বাস্তব এক নয়। একটা পেঁচা ওই ভাঙা বাড়ির কোনও ফোঁকর থেকে বেরিয়ে আমার সামনে দিয়ে অন্য জায়গায় উড়ে চলে গেলো। আমি ভয়ে মা বলে ডেকে উঠলাম। হাত পা যেন ঠক্ ঠক করে কাঁপতে লাগল। চলার আর শক্তি পাচ্ছি না। একটা শিরশির করা ভয়, মাথা থেকে পা অব্দি নেমে এলো। নিজের অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, বিশমিল্লা রহমানের রহিম। লা ইলাহা ইল্লেলা, মহম্মদিন রসুল আল্লা। এতেও ঠিক মন ভরলো না। ভাবলাম, ভূত যদি এতটুকুতে না থামে? তাই আবার জোরে জোরে বললাম,- আল্লা মসয়লি, আল্লা মহম্মদিন, ওলা আল্লা মহম্মদিন, কামা সোয়ালায়, আল্লা ইব্রাহিম, অলা আল্লা ইব্রাহিম, ইন্নাকামেদুমছি, আতিনা পিত দুনিয়া, আস্নাতম, পিল আখেরাতে আস্নাতম, ওয়াকিনা আজাবনার।
এই সুরাটা ঠিক কি ভুল তা আমি জানি না। তবে আমার শাশুড়ির কাছে শেখা। ভাষার তারতম্যের জন্য ভুলও হতে পারে। আমি এই সুরাটা বলতে বলতে এগিয়ে চললাম। কত ক্ষেত, খামার, ঘন জঙ্গল, গ্রাম পেরিয়ে এলাম জানি না। রাতের অন্ধকারে হঠাৎ একটা বাচ্চার কান্না ভেসে এলো। রাস্তার বাঁদিকে একটা বাড়ির থেকে এই কান্নার আওয়াজ আসছে। মুহূর্তের জন্যে আমি একটু দাঁড়ালাম। বোঝার চেষ্টা করলাম, এটা ভালো বাড়ি? নাকি পোড়ো? না, পোড়ো বাড়ি নয়। আবার চলতে আরম্ভ করলাম। যেতে যেতে বাঁ দিকে একটা কবরস্থান দেখতে পেলাম আবার সেই কলেমা বলতে লাগলাম। তবুও বার বার মনে হচ্ছে পিছনে যেন কেউ আছে। কিন্তু চলা থামে না। চলাই যেন শেষ কথা।
এবার একটা গ্রামের মধ্যে ঢুকলাম। এক সময় গ্রাম পেরিয়ে গেলাম। এবার দুধারে জঙ্গল পড়ল। তার মাঝখান থেকে সরু রাস্তা চলে গেছে। এই সরু রাস্তা ধরে আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। দূরে, অনেক দূরে একটা গ্রাম দেখতে পাচ্ছি। প্রায় আধঘণ্টা হাঁটার পর, গ্রামের ঠিক সামনে এলাম। এবার বাড়িগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ একটা কুকুর তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলো। আমি এবার বিপদে পড়লাম। এগিয়ে যেতে আর সাহস পাচ্ছি না। এখানকার কুকুর ভীষণ হিংস্র হয়। ডোভারম্যান বা অ্যালসেসিয়ানের মতো। আমার থেকে মাত্র সাত মিটার দূরে, কুকুরটা দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে বিশ্রীভাবে। সেও আমার দিকে এগিয়ে আসছে না। আমিও তার দিকে এগিয়ে যেতে পারছি না। আমি হতাশ হয়ে বসে পড়লাম, রাস্তার ঠিক মাঝ বরাবর। আমি উত্তর দিকে মুখ করে আছি। আর কুকুরটার দক্ষিণ দিকে মুখ। দুজনে দুজনকে ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আমার ডান দিকে বিশাল গমের ক্ষেত। বাঁদিকেও তাই। বাঁদিকে গমের খেত ছাড়িয়ে প্রায় তিরিশ গজ দূরে কে যেন একজন দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ গলাটা আবার ভারী হয়ে উঠল। আবার এমনও হতে পারে–কেউ গমের ক্ষেতে জল দিচ্ছে। আচ্ছা; লোকটাও কি আমাকে দেখতে পাচ্ছে? যদি কাছে আসে? জিজ্ঞাসা করে আমি কে? কোথা থেকে আসছি? কোথায় যাবো? একা মেয়ে দেখে যদি কিছু খারাপ করার চেষ্টা করে? আমি, মনে মনে তৈরি হয়ে নিলাম। তেমন কিছু অঘটন ঘটার সম্ভাবনা দেখলে, তখুনি চিৎকার করব। রাতের আওয়াজ অনেক দূরে যায়। চিৎকার শুনে সামনের বাড়ি থেকে নিশ্চয়ই কেউ বেরবে। কলেমা এ ক্ষেত্রে কাজে লাগবে কিনা কে জানে। এতদিন এখানে থাকতে থাকতে কলেমা আমার অবচেতন মনের মধ্যে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে তা আগে বুঝতে করতে পারিনি। আর পারতামও না যদি না এই নিশুতি, নিঝুম রাতে একা বাড়ির বাইরে পা রাখতাম। একটানা ঝিঁঝি পোকা ডেকে চলেছে। কিন্তু জোনাকির আলো নেই। শুধু অন্ধকার, নিকশ কালো ঘন অন্ধকার।
হঠাৎ আমার মনে হলো এই দেশের ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে আমার দেশের ঝিঁঝির ডাকের একটুও মিল নেই। থাকবেই বা কী করে? এখানকার ভাষা ও আমাদের ভাষা তো সম্পূর্ণ আলাদা। অন্ধকার ছুঁয়ে আস্তে আস্তে ভোরের স্বচ্ছতা প্রকাশ হতে লাগল। চারদিকে তখনো খানিকটা অন্ধকার। হঠাৎ দূরে কার পায়ের শব্দ। পিছন ফিরে দেখলাম, একটা লম্বা লোক এই দিকেই এগিয়ে আসছে। ত্বরিতে ঠিক করে ফেললাম। নিজেকে বাঁচাতে মিথ্যের পথেই এগুতে হবে। তাই দূর থেকেই আমি বললাম, মুসলমান? ইয়া কাফের? এখানে, যদি কেউ এই কথা বলে, তবে বুঝে নিতে হবে সে ভালো লোক। এবং সাহায্য চাইছে।
-মুসলমান? তা তুমি কে? একা একা এখানেই বা কী করছ?
-আমি গজনীতে যাবো। আসছি কাবুল থেকে। কাবুল থেকে গজনী যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। তাই আমি গড়দেশের রাস্তা ধরে এসেছি। এই সমস্ত কথা পুস্ততেই হচ্ছে।
-তা, এখানে পৌঁছালে কী করে? গড়দেশ থেকে সোজা রাস্তা পাতানা ধরে তো গাড়ি গজনীতে যাবে। এটা তো সম্পূর্ণ উল্টো রাস্তা। আমি তো জানি এটা উল্টো রাস্তা।
কিন্তু লোকটাকে বললাম–কী জানি, কী করে এলাম। জিপের মধ্যে কিছু লোক আমার সোনাদানা, টাকা সব ছিনিয়ে নিয়ে একটা জায়গায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। তারপর আমি হাঁটতে হাঁটতে এখানে এসে পৌঁছেছি। অন্ধকারে তো রাস্তা চেনা যায় না।
তা ছাড়া আমি এদিকের রাস্তা চিনি না। আমি ডাক্তার। গজনীর একটা হাসপাতালে যাবো। সেখানে একটা অপারেশান কেস আছে আমার। আপনি দয়া করে, আমাকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন। আমাকে এখুনি গজনীতে পৌঁছোতে হবে।
-আমার সঙ্গে এসো। একটা মৌলানাকে তোমার সঙ্গে পাঠাচ্ছি। সে তোমাকে গাড়ি ঠিক করে দেবে। আমি গম কাটতে যাচ্ছি। আমার ট্রাক্টর এখন গম নিয়ে বাড়ি যাবে নইলে আমিই তোমায় গজনী পৌঁছে দিতাম। আমি লোকটার পিছন পিছন যেতে লাগলাম। অনতিদূরে একটা বাজার চোখে পড়ল। একটু পরে আমরা বাজারের কাছে চলে এলাম। কিন্তু এ কি? এ আমি কী দেখছি?
কী সর্বনাশ? অন্তত কুড়িটা বিশাল আকারের কুকুর আমাদের দিকে ধাওয়া করে এল। সঙ্গের লোকটা একটা রুটি টুকরো করে ওদের দিল। এ ওর পিঠের ওপর দিয়ে গিয়ে ওরা রুটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পরলো। আমি ভয় পাচ্ছি দেখে, লোকটা বলল, ভয় নেই। রুটি পেয়ে ওরা বুঝেছে, এরা আমাদের শত্রু নয়। নইলে এতক্ষণ ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত। কলেমা। ওই কলেমাই আজ আমাকে রক্ষা করেছে? ওই কুকুরটা ওইখানে আমাকে যদি না থামাতো? এখানে নির্ঘাত মৃত্যু। যা মেসিনগানের গুলির চাইতেও ভয়ঙ্কর। গ্রামের ওই কুকুরটা নিশ্চই ভগবানের প্রেরিত দূত।
বিকেল পাঁচটা বাজে। আজ গজনীতে আমার যাওয়া হয়নি। মৌলানা, একটা বাড়িতে জিপের খোঁজ করতে এসে, জানতে পারল যে আজ এখান থেকে, কোনও গাড়ি গজনী যাবে না। কাল যাবে। গাড়ির মালিক মৌলানার জানাশোনা। তাই আমাকে এখানেই থেকে যেতে বলল আজকের রাতটা। কাল ভোরে গাড়ি ছাড়বে। আমিও চিন্তা করলাম দেওররা যদি খোঁজে তবে আজকেই খুঁজবে। অতএব আজকের রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল গেলে আর কোনও চিন্তা থাকবে না। নিশ্চিন্তে যাওয়া যাবে। এদের বাড়িতে আমাকে খুব যত্ন করেছে। মেহমান বলে কথা। মুরগি কেটে আমার জন্যে কোরমা টাইপের রান্না করেছে। একে সারা রাত পথ চলেছি, তারপর দেওরদের, তালিবানদের আতঙ্ক, আবার ভূতের ভয়। বাঘ, কুকুর, শেয়ালের জন্যে ত্রাস। সব মিলিয়ে আমি একেবারে বিধ্বস্ত। দুপুরে স্নান করার পর, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু ঘুমোতে পারিনি। ইতিমধ্যে এই পাড়ায় সবাই জেনে গিয়েছিল যে, এই বাড়িতে কাবুলের এক ডাক্তার এসেছে। সারাদিন পিলপিল করে লোক এসেছে। মহিলারা কিছু না হলেও ডাক্তার যখন এসেছে বাড়ি বয়ে, তখন দেখিয়ে নিতে দোষ কি? রাতের খাবার খাওয়ার পর, বাড়ির মালিকটি ঘোষণা করল, ভোরে আপনার যাওয়া হবে না। কারণ পাশের বাড়ির লোক তালিবানকে খবর দিয়েছে, এখানে একা একজন মহিলা এসেছে। তালিবানরা বলেছে, মহিলাকে ধরে রাখতে। কাল দশটার সময় এখানে এসে আপনার সঙ্গে কথা বলবে। এই মুহূর্তে বজ্রপাতের মতো আকাশটা আমার মাথায় ভেঙে পড়লেও, আমি একটুও আঘাত পেতাম না। বা দুঃখিত হতাম না। এখন আমি কী করব? এবারেও আমাকে ফিরে যেতে হবে? তবে কি সত্যিই আমার মুক্তি নেই? আমি হতাশায় ভেঙে পড়লাম। কিন্তু না ভেঙে পড়লে চলবে না। এখানে শয়তানি বুদ্ধি দ্বারা জয়লাভ করতে হবে। হেরে গেলে তো সব শেষ হয়ে যাবে। জিত, জিত চাই আমার। ছলে বলে কৌশলে জিততে আমাকে হবেই। আমি মালিকটাকে বললাম,–শুনুন। সকালেই আমি এখান থেকে চলে যেতে চেয়েছিলাম, অন্য গাড়ির খোঁজে। আপনিই আমাকে যেতে দেননি। সুতরাং কাল ভোরে, অন্ধকার থাকতে থাকতে আমাকে এখান থেকে পাঠিয়ে দেবেন গজনীতে। নতুবা আমি তালিবানকে বলব, আপনিই আমাকে জোর করে এখানে রেখেছেন। এবং আমার ওপর শারীরিক অত্যাচার করেছেন। এই কথা শোনার পর, তালিবান আপনাকে কী করবে, বুঝতেই পারছেন? মালিকটা একটু কি যেন ভাবলো, তারপর বলল,-বেশ। আমি কাল ভোরে আপনাকে আমার ভাইয়ের মটর সাইকেলে করে গজনীতে ছেড়ে আসতে বলব। আপনি একটা কাজ করবেন। গজনীতে এখন মাদালি আছে। তার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে, আমার ভাইয়ের হাতে দেবেন যে আপনি গজনী পৌঁছে গেছেন। আমি সেটা তালিবানের কাছে দিলে আমার ছুটি। ওরা আর আমাকে কিছু বলতে পারবে না।
চতুর্দশ অধ্যায়
বেলা দশটা। আমি গজনী চৌকির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। চৌকি মানে থানা। মাদালির চিঠি পেয়ে গিয়েছি। এবার আমি কাবুলের বাসে উঠব। গজনী বাজার থেকে একটা বড় ব্যাগ কেনার জন্যে ব্যাগের দোকান দেখতে পেয়ে সেই দোকানে গেলাম। একটা ব্যাগ কিনলাম। তারপর কাবুলের বাসের গুমটির কাছে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ বাসটা যাবে কাবুলে? হঠাৎ একটা লম্বা লোক এসে আমাকে বলল–আপনি জাম্বাজের বিবি না? দাঁড়ান গাড়িতে উঠবেন না। আসুন আমার সঙ্গে, এবারেও আমাকে ফিরে আসতে হল। তবে বাড়িতে নয় রফিক খুরিয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। আমাকে এই ভাবে দেখে ওদের বাড়ির কারো আর বুঝতে বাকি রইলো না। এর আগে আমি পাকিস্তানে চলে গিয়েছি, তাও এরা জানে। বাড়ির সবাই আমাকে বসিয়ে আমার মাথায় হাত বোলাতে লাগল। ওনার চার ছেলের চার বৌ আমার জন্যে খাবার আনতে গেল। রফিকের বিবির স্নেহের স্পর্শ পেয়ে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। বিবি সাহেবার কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। আমার কান্না দেখে উপস্থিত সবাই কাঁদছে। আমাকে ধরে ফেলার অপরাধে পাকড়াওকারীকে অভিশাপ দিতে লাগল। বিবিজি যত অভিশাপই দিক না কেন ওতে কারো কিছুই হবে না। সিদিকের বৌ আমেদা। সিদিক, রফিক খুরিয়ের বড় ছেলে। আমেদা ফার্সিবান। বৌটাকে আমার খুব ভালো লাগে।
আমি দোতলায় আমেদার ঘরে বসে আছি। এই রফিক খুরিয়ের বাড়িটা খুব সুন্দর। গতানুগতিক আফগানিস্তানের মতো নয়। মাটিরই বাড়ি। তবে দোতলা। আমি দোতলায় ঘরে বসে আছি। নিচে মেহমান ঘরে আমার শ্বশুরবাড়ির লোক মুরুব্বিরা বসে আমার বিচার করছে। আমাকে কী করবে তাই ভাবছে। গুলি করে মেরে দেবে? নাকি হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেবে? দুচারজন তালিবানও এসেছে। এদের মধ্যে একজনকেই আমি বিশ্বাস করতে পারি। তিনি হলেন দ্রানাইচাচা। আমার পালাবার ব্যাপারটা সবটা না হলেও কিছুটা তিনি জানতেন। সেরিনা চাচি বলেছিল ডরিজো–মা ভয় পেয়ো না। জে, চাচাতা উইয়াম-আমি চাচাকে বলব। চাচা-ইসসি না আই চাচা কিছুই বলবে না।
সেই দ্রানাই চাচাও এসেছে। তালিবানরা বলছে এমন জঘন্য চরিত্রের মহিলাকে মেরে ফেলে দেবো। কিছুতেই একে ছাড়বো না। আমি মেহমান ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিলাম। তালিবানের কথাটা শুনে আমার মাথার পোকাটা আবার নড়েচড়ে উঠলো। একটা জঘন্য শরিয়তির হিংসাত্মক মনোবৃত্তির মানুষ আমাকে জঘন্য চরিত্রের বলছে? আর আমি? সরোজিনী নাইডু, রানি লক্ষ্মীবাঈ, দেবী চৌধুরানির, ইন্দিরা গান্ধীর দেশের মেয়ে হয়েও কতকগুলো নোংরা মানুষের নোংরা মন্তব্য মুখ বুজে হজম করছি? আমি মুহূর্তে আমার কর্তব্য ঠিক করে নিলাম। মরব, আমি মরব। তবে এদের হাতে নয়। আর মরার আগে এই তালিবানদের জিজ্ঞাসা করব আমার চরিত্রের কী জঘন্যতার প্রমাণ পেয়েছে তারা? এর উত্তর আমার চাই। আমি সোজা ওপরে উঠে গেলাম। ঘরে কেউ নেই। সবাই নিচে। ঘরের দেওয়ালে কালাউনশীকোপ ঝোলানো আছে। আমি জাম্বাজের কাছে চালানো শিখেছি। কালাখানের বিয়ের সময় অনেক গুলি ছুঁড়েছি আকাশের দিকে। মেসিনটা হাতে নিয়ে যেখানে গুলি লোড করা হয় সেইটা খুলে দেখলাম গুলি লোড করা আছে কিনা। দেখলাম লোড। মেসিনটা নিয়ে আমি এবার নিচে নেমে এলাম। কপালের পাশের রগ দুটো যন্ত্রণায় ফুলে উঠেছে। আমি নিজেই বুঝতে পারছি আমার সমস্ত মুখে একটা আক্রোশ, ঘৃণা ও প্রতিহিংসায় প্রকট হয়ে উঠেছে। রাগে, অপমানে, দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি সোজা মেহমান ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আমার মাথার দোপাট্টাও তখন খসে পড়েছে।
আমাকে এই ভাবে দেখে ঘরের উপস্থিত সবাই এক সঙ্গে আমার দিকে নজর দিল। আমি মেসিন উঁচিয়ে তালিবানদের দিকে ধরলাম। জনা পাঁচেক তালিবান এসেছে। ওরা কেমন যেন বোকা, বোবা দৃষ্টি নিয়ে অস্ফুট স্বরে অন্যদের বলল–
–দা সি আই। ও কী বলছে?
-কী বলছি বুঝতে পারছে না, না? তোমরা কী মনে করেছে কী? যখন তখন সবার নামে একটা করে মিথ্যে কলঙ্ক দিয়ে তাদের হত্যা করবে? সে সুযোগ আমি তোমাদের দেব না। আমি তোমাদের হাতে মরব না। আগে তোমাদের মারব, তারপর নিজেই নিজেকে গুলি করব। আমার কথায় সবাই বুঝল আমি নিছক কথার কথা বলছি না। দ্রানাই চাচা আমাকে বলল,-সাহেবকামাল, তুমি শান্ত হও। আমি তো আছি? তোমার কোনও চিন্তা নেই।
কথাটা ঠিকই। দ্রানাই চাচাকে সবাই খুব মানে, শ্রদ্ধা করে। দ্রানাই চাচার কথা কেউ অমান্য করে না। তবুও আমি থামলাম না, বললাম –থামবো? চাচা কী বলছেন আপনি? আমি সব শুনেছি এই তালিবানগুলো কী বলেছে। আমি জঘন্য চরিত্রের, তাই না? বলল। এই তালিব, বলল আমার চরিত্রের মধ্যে কী জঘন্যতা দেখেছে তুমি?
তখন একজন তালিবান উঠে দাঁড়ালো। মুখটা দেখলেই বোঝা যায় যে হিংস্র জানোয়ার। চিবুকটা তার গলার কষ্ঠির সঙ্গে লাগানো, মাথাটা ঈশৎ ডানদিকে হেলাননা। চোখ দুটো ওপরের দিকে তোলা, কপালটা কুঁচকে মাঝখানে এসে মাংসটা দলা পাকিয়ে গেছে। আমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। দুটো হাত কোমরে রাখা। যেন এখুনি আমাকে খতম করে দেবে এমন ভাব। ওর ওই দৃষ্টি দেখে যে কোনও মানুষ মূৰ্ছা যেতে পারে। কিন্তু আজ আর আমার কোনরকম ভয়, ভাবনা হচ্ছে। আমি আজ ডিটারমাইন্ড মেরে মরব। হারবো না। কোনও অপমান সহ্য করব। আফগানিস্তানের বুকে নজির রেখে যাবো। ইতিহাসের পাতায় যতদিন তালিবান বেঁচে থাকবে ততদিন আমিও থাকব।
-এই মেয়ে। তোমার সাহস তো মন্দ নয়? তুমি আমাদের কাছে জবাব চাইছো? তুমি দুবার পালিয়েছে বাড়ি থেকে। চরিত্র খারাপ না হলে তুমি পালিয়েছো কেন?
বেশ করেছি পালিয়েছি। প্রয়োজনে দুবার নয়, দশবার পালাবো। আর সাহসের কথা বলছ? আজ আমি তোমাকে দেখার সাহস কাকে বলে। তোমরা কী জানো? আমাকে বাড়িতে কী অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয় আমার দেওরদের কাছে? তুমি চোখ নামিয়ে কথা বলো। আমি তোমাদের দয়ায় বেঁচে নেই। আমি হিন্দুস্থানি মেয়ে। অহেতুক কারো চোখ রাঙানি সহ্য করার ধৈর্য আমার নেই।
অন্য একজন তালিবান, হিংস্র লোকটাকে জামা ধরে টেনে বসিয়ে দিল। যারাই এখানে বসে আছে সবাই নিরস্ত্র। আমি দেওয়ালে পিঠ করে ওদের দিকে মেসিন উঁচিয়ে এমন ভাবে দাঁড়িয়েছি যে; কেউ আমার দিকে এলেই ফায়ার করব। মেসিনের একটা পয়েন্ট মাঝখানে আছে, সেটা নিচে নামিয়ে উপরে তুলে নিলাম। এবার ট্রিগারে হাত দিলেই পর পর ষাটখানা গুলি চলবে। সুতরাং ভয়ে কেউ আর উঠছে না। যে যার জায়গায় বসে আছে। এবার দ্রানাইচাচা বলল-তুমি শান্ত হয়ে বল কী চাও? আমরা তাই করব।
-এই তালিবান, তোমরা ভালো করে মন দিয়ে শোনো। আমি যখন পাকিস্তানে গিয়েছিলাম, তখন আমি আমার দেশের হুকুমতের কাছে খবর পাঠিয়েছি যে এখানে আমাকে বন্দী করে রেখে, আমার প্রতি অত্যাচার করছে। যদি আমার কিছু হয় তবে জেনে রাখো হিন্দুস্থানে যত খান আছে সবাই মরবে। তাই বলছি আমাকে এখুনি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা। নতুবা এই খানেদের হত্যার জন্যে দায়ী তোমরা হবে।
সিদক ভাই তখন তালিবানদের বলল,
-এটা ঠিক। একটা মেয়ের জন্যে কেন এতগুলো লোকের প্রাণ যাবে? একে এর দেশে পঠিয়ে দাও। আমাকে যাতে যেতে দেয় তাই কথাগুলো বলল।
-কিন্তু মেয়ের এত সাহস আমাদের ওপর মেসিন উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে? এর প্রতিকার না করে ওকে আমরা ছাড়বো না। অন্তত পঁচিশটা চাবুকের বাড়ি ওকে আমরা মারবো।
আমার পা থেকে রক্ত চড়াত করে মাথায় উঠে গেল। আমার আর ইচ্ছা করল না ওদের তুমি বা আপনি বলতে। তাই তুই বলে সম্বোধন করলাম।
–এই, আমি কি তোদের বাপের সম্পত্তি? যে আমাকে তোরা চাবুক মারবি? আয়-আয় আমার কাছে, কে আমাকে চাবুক মারিব? পাকিস্তানের দুটো উর্দু অক্ষর উচ্চারণ করেছিস বলে নিজেকে কী মনে করেছিস? আগে নিজের ঘরে গিয়ে মা বোনদের সামলা তারপর আমাকে চাবুক মারতে আসবি, এতদিন কোথায় ছিলি? যখন তোদের দেশের একটা ছেলে মিথ্যে বলে বেড়াতে আসার নাম করে এসে আমাকে এই নোংরা, নেটিভ দেশে বন্দী করে রেখেছে আজ আট বছর? কেন সেই বাড়ির বিচার করিসনি? আমি তো মুশাফির, কোন মানবিকতায় আছে একটা অন্য দেশের নাগরিককে এই ভাবে বন্দী করে রাখে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে? এখন আমার এত সাহস কেন তার বিচার করতে এসেছিস? তোরা কে আমার কাজের বিচার করার? আর আমাকে দুশ্চরিত্র বলছিস। তোদের দেশের মেয়েরা শুধু চুল কেটে দেওয়ার, চুলচেরা বিচার নিয়ে তোরা ব্যস্ত। মেয়েদের বোরখা পরা নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু তখন কোথায় ছিলি? ১৯৯৩ ই সালের আগস্ট মাসে? যখন একটা সদ্যজাত শিশুকে কেউ এসে একটা নর্দমায় ফেলে দিয়ে গিয়েছিলো? তারপর অন্য কেউ নেইনি দেখে এক অদক জাত তাকে নিয়ে গিয়েছিল? এই তোদের সতী নারীর সতী দেশ?
আমার কথা শেষ হওয়ার পর একজন মুরুব্বি গোছের তালিবান কী যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তখন বাইরে থেকে বিবিজি ও তার চার ছেলের বৌ বলে উঠল– সত্যিই তো! এ তো অন্যায়। সাহেব কামালের সাহস আছে তাই প্রতিবাদ করতে পারলো। তা না হলে এই তালিবানরা আজ হয়ত ওকে গুলি করে মেরেই দিত। দেশের সব মেয়ে যদি এই ভাবে প্রতিবাদ করতে শিখি তবে কার সাধ্য যে আমাদের ওপর অত্যাচার করে?
কী জানি, তালিবানদের কী হলো। বলল, –বেশ তুমি হিন্দুস্থানে চলে যাও। কিন্তু তুমি একা তো যেতে পারবে না।
-কেন যেতে পারবো না? আমরা পরাধীন নই, স্বাধীন। পরনির্ভরশীল নই। আমি একাই যেতে পারবো। মনে মনে ভাবলাম, ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি। দ্রানাই চাচা এবার আমাকে বলল-কী? খুশি তো? এবার বন্দুক রেখে বোসো।
আমি পাশে বন্দুকটা রেখে বসলাম। তবুও মনে শান্তি নেই। যদি এটা ওদের চাল হয়? আমাকে নিরস্ত্র করে তারপর আমার ওপর যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে? গফর চাচার ভাই সাঁতার চাচা বলল,-সাহেবকামাল, তোমার কাছে টাকা আছে হিন্দুস্থান যাওয়ার?
-না। মাত্র এক লাখ আফগানি আছে।
-তবে যাবে কী করে? যদি মুশা টাকা না দেয়?
-দরকার নেই মুশার টাকার। আমার গায়ের গহনা বেচে আমি যাবো।
দ্রানাই চাচা বলল, গহনা বেচতে হবে না। আমি কাল ভোরে এসে টাকা দিয়ে যাবো। আজকের রাতটা তুমি এখানে থাকো।
-তাই হবে। আমি কলকাতায় গিয়ে তোমার টাকা পাঠিয়ে দেব।
এরপর সবাই চা-খাবার খেয়ে চলে গেল। ওরা যখন গাড়িতে উঠতে যাবে তখন হঠাৎ আমার মনে হল, যদি রাতে অনেক তালিবান এসে আমার সামনে দাঁড়ায়? তখন আমি কী করব? তালিবানদের মোটেও বিশ্বাস নেই। তার থেকে এখুনি এখান থেকে চলে যাওয়া ভালো। সকাল দশটা বাজে। চাচারা খুব ভোরেই এসেছিল। লপু চাচার ছেলে আব্দুলাক বলেছে ওরা রাতেই এখানে আসতে চেয়েছিল। আম্মাজান গাড়ি নিয়ে শ্বশুর বাড়ি গিয়েছিল বলে আসতে পারেনি। ভোর চারটেয় রওনা দিয়েছে। সকাল সাতটায় এখানে পৌঁছেছে। তারপর তিন ঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে চলে গেল বুঝতেই পারলাম না। আমি দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দ্রানাই চাচাকে ডাকলাম। দ্রানাই চাচা কাছে এলেন। আমি খুব আস্তে আস্তে বললাম চাচা, আমার মন বলছে, তালিবানরা রাতে হামলা করবে। দেখলেন না? একটা তালিবান রাতে থাকার সিদ্ধান্তে কেমন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে সায় দিল?
-সত্যি বলেছো তো? এই দিকটা আমি ভাবিনি? তবে তুমি এখুনি চলে যাও। টাকার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। গাড়ির ব্যবস্থাও করছি।
দ্রানাই চাচা সিদিক ভাইকে ডাকল। সন্দেহের কথাও বলল। শুনে সিদিক ভাইও বলল- হ্যাঁ, হতে পারে। তখন চাচা সিদিকের কাছ থেকে আট লাখ আফগানি চাইল। বলল কাল এসে দিয়ে যাবে।
তালিবানরা বলল, কী দরকার? কালই যাবে।
দ্রানাইচাচা স্পষ্ট বলল,-না, এখুনি যাবে। সিদিককে বলল,-দেখ একটা গাড়ি পাওয়া যায় কিনা কাবুল পর্যন্ত।
সিদিক বলল,-আমার শালাই তো আছে। বারিতখান –বারিত নিয়ে গেলে আমরাও নিশ্চিন্ত হতে পারবো। কাবুলে ম্যাক্রন টুতে এক হাজি সাহেব আছে, পাসপোর্ট বানানোর কাজ করে। বিবিও আছে। বারিত বরং একেবারে হাজির বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে।
-বাঃ। এ তো চমৎকার। ডাকো তোমার শালাকে।
সবাই আবার ঘরে এসে বসল। তালিবানরা বলল-আমরা আর বসে কী করব? চলে যাই। দ্রানাই চাচা বলল,-বোসোবোসো। এক সঙ্গে যাবো।
বুঝতে পারলাম কথাটা চাচা কেন বলল। ভাবলো যদি ওরা রাস্তায় গিয়ে ওঁত পেতে থাকে? আমাদের গাড়ি দেখলে ধরে?
সিদিক তার শালাকে নিয়ে এসেছে। মটর সাইকেলে করে গিয়েছিল সিদিক। তাই তাড়াতাড়ি যেতে পেরেছিল। একটা টাটা-সুমো গাড়ির মত গাড়ি এসে বাড়ির দরজায় দাঁড়াল। চাচা গুনে গুনে আটখানা হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল দিলেন। বললেন-একটা বান্ডিলে এক লাখ আছে। খুব ভেবে-চিন্তে খরচা করবে। রাস্তায় দরকার হলে টাকা দেওয়ার মতো কিন্তু কেউ নেই। গিয়ে আমাকে ক্যাসেট করে পাঠাবে।
আর শোন। জাম্বাজ পরের প্ররোচনায় তোমার সঙ্গে ঠিক ব্যবহার করতে পারেনি। ওর ওপর অবিচার করো না। আমার হাতে হাত রেখে কথা দাও জাম্বাজকে কোনও কষ্ট দেবে না? যদি কখনো ওকে কষ্ট দেওয়ার কথা মনে আসে তখন আজকের দিনটার কথা চিন্তা করো। তোমার প্রতি আমার স্নেহের দান হিসাবে জাম্বাজকে ক্ষমা করো।
মুক্তি পেয়েছি। আজ সত্যিকারের বিদায় নিয়েছি সবার কাছ থেকে। যখন সবাই খোদাপামানি দিল তখন আমার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছিলো। এখানে বিদায় সম্ভাষণকে খোদাপামানি বলে। বিবিজি একটা প্লাস্টিক প্যাকেটে করে খানিকটা মেওয়া দিয়েছে। বাড়ির সবাই যখন আমাকে গাড়িতে তুলে দিল তখন কেঁদে কেঁদে বলেছে- সাবেহ কামাল। মুগ, মা ইরিয়েজা। ফিতা রাওয়াবিলেগা। মানে, আমাদের ভুলো না। ক্যাসেট পাঠিয়ে দিও। তু মুগ ডের আকপাল। অর্থাৎ তুমি আমাদের খুব আপন।
আমি ওদের আশ্বস্ত করলাম। ঠিক এমনি করে আজ থেকে আট বছর আগে আমাকে বিদায় দিয়েছিল আমার বাড়ির লোক। সেদিন সকাল থেকেই একটা উত্তেজনা ছিল আমার মধ্যে। সবাই বারণ করা সত্ত্বেও আমি যাচ্ছি। আমার হঠাৎ এমন একটা বিয়ে করা, বাবা ঠিক মেনে নিতে পারেনি। প্রথম দিকে বাবা ভীষণ মারধোর করেছে। বাবার কাছে অত্যাধিক পরিমাণে মার খাওয়ার পর আরো জেদ চাপে। বাবা আমার চুলের মুঠি ধরলো। একটা বত্রিশ বছরের মেয়েকে বকা যায়। শাসন করা যায় কিন্তু মারা যায় কী? বাইরের সবাই একটা কুনজরে দেখতে লাগল আমাকে। তবুও জাম্বাজকেই বিয়ে করেছি। বিয়ের পর থেকে বাবা আমার সঙ্গে বেশি কথা বলতো না। যতটা পারতেন নিজেকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখতেন। ভাইরা আমার উপর কথা বলতে সাহস পায় না। সেদিন সকালে আমি ঘুম থেকে উঠে ভি.আই.পি গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। মা বড় বড় ট্যাংরা মাছের সঙ্গে বড়ি ও আলু দিয়ে ঝোল রান্না করেছে। একটার সময় দ্রানাই চাচা আমাকে নিতে আসবে। সেই সময় দ্রানাই চাচা কলকাতাতেই ছিল। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিলাম। অভিষেক আমার সঙ্গে দিল্লি পর্যন্ত যাবে। আমি জামা কাপড় পরে বাবাকে প্রণাম করতে গেলাম, তখন বাবা মাথা নিচু করে পা ঝুলিয়ে খাটের ওপর বসে আছে। বাবাকে প্রণাম করে আমি মাকেও প্রণাম করলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম। হাওড়া স্টেশনে অনেকে এসেছিল। সেদিন আমাকে বিদায় দেওয়ার সময় সবাই চোখের জলে বুক ভাসিয়েছিল। আর রুমা। রুমাও কেঁদেছে। রুমা যদি আমাকে জাম্বাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে না দিত; তবে কি আজ বিদেশে পড়ে থাকতে হতো?
আমার সমস্ত সর্বনাশের মূলে ওই রুমা। অনেক ইনিয়ে বিনিয়ে নিজেকে আমার সামনে জাহির করেছিল। ওর নীল। ওর ভালবাসা দীপঙ্কর। সেই ভালবাসাকেও ধরে রাখতে পারেনি। নীলও ওর জীবন থেকে বিদায় নিয়েছিল। দীপঙ্করকে নিজে ছেড়ে ছিল। তারপর রুমার বন্ধু হয় রহিম খান। এই সময়ে রুমার সঙ্গে আমার প্রায় রোজই দেখা হতো। একদিন রুমা আমাকে নেমন্তন্ন করল। গ্রান্ড হোটেলের রেস্টুরেন্টে একটা ফোর সিটের টেবিলে আমরা বসেছি। রুমা ওইদিনই পরিচয় করালো জাম্বাজের সঙ্গে। তারপর আলাপ। কিছুদিন পরে ভালবাসা। আরও পরে আজ এই সংশয়, অনিশ্চয়তা। রুমার কথা আজ থাক।
গাড়ি সেই প্রথম দিনের আসার রাস্তা দিয়েই যাচ্ছে। সেদিন ছিল সব কিছু আজানা, দুর্বোধ্য কিন্তু আজ! সব জানা, চেনা। এখানকার প্রতিটি পাথরের কুচি আমার চেনা। আমি চলে যাচ্ছি। চিরদিনের জন্যে এদেশ থেকে বিদায় নিচ্ছি। কোনদিন হয়ত এ দেশের মাটিতে আর পা রাখবো না। কিন্তু তিন্নি।? সে আজ আমার সঙ্গে নেই। তিন্নিকে কালাখান কেড়ে নিয়েছে। পাকিস্তান থেকে ফিরে আসার পর ওরা তিন্নিকে নিয়ে আসামের বাড়ি রেখে দিয়েছে। মাত্র চার বছরের মেয়ে, যে তখনো নিজের হাতে খেতে জানে না। কেমন করে বালিশে মাথা রেখে শুতে হয়; সেটাও তাকে মা দেখিয়ে দেয়। মায়ের বুকে হাত না রাখলে ঘুম আসে না। মা খাইয়ে দিলে তবেই খায়। মা, জামা পরিয়ে দিলে তবেই জামা পরে। এক দণ্ড মাকে না দেখলে তার ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না এসে যায়। মা যদি বাথরুমে স্নান করতে ঢোকে, সে দরজার কাছে বসে থাকে। আজ সেই মাকে দেখতে পাচ্ছে না। আমার কাছে তাকে কেউ আসতে দিচ্ছে না। উঃ! কী অসহ্য যন্ত্রণা। কী অপরিসীম কষ্ট। রাতে আমি তিন্নির বিছানায় হাত বোলাই। ভাবি হাত বাড়ালেই তিন্নিকে স্পর্শ করতে পারবো। যখন ওকে পাই না, তখন আমার চোখ দুটো দিয়ে জলের ধারা নামে। মাঝ রাতে উঠে বসি। ভাবি নিশ্চয়ই ওর কোনও কষ্ট হচ্ছে। ঠিক পেট ব্যথা করছে, হয়তো পটি করবে। কে ওকে বাইরে পটিতে নিয়ে যাবে? ও এখন আমার জন্যে কাঁদছে। গা থেকে চাদরটা হয়তো সরে গিয়েছে। সবাই তো ঘুমোচ্ছে। কে ওর গায়ে চাদর তুলে দেবে? এ দেশের মায়েরা সন্তানের প্রতি এত খেয়াল রাখে না। সময় কোথায়। কোলে আরেকটা। দ্বিতীয়টা হলে প্রথমটার কথা ভুলে যায়। প্রথমটা তখন আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালের মতো অবাঞ্ছিত। কিন্তু আমি তিন্নিকে সেভাবে মানুষ করিনি। কালাখানের ও সাদগির তো অনেক সন্তান। তিন্নিকে আমার বুক ফাঁকা করে কেড়ে না নিলেই কি চলছিল না? উদ্বিগ্ন নয়নে বারান্দায় বসে, সদর দরজার দিকে তাকিয়ে থাকি। যদি একবার অন্তত তিন্নিকে দেখতে পাই। আমার জন্যেই কি এত কষ্ট অপেক্ষা করেছিল? যদি কেড়েই নেবে তবে কেন দিয়েছিল? আমাকে ছাড়া তিন্নির জগৎ অন্ধকার। এই তো কাল গুলগুটি বলল। সারাক্ষণ তিন্নি কাঁদে। মার কাছে যাবো বলে। খেতে চায় না। শুধু বলে মা কোথায়? মা না এলে আমি খাবো না। কালাখান যেই বলেছে, তোর মা হিন্দুস্থানে চলে গেছে অমনি মেয়ে আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে, কালা ও সাদগির কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে অনুরোধ করলাম তিন্নিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে। দিল না। ওরা তিন্নিকে দিল না। নির্মমের মতো আমার অনুরোধ প্রত্যাখান করল।
দুপুর দুটো বাজে। হঠাৎ আমি শুনতে পেলাম, তিন্নি চিৎকার করে কাঁদছে। আর থাকতে পারলাম না। সমস্ত নিষেধ অমান্য করে দৌড়ে গেলাম। গলি দিয়ে দৌড়ে সোজা আসাম চাচার বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। তিন্নি বলে ডাক দিলাম। তিন্নি কোথায় ছিল জানি না। মা বলে দৌড়ে আসতে লাগল। আমিও এগিয়ে গেলাম। তিন্নি আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাস্তার মাঝেই মাটিতে বসে পড়লাম। তিন্নি আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল-মা, তুমি কোথায় গিয়েছিলে আমাকে ছেড়ে? আমি খাইনি, ঘুমাইনি, শুধু তোমার জন্যে কেঁদেছি। তুমি বলো আমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাবে না। আমি তিন্নির গালে চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিলাম। এতদিনের সুপ্ত আদর একদিনে পূর্ণ করে নিতে লাগলাম। হঠাৎ! বাজপাখির মতো সাদগি এসে তিন্নির হাত ধরে টানতে লাগলো। আমি পাথরের মূর্তির মত চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছি। তিন্নি চিৎকার করে বলতে লাগল-মা, আমাকে নিয়ে চলল। আমাকে ছেড়ে যেও না। আমাকে কেন সাদগি টেনে নিয়ে যাচ্ছে? আমি কি করেছি? আমি একচুলও নড়াচড়া করতে পারলাম না। স্তম্ভিত। নোংরা মনের নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ মানুষকে, আর কীই বা বলা যায়? এমনিতেই সাদগির কোনও লজ্জা, আত্মসম্মান, কৃতজ্ঞতা কিছুই নেই। সাদগি বহুবার জাম্বাজকেই অপমান করেছে। জাম্বাজ যা বারণ করেছে, সাদগি সেটাই করেছে। বাপের বাড়িতেও ওর কোনও কদর নেই। ছমাসে নমাসেও কেউ ওর খবর নিতে আসে না। বৌদিগুলো ভেবেছে আপদ বিদায় হয়েছে, আমরা বেঁচেছি। ভাগ্যও তেমনি। এক অকর্মন্য, অপদার্থ, পাগল স্বামী তার। কালাখানকে আগে সবাই পাগল বলত। একটা আটত্রিশ বছর বয়সের ছেলে হিসেব জানে না। ঘড়ি দেখতে জানে না। হিন্দুস্থানের পাঁচটা রুটির গোলা একবারে মুখে দেয়। খাওয়া শোয়া আর সন্তান উৎপাদন ছাড়া আর কিছুই জানে না। বিবির ক্ষেত্র ছাড়া সব ক্ষেত্রেই সে পাগল।
একবার আমি কালাকে বলেছি-এই কালাখান, তুই পাতকুয়াতে গিয়ে ঠাণ্ডা জল খাস নাকি? আমি ওকে যে ঠাট্টা করছি তা ও বুঝতে পারলো না।
-হ্যাঁ খাই তো। কেন? খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই জবাব দিল।
-না মানে তোর সদ্য মেয়ে হয়েছে তো? তাই!
–তাই কী?
-তুই ঠাণ্ডা জল খেলে তোর মেয়ের শরীর খারাপ হবে।
-আমি ঠাণ্ডা জল খেলে মেয়ের শরীর খারাপ হবে নাকি?
-হবে না? তুই তো মেয়ের বাবা। দেখিস না সাদগি ঠাণ্ডা জল খায় না। সদ্য বাচ্চা হলে বাবা-মাকে এমন কিছু খেতে নেই যাতে মেয়ের শরীর খারাপ হয়।
-দেখেছো। গুলগুটিটা কি পাজি। ওর সামনে আমি সেগিই থেকে জল তুলে খাই। ও আমাকে বারণ করে না। ভাগ্যিস তুমি বলে দিলে। এখানে পাতকুয়াকে সেগিই বলে। আবার বিয়েকে সাগাই বলে এবং ওয়াদা বলে। স্ত্রীকে খাজা বলে আর স্বামীকে মেরো বলে। ছেলেকে জোয় ও মেয়েকে লোর বলে। মাটিকে খাবড়া বলে। গাছকে ওয়েনা বলে। প্রিয় এবং প্রিয়াকে সানাজ ও গ্রানা বলে। তো এই হচ্ছে সাদগির স্বামী। প্রতিপদে ওকে আমার স্বামীর কাছে হাত পাততে হবে। যার কাছে হাত পেতে দাঁড়াতে হবে তার বিবির সঙ্গে কী ব্যবহার করছে সে? তিন্নিকে সাদগি আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। সাদগির মতো মেয়ের কাছে অপমানিত হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। তখন আমার ঠামার বলা একটা কথা মনের কোণে ঘুরপাক খেতে লাগলো পরের সোনা দিয়ো না কানে। প্রাণটা যাবে হেচকা টানে। মেয়েটা হারিয়ে গেল। তিন্নিকে ছাড়াই আজ আমার নতুন পথের যাত্রা। শুরু হল। তিনি চিরদিনের জন্যে আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল। বেঁচে থেকেও ছবি হয়ে গেল। আজ তার ছবিটাই আমার আগত দিনের চলার পথের সাথী।
.
বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হবে হবে। কাবুলে ম্যাকরিয়ান টুতে আমরা এসেছি। এখানে কোয়ার্টারের মতো সারি সারি বাড়ি। সামনের ডান হাতে একটা ঘর ছেড়ে বাঁদিকের সিঁড়ি দিয়ে দোতলাতে একটা বন্ধ দরজাতে টোকা দিল। একটু পরে দরজা খুলে দিল এক মহিলা। শালাবাবুকে দেখে বলল-আরে ইসলাম? তুমি? এসো, এসো। তারপর আমাকে দেখিয়ে ফার্সিতে কী সব কথা বলল। শালাবাবুও ফার্সিতে কী যেন বলল। তখন বৌটি আমাকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। কোয়ার্টারটা ভালোই। বৌটা একটু মোটা, বেঁটে, শ্যামবর্ণ। মোটা নাক। বয়েজ কাট চুল একটা সালোয়ার কামিজ পরা। রাস্তায় আসতে আসতে শালাবাবু বৌটার কথা বলেছে। বৌটা জালালাবাদের মেয়ে। হাজিসাহেব বিয়ের আগে দুটো বিয়ে করেছিল। কিন্তু টেকেনি। এই হচ্ছে তালিবানের সতী নারীর সতী দেশ। এরাই নাকি বোরখা না পরলে তালিবানদের বদনাম হবে। আর যত দোষ তা আমাদের। আমরা চরিত্রহীনা। হাজির সঙ্গে বৌটার বিয়ে হয়নি। লিভ টুগেদারে আছে। বৌটার দুই স্বামীর কাছ থেকে তিনটে সন্তান আছে। বড়োগুলো তাদের বাবার কাছেই থাকে। ছোটোটা বৌটার সঙ্গে থাকে। হাজির নাকি তিনটে বিয়ে। একটা গজনীতে থাকে। একটা আমার বাড়ির ওখানে থাকে। তৃতীয়টা তো লিভ টুগেদার। কিন্তু ব্যবহারটা ভালোই বৌটার। রাতে তাড়াতাড়ি মাংসের কোরমা বানাল। রুটি শালো থেকে আসবে। কাবুল শহরে রুটি তৈরি কারো বাড়িতে হয় না। শালো বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে রুটি তৈরির মেসিন আছে। রুটি সেখানেই তৈরি হয়। আজ সবই কিছুই ভালো লাগছে। আমি প্রায় একটা গোটা রুটি খেয়ে নিয়েছি। কাবুল শহরের রুটি নান্ রুটির মতো। তিন কোনা লম্বা। কাবুলেও এখন আর বিদ্যুতের কোনো আলো নেই। যুদ্ধে সব নষ্ট হয়ে গেছে। শালাবাবু আমাকে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়েই চলে গেছে। আর আমার কোনও ভাবনা নেই। চিন্তা নেই। শুধুই সুন্দর। সুন্দর। আর নিশ্চয়তা। কেবল মনের কোনখানে একটা চাপা কান্না যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নেই। সম্পূর্ণ মুক্তি নেই এই অপরাজেয় কান্নার হাত থেকে। কান্নার কাছে হার মেনে যাই। ব্যক্তিত্ব হার মানে। উঁচু মাথাটা নিচু করে দেয়। আমার কঠিনতাকে ভেঙে চুরে দুমড়ে মুচড়ে তছনছ করে দেয় এই কান্না। কান্নার কাছে আমি বিধ্বস্ত, বিপন্ন। ছোট্ট শিশুর মতো কান্নার হাতে আমি নিজেকে সমর্পণ করি। এই কান্নাই আমার আনন্দকে মাটি করে দিল। সারাদিন, সারাক্ষণ, আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমার তিনি সোনা নেই। কোনখানেই আজ সে নেই। আর সে জ্বালাতন করবে না। আর সে বলবে না–মা, ব্যতা? মা, কানা? কান্না কে কানা বলত। আর কাউকে বলবে না-আমাল মাল দামা। আমাল মাল ততি। দাও। দাও। সে আর মা ছিলো তার জগৎ। কতবার তাকে মেরেছি। গাল দুটো লাল হয়ে গেছে। একবার গুলগুটির মেয়ের হাত থেকে রুটি কেড়ে নিয়ে খেয়েছিল বলে, গাল চেপে দিয়েছিলাম। পরে ও বহুবার বলেছে-মা এতানে ব্যতা। বলে গাল দেখিয়েছে। উঃ! কী ভয়ঙ্কর। কী নিষ্ঠুর আমি। একদিন আমি পাতকুয়ার সামনে বসে মাথায় মেহেন্দি লাগাচ্ছি। এমন সময় ও ঊর্ধ্বশ্বাসে আমার কাছে দৌড়ে আসছে। পিছনে গুলগুটি দেীড়ে আসছে।
-কী ব্যাপার কী? কী হয়েছে?
গুলগুটি ওকে বলছে দাঁড়া তোর মজা দেখাচ্ছি। মার পিছনে লুকালে কী হবে?
এবার গুলগুটি যা বলল তা শুনে আমি আর হাসি চাপতে পারিনি।
গুলগুটির ছোটো মেয়ে শবেরা। তিন্নির চেয়ে এক বছরের ছোটো। তাকে একলা ঘরে পেয়ে তিনি ঘেরাও করেছে। তারপর জেরা করছে –এই শবেলা তুই আমাল মাকে মা বলিচ কেনো? তালপল কালকে আমাল মাল কোলে উতিচিচ কেননা? জেরা করে যখন শবেরার থেকে কোনও উত্তর পায়নি তখন ধরে মেরেছে। গুলগুটি জানালায় দাঁড়িয়ে চুপিচুপি দেখছিল। তিনি এদিক ওদিক দেখছে কেউ দেখে ফেলল কিনা? গুলগুটিকে দেখতে পেয়ে নিরাপদ স্থানের আশায় দৌড় লাগিয়েছে। এই সব কথা অবশ্যই পুস্তুতে হয়। তার বাংলা করলে যা হয় তা এই রকমই দাঁড়ায়। আজ সে কোথায় পাবে নিরাপদ স্থান? কাকে মা বলে ডেকে কোলে বসে নিজের স্থানটাকে আগলে রাখবে? যদিও তার নিজের মা সাদগি। কিন্তু সে তো জন্ম থেকেই আমাকে তার মা বলে জেনে এসেছে। পাঁচ বছর পরে সে কি অন্য কাউকে নতুন করে মা বলে মেনে নেবে? ভয়ে মুখে কিছু না বললেও তার অন্তরের ভিতরটা? সেখানে কি ব্যথা লাগছে না? তিন্নি আজ নিঃস্ব, রিক্ত। তার ছোট্ট বুকের ভিতরটা মায়ের জন্যে হাহাকার করছে। যার খবর কেউ রাখে না। তিনি তার অন্তরে সর্বহারা। সর্বগ্রাসী কালাখান, সাদগি তার সবটুকু গ্রাস করেছে। আর আমি হচ্ছি তার অপদার্থ মা। এই সর্বগ্রাসী ভয়ঙ্কর মানুষটার হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারিনি। তিন্নি। তোর অসহায় মাকে তুই ক্ষমা করিস সোনা। তিন্নি আমি শুধুই তোর মা। তোর অধিকার থেকে তোকে কোনদিন বঞ্চিত করব না। আমি শুধুই তোর মা। মনে মনে কথাগুলো বলে বেশ শান্তি লাগছে।
ক্ষমা করব? কী করে ক্ষমা করব? আমার সমস্ত যন্ত্রণার মূলেই তো জাম্বাজ। যা কিছু সুখ আনন্দ তার? দুঃখ শুধুই আমার? অথচ, এই মানুষটার সঙ্গে সমঝোতা করে নিতে হবে। দুঃখ আমার সহ্য হবে কিন্তু বদনাম? না কিছুতেই তা সহ্য করতে পারবো না। সবাই আঙুল তুলে বলবে–দেখ। এক মুসলমানকে বিয়ে করে কিছুদিন জীবন কাটিয়ে, আবার তাকে ছেড়ে এখন রুমার মতো বাবার বাড়ি এসে উঠেছে। এ অপমান আমার কিছুতেই সহ্য হবে না। তা ছাড়া দ্রানাই চাচাকে যে কথা দিয়েছি। যে মানুষের কথার দাম নেই সে তো মানুষই নয়। কৃতজ্ঞতার হাতে বাঁধা পড়লাম। কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি স্বরূপ শুধু জাম্বাজকে ক্ষমা কেন? নিজের জীবনটাও উৎসর্গ করতে পারি। এত শান্তির মধ্যেও ঘুম আসছে না কেন? সকাল হলেই আবার পাসপোর্টের জন্য চেষ্টা করতে হবে। হাজি সাহেব বলেছে টাকা দিলে একদিনে পাসপোর্ট পাওয়া যাবে। যদিও এখন আর কোন লোক আমাকে দেশে যেতে বাধা দেবে না। তবুও তাড়াতাড়ি এ দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়াই শ্রেয়। বলা যায় না। হয়ত কোনও তালিবান ছদ্মবেশে এসে, গুলি চালিয়ে দিয়ে চলে গেল। এখন আমি এখনকার কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। তা বলে কি ভালো কেউ নেই? নাই যদি থাকবে, তবে দ্রানাই চাচা কেন এত সব করল? সবাই তো গার্ডেন অফ ভেনাসের সাইলক নয়? কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালার রহমত খানও বটে। তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হয়, গ্রামের সবাই আমাকে ভালো কতখানি বাসত জানি না। তবে মান্য সবাই করত। এখানে প্রচুর বাঙালি মেয়ে এসেছে। তাদেরকে কেউ পাত্তাই দেয় না। সম্মানও করে না। আমার ক্ষেত্রে ছিল আলাদা ব্যাপার। আমাকে রাস্তায় কেউ দেখলেই, ডেকে কুশল জানতে চাইতো। কারো বাড়িতে অনুষ্ঠান হলেই ডেকে নিয়ে যেত। পাড়ার মেয়েরা আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইতো। তবে আমি ছিলাম সতন্ত্র।
হাজিকে আমি এক লক্ষ আফগানি টাকা দিয়েছি। হাজি বলেছে এই টাকাতে পাসপোর্ট হয়ে যাবে। আমার হাতে কোনও কাজ নেই এখন। পাসপোর্ট এলে তবেই যাবো ভিসা অফিসে। তাই হাজির বিবিকে বললাম-এখানে বিউটি পার্লার আছে?সে বলল,-আছে, যাবে?
-চলো। একবার দেখি কেমন বিউটি পার্লার। তারপর জামা কাপড় পরে বেরিয়ে পড়লাম। ম্যাকরোবিয়ান থেকে একটা ট্যাক্সি ধরলাম। ট্যাক্সি আমাদের নিয়ে চলল। হাজির বিবি ড্রাইভারের সঙ্গে কি সব কথা বলছে ফার্সিতে। ড্রাইভার বলল–ফার্সি পমে? মানে ফার্সি জানে? বোধহয় আমার কথাই বলল। হাজির বৌয়ের নাম মামো।
ড্রাইভারকে মামো বলল,-এ্য, খারিজি। পরে জানলাম খারিজি কথার অর্থ বাইরের দেশের।
আমরা সাড়ানাও বলে একটা জায়গায় নামলাম। এই জায়গাটা কাবুল শহরের সব চাইতে পস্ এলাকা। যেমন আমাদের নিউ মার্কেট এলাকা। সাড়ানাওতে বেশ বড় বড় দোকান। আমাকে নিয়ে মামো একটা বেশ বড় বিউটি পার্লারে ঢুকল বলল–তুমি কী করাবে?
-ফেসিয়াল করবো।
হাজির বৌ আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে নিজে একজন কিম্ভুত মার্কা মেয়ের কাছে গিয়ে বসল। তার থেকে সিগারেট নিয়ে খেতে আরম্ভ করল। আমাকেও জিজ্ঞাসা করল আমি সিগারেট খাবো কিনা। আমি না বললাম। আমার মোটেও ভালো লাগছিল না পরিবেশটা। ফেসিয়ালটা শেষ হলে বাঁচি। ফেসিয়াল সেরে হাজির বৌকে বললাম কত দিতে হবে? মামো বলল-তিরিশ হাজার আফগানি। শুনে ভিমরি খাওয়ার জোগাড়। তবুও মুখে কিছু প্রকাশ না করে, টাকাটা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। এবার মামোকে বললাম-চলো ভালো কোন হোটেলে যাওয়া যাক। এই দিকটাতে যুদ্ধের রকেট বা মিসাইল নাকি পড়েনি। তাই এদিকটা এখনো অক্ষত। ট্যাক্সিতে করে যখন এদিকে আসছিলাম; তখনি দেখলাম শহরের প্রায় অর্ধেক বাড়ি ভেঙে পড়ে আছে। আর অনেক কোয়ার্টারের দেওয়াল সব ফুটো ফুটো হয়েছে গুলির আঘাতে। এত সুন্দর শহরটা একেবারে বিধ্বস্ত। দেখলেই বোঝা যায় এই কাবুল শহরের মাথার ওপর দিয়ে; কী ভাবে ঝড় বয়ে গেছে। মামো আমাকে বলল,-চলো ওই পর্দা দেওয়া হোটেলটা দেখছো? ওইখানেই যাই।
অগত্যা তাই। নাম তো জানি না। আমাদের দেশে পানভাজিওয়ালারা যেমন লোক ডাকে, হোটেলের কর্মচারীরা তেমনি লোক ডাকছে। আর কাঁচের বাক্সে করে হোটেলের সামনে অনেক লোক স্টল দিয়েছে। তাতে গাজর, মুলো বিক্রি করছে। ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে।
হোটেলের ভিতরে গিয়ে বসলাম। আমাদের সামনের টেবিলে একটা মেয়ে ও ছেলে বসে প্রেম করছে। এ দেশেও এই ভাবে বসে কেউ প্রেম করতে পারে তা আমার স্বপ্নেরও অতীত। আমাকে দেখে বা আমার কথা শুনে সবাই দেখতে লাগল। কাবুলে ফার্সি ভাষা চলে। যা আমি জানি না। নান্ ও কোরমা খাবারের অর্ডার দিলাম। সঙ্গে সালাড। খাওয়া শেষ করে ওখান থেকে বেরিয়ে একটা ছিট কাপড়ের দোকানে ঢুকলাম। একটা কাবুলি ড্রেস বানানোর শখ হলো। আসলে বাঁধা গরু ছাড়া পেয়েছি। পিছনে আর ফিরে তাকাবার সময় নেই। তাই খরচার ব্যাপারেও আমি শিথিল। যা হবার তা হবে। যখন হবে তখন দেখা যাবে।
আমরা বাজার থেকে কিছু মাংস, আলু, টমেটো কিনে বাড়ি চলে এলাম। ঘরে গিয়ে দেখলাম হাজি সাহেব বাড়িতে বসে আছে। আমাদের দেখে বললেন,
–সেই সকালে বেরিয়েছে তোমরা। আর এখন ফিরলে?
মামো বলল–কী করব। সাহেব কামালের বেড়ানো শেষ হতেই চায় না।
হাজি আমাকে বলল-তোমার পাসপোর্ট এনেছি। কাল তুমি ভিসা অফিসে গিয়ে ভিসার ব্যাবস্থাটা করতে পারো।
মনে রামধনুর রং লাগল। কাপের মতো নেচে উঠলো। কিন্তু বেশিক্ষণ এই আনন্দ উপভোগ করতে পারলাম না। কারণ হাজি তার বিবিকে বলল-লজ্জা করে না? বেহায়ার মতো বাজারে ঘুরে বেড়াতে? আমি তখন হাজিকে বললাম,-লজ্জা করার কি আছে? আমিও তো ছিলাম? ওকে বকা মানে তো আমাকেও আপনি অপমান করছেন।
-তা নয় ভাবি। আমাদের বাড়ির মেয়েরা রাস্তায় বেরোয় না। আপনারা তো রাস্তায় বেরোতে অভ্যস্ত।
শুনে মাথাটা গরম হয়ে উঠল। এতদিন পর সাহস পেয়েছি পাল্টা আঘাত করার। অনেক অত্যাচার অপমান সহ্য করেছি আর নয়। আর কত সহ্য করব? এরা শুধু বলেই যাবে? হাজি সাহেবকে বললাম।
–কেন? আপনাদের জাতের মেয়েদের এমন কী বৈশিষ্ট্য আছে? যা আমাদের নেই? কেন ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীত্বের অবমাননা করছেন? আপনারা যতখানি নিজেদের সবাইকার কাছে জাহির করেন, সত্যিই আপনারা কি তাই? মুসলিমরা নিজেরাই নিজেদের জাতের কলঙ্ক নয়? সব মুসলিম সম্পর্কে আমি জানি না। তবে কাবুলের মুসলিমদের মধ্যে যে ভ্রষ্টতা দেখে যাচ্ছি, তাতে মুসলিমদের প্রতি আমার আর সেই ধারণা রইলো না। মুসলিম মানেই একটা আতঙ্ক। ভয়, ত্রাস। অথচ একদা মুসলিমের অর্থ ছিলো ঐকতা। অন্তত আমি তাই শুনেছি।
-আপনাদের হিন্দু ধর্মের মধ্যে সবই কি ভালো? কিছুই কি খারাপ নেই? আপনাদের সনাতন ধর্মের ভ্ৰষ্টামি কি আমি কিছু জানি না মনে করেন? বর্ণ বৈষম্যের কী চমৎকার লীলা খেলা যে রাজনীতিবিদরা করে তা আমি সব জানি। হিন্দুরাই মুসলিমদের এক ঘরে করে রেখেছে। হিন্দুদের শিক্ষা আছে বলে যে গর্ব করে, সেটা প্রকৃত শিক্ষা নয়। শিক্ষার অপভ্রংশ। আর তাছাড়া আপানাদের হিন্দুস্থানে মানুষরা মুখেই বলছে যে হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই। কিন্তু বাস্তবে কি তাই মানছে?
মনে মনে ভাবলাম হাজি সাহেবের কথাটা ঠিক। কারণ আমি বাস্তবে তাই দেখেছি, প্রমাণ পেয়েছি। আমি জাম্বাজকে বিয়ে করে বাড়ি থেকে চলে এসেছিলাম, তখন একটা বাড়ি ভাড়া করতে গিয়ে সবার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। দালালরা তো মুখের ওপর বলেই দিল, ভালো পরিবেশে বাড়ি পাবেন না। কারণ মুসলিম বলে কেউ বাড়ি ভাড়া দিতে চাইছে না। যাদবপুরে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলাম, সেখানে পাড়ায় আমাকে নিয়ে সমালোচনা আরম্ভ হল। কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলত না। আমাদের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়াতো না। পাড়ার ক্লাবে মিটিং বসল মিটিংয়ের বিষয়বস্তু একজন ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে ফ্ল্যাট নিয়েছে। কিন্তু ওরা মুসলিম। ওদের পিটিয়ে শেষ করে দেওয়া হোক। মুসলিমকে বিয়ে করেছি বলে আমার পিতৃ পরিচয় তখন মিথ্যে হয়ে দাঁড়ালো। তারপর সেখান থেকে আমরা উঠে যেতে বাধ্য হলাম। আবার বাড়ি ভাড়া করলাম যাদবপুরেই দীপক ঘোষের বাড়ি। অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক ফ্যামিলি। তবুও তারা বাড়িওয়ালারা আমাদের ভাড়া দিয়েছে বলে বাড়ির আশেপাশের বাড়ি থেকে অবজেকশান্ করতে লাগল। কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলত না, উল্টে বলত আমাদের পাড়ার জল অপবিত্র হয়েছে মুসলিমের ছোঁয়ায়। আবার আমরা সেখান থেকে উঠে গিয়ে অন্য একটা বাড়ি ভাড়া নিলাম। সেটাও ওই যাদবপুরেই। আমার যেন জেদ চেপে গিয়েছিল। অন্য কোথাও যাবো না। এখানেই থাকবো। দেখবো মানুষ কত ঘৃণ্য হতে পারে। আমি অনেকক্ষণ কোনও কথা বলছি না বলে হাজি আমাকে বলল-কি এত ভাবছেন ভাবি? আমার কথা আপনাকে কি আঘাত করল?
-না-না। আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। যতই হোক একজন বাইরের লোকের কাছে; বিশেষ করে একজন মুসলিমের কাছে নিজের জাত-ধর্মের সম্পর্কে কোনও আলোচনা করতে আমার দ্বিধা হল। আবার সেই জাত-ধর্মের প্রশ্ন। এই প্রশ্নের বাইরে আমিও কি যেতে পারি না? নিজের মনেই প্রশ্ন করি। আসলে তা নয়। জন্ম থেকে বাড়ির বা পরিবেশের মানুষ মনে যা গেঁথে দিয়েছে, তা থেকে মুক্তি কারো নেই। চাইলেও পাওয়া যাবে না। জাতের বা ধর্মের একটা গন্ডির মধ্যেই চলাফেরা করতে হবে।
সংস্কার যদি করতেই হয়, তবে মাথাগুলোকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া উচিত। যারা মানুষের মধ্যে সৃষ্টির সৌন্দর্যে বার বার আঘাত হেনেছে মায়ের হাতে পায়ে শেকল দিয়ে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে, একদল এদিকে টানছে, ওদিকে যেও না ওরা মুসলিম, বিধর্মী। আর একদল টানছে ওদিকে, এদিকে যেও না ওরা হিন্দু কাফের। মাঝখানে দাঁড়িয়ে মা কপাল চাপড়াচ্ছে। এ কাকে সে জন্ম দিয়েছে? এই লজ্জার হাত থেকে কি মুক্তি নেই?
হোয়াট ইজ দা মিনিং অফ বিধর্মী অর কাফের? যার ধর্ম নেই সেই তো বিধর্মী? যে হিংস্র ও নাস্তিক সেই তো কাফের? মানে বুঝে দেখলে মনে হয় যে যারা এই পদবি দুটো ব্যবহার করে তারা মূর্খ। চরম মূর্খ।
হাজি বলল,–ভাবি, একটা কথার যথার্থ উত্তর আমাকে তুমি দিতে পারবে? কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার করতে হবে তোমাকে। কারো পক্ষ নিয়ে বলবে না।
হাজিকে কথা দিলাম নিরপেক্ষ ভাবেই উত্তর দেবো। তখন হাজি বলল,–আচ্ছা ভাবি, হিন্দুরা মাটির মূর্তি গড়ে পুজো করে, কেন?
–ঠাকুরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার জন্যেই।
-বেশ, তাই হলো। তো যাকে ভক্তি করে যাকে শ্রদ্ধা করে, তাকে আবার জলে ফেলে দেওয়া যায়? গাছের তলায় দাঁড় করিয়ে রাখা যায়? ওই মূর্তি, পুজোর আগে কত টাকা দিয়ে বানায়। তারপর কত শ্রদ্ধার সঙ্গে ঘরে নিয়ে রেখে, প্রচুর ফল মিষ্টি তার সামনে সাজিয়ে দিয়ে, অনেক মানুষ তাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে। তারপর সব শেষ। তাকে গাছের তলায় রেখে এল। এবার যত ঝড়, জল সেই মূর্তির ওপর। কাক, শকুনের বসার জায়গা তার মাথা। যে মূর্তির কপালে একদিন ফল, মিষ্টি ও প্রণাম জুটেছিল, তারপর দিনই চরম অবহেলিত। এই প্রহসনের কি কোনও প্রয়োজন ছিল? এর থেকে ওই ফল মিষ্টিগুলো কি তাদের দেওয়া উচিত ছিল না? যাদের সামর্থ্য নেই ওসব খাওয়ার?
-দেখুন হাজি সাহেব, আমি সামান্য নারী। অতি সামান্য আমার জ্ঞান। সুতরাং আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যের মধ্যে নেই। এত আধ্যাত্মিক চিন্তার শক্তি আমার নেই। শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে ঈশ্বর কখনোই বলেননি যে মাটির মূর্তির মধ্যে দিয়ে আমাকে পাবে। তিনি বলেছেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আমি আছি। যারা বর্ণশ্রেষ্ঠ আমি তাদের শুধু নয়। যারা অচ্ছুত, তারাও আমার। অচ্ছত বলে তাদের ঘৃণা করিও না। বিবেকানন্দ বলেছেন, মহাত্মা গান্ধী বলেছেন অস্পৃশ্যতা আমাদের জীবনের একটা অভিশাপ। সুতরাং অস্পৃশ্যতাকে পরাজিত করতে হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষরা হচ্ছে জ্ঞানের জ্ঞানী। তাই তাদের কথা মানা প্রয়োজন বলে মনে করে না। আরও এইটুকুই বলতে পারি যে, চিত্তের একাগ্রতা ঠিক একটি স্থানে নিবদ্ধ রাখার জন্যেই এই মূর্তির প্রহসন করে। যা আপনারাও করেন। এবং একটা ঘড়ি যেমন সবাইকে সময়ের গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখে! ধর্মও ঠিক তাই। ঘড়ির কাজ ও ধর্মের কাজ একই।
-আমরা কোনও মূর্তির ওপর নজর রেখে নামাজ পড়ি না।
-মূর্তির ওপর না হলেও একটা দিক্ নির্দিষ্ট করে তবেই তো নামাজ পড়েন?
-তার জন্যে প্রচুর অর্থের নষ্টামি করি না।
-করেন, করেন হাজিসাহেব। আপনারা হজ উপলক্ষে মক্কায় যান। এতে অর্থের অপচয় হয় না? এই অপচয় না করে মানুষকে শ্রদ্ধা করুন। জাত, ধর্মের অশচিতা থেকে বাইরে এসে জীবনমুখী হয়ে সবার হাতে হাত মেলান সেটাই তো হজ হয়ে যাবে। আল্লা কি শুধু মক্কাতেই বসে আছেন? ওইটুকুই কি তার গতিবিধি? তিনি সমগ্র বিশ্বের অধীশ্বর হলেন কী করে? আল্লা, ভগবান প্রতিটি মানুষের অন্তরে আছে। তার আলাদা কোনও স্থান নেই।
-তা কেন? ওখানে মহম্মদ রসুলের কবর আছে। কথিত আছে যে মক্কার ওই পাথর যখন গাঁথা যাচ্ছিল না, যতবার পাথর গেঁথেছে ততবার ভেঙে পড়েছে। তখন আল্লার বাণী হল ইব্রাহিমের নিজের ছেলেকে যদি বলি দেয়; তবেই মসজিদ নিজের জায়গায় দাঁড়াবে বা মসজিদ বানানো সফল হবে। তারপর ইব্রাহিম খলিফা তাঁর ছেলেকে যখন বলি দিতে গেলেন তখন নিজের চোখ বন্ধ করে বলি দিলেন। চোখ মেলে দেখলেন সেখানে খাসি বলি হয়েছে। তার ছেলে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরই মসজিদ আর ভেঙ্গে পড়েনি তৈরি হল মক্কা সেই থেকে ওই মক্কা শরীফ প্রতিটি মুসলমানের কাছে পবিত্র স্থান হয়ে উঠেছে।
-হিন্দুদের মধ্যেও সেইরকম অনেক কথা কথিত আছে। এই সব তর্কের কি শেষ আছে? তর্ক যেমন আছে তেমনি সমাধাও আছে। সুতরাং তর্ক থামিয়ে আসুন রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়া যাক।
আমরা যখন এই সব তর্কে বিভোর হয়ে আছি, সেই সময় হাজির বিবি রান্না করে নিয়েছে। মামো মেয়েটা খারাপ নয়। তবুও আমার যেন তাকে ভালো লাগে। আবার বলি। যা খারাপ তা চিরদিনই খারাপ। খারাপের কোনও বিকল্প হয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পড়ে সমাজের কটাক্ষকে পদদলিত সমাজের মাথাকে নস্যাৎ করার জন্যে। খারাপ হয়ে যাওয়া মোটেও খারাপ নয়। কিন্তু নিজের কিছু ভালো লাগাকে চরিতার্থ করার জন্য যারা নিজেদের অন্যের হাতে বিলিয়ে দেয় তারা কি ভালোর পর্যায়ে পড়ে? জাহানারা কি ভালো কাজ করেছিল? সেই দিনের সেই মুহূর্ত আজ আমার চোখের সামনে জাজ্বল্যমান। সেদিন গফর চাচার বিয়ে ছিল। বড় বড় তিন ছেলে রেখে গফর চাচার বিবি মারা গেল। গফর চাচার বয়স নাকি অল্প। তাই বাড়ির সবাই ব্যস্ত হল, গফরচাচার বিয়ের জন্যে। যে সময় ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ আনার কথা, সেই সময়ে নিজে বিয়ে করে বৌ আনতে চললেন গফরচাচা। আমার বাড়ির সবাই বিয়েতে গিয়েছে। তখন নতুন। সবে চারমাস হয়েছে আমি বৌ হয়ে এ বাড়িতে এসেছি। বিয়েতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।
দুপুর একটা। আমার জ্যাঠতুতো জা জাহানারা। আমার সঙ্গে শুয়েছিল। হঠাৎ সে উঠে আমাকে একটা সাবান দেখিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কী সব বলল। যেন অনেক কিছু আমি বুঝলাম। বললাম-হ্যাঁ, হা। তারপর জাহানারা ঘর থেকে চলে গেল। মোটামুটি বুঝলাম যে ও জামাকাপড় কাঁচাকাচি করতে যাচ্ছে। একটা খাতা নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আমি দৈনন্দিনের কথা লিপিবদ্ধ করতে ব্যস্ত। এইভাবে বেশ খানিকটা সময় অতিবাহিত হলো। ঘড়ির কাঁটা তখন একটা চল্লিশের ঘরে। লিখতে লিখতে হঠাৎ কী মনে হতে মুখ তুলে পাতকুয়ার দিকে তাকালাম। কিন্তু সেখানে কাউকেই দেখতে পেলাম না। ভাবলাম, জাহানারা তো বলল কাঁচাকাচি করতে যাচ্ছে। সাবান ও জামা-কাপড় হাতে করে পাতকুয়া দেখাবার অন্তত এই অর্থ দাঁড়ায়। কিন্তু কই? জাহানারা তো ওখানে নেই? তবে কোথায় গেল? ও কোথায় গেল দেখার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। হয়তো সন্দেহের কোনও অবকাশই থাকত না, যদি না আমি কয়েক দিন আগে শুনতাম, যে জাহানারা পিজলা খানকে বলছে সানাজ। সানাজ কথাটার অর্থ প্রিয়, প্রিয়া, পেয়ারা। আর এই কথাটা একমাত্র এখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই ব্যবহার হয়। জাম্বাজ আমাকে সেইরকমই বলেছে। সেই কারণেই একটা অহেতুক সন্দেহ হয়েছে আমার। আমি জাম্বাজকে কথাটা বলে প্রশ্ন করেছিলাম পিজলামিন ছেলেটার পরিচয় কী? জাম্বাজ বলেছিল–আসাম চাচার দূর সম্পর্কের শালা। কেউ কোথাও নেই। তাই মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়িতে এসে থাকে। খুব ভালো ছেলে। তোমার সন্দেহ অমূলক। তবুও একটা সন্দেহের বীজ আমার মাথা থেকে যায় না। একটা বাইরের লোককে ঘরের বৌ কি করে সানাজ বলতে পারে? বিশেষ করে যারা মুসলিম? এবং অর্থডক্স মাইন্ডের তাদের ক্ষেত্রে প্রশ্নই ওঠে না। এই কারণেই মনটা কেমন যেন বিচলিত হল। যদিও আমার কিছুই এসে যায় না জাহানারা কি করল আর না করল। তবুও ভাবলাম যাই দেখি। একটা মন যেতে চাইছে না। অন্য মন বলছে চলোই না জাহানারা কোথায় দেখা যাক। ঘর থেকে এসে বারান্দায় পা রাখলাম। পুরো বাড়ি নিশ্চুপ। দুপুর বেলার গরমে বাইরে কেউ থাকে না। যে গরম আমরা জানি সেই রকম গরম এখানকার মানুষ; কিছু লোক ছাড়া চিন্তাই করতে পারে না। আমাদের দেশে ডিসেম্বরের দুপুরে যেমন থাকে? এখানে সেটাকে গরম বলে। যাই হোক, কোথায় গেলে জাহানারাকে পাবো বুঝতে পারছি না। আমার পাশের ঘরটাই জাহানারার ঘর। দেখলাম দরজা বন্ধ। বন্ধ দরজায় একটা আঙুল দিয়ে ঠেলা দিলাম। ভেতর থেকে বন্ধ। এই সময় ভিতর থেকে দরজা বন্ধ হওয়ার কথা নয়। যদিও দরজা বন্ধ বা খোলা রাখা কথা অনুযায়ী হয় না। তবুও সাধারণত এই সময়ে কেউ এখানে ভিতর থেকে খিল দেয় না। রাতেই খিল দেয় না তো দিনে। বিশাল পাঁচিল দেওয়া চতুর্দিক। মাঝখানে সব ঘর। তাই প্রয়োজন হয় না খিল দেওয়ার। তবে কেন বন্ধ? কেন খিল দেওয়া? চড়াত করে একটা অশুভ চিন্তা মাথায় এসে ভিড় করল। তবে কি….? আস্তে আস্তে পা ফেলে দরজা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম। একটা অনেক চওড়া ও অনেক লম্বা জানালা এখানে আছে। কিন্তু মাটি দিয়ে দেওয়াল গেঁথে দিয়েছে। কারণ যুদ্ধের গুলি এসে ঘরে যেন কারো গায়ে না লাগে। ওপর দিকে মাত্র হাফ মিটার ফাঁকা রেখেছে। সেখানে পর্দা দেওয়া আছে দেখলাম। পর্দা দিয়ে রাখা মোটেও স্বাভাবিক নয়। এবার আমি আচমকা পা উঁচু করে পর্দাটা সরিয়েই মুখ ঢুকিয়ে দিলাম। কিন্তু একি? এ আমি কী দেখছি? কারেন্ট খেলে মানুষ যেমন হয়, কারেন্টের স্পর্শে সবার শরীরের ভিতরটা যেমন করে ওঠে, আমার ঠিক তেমনি হল। জাহানারা ও পিজলামিন। জাহানারা পুরো উলঙ্গ। আর পিজলামিনের শরীরে একটা গেঞ্জি আছে মাত্র। আমার কথা বলার শক্তি নেই। নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে করতে লাগলাম। কী করবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। জানালা থেকে মুখ সরিয়ে নিচে বসে দুই হাতে মুখ লুকিয়ে চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে লাগলাম। ডাক নয় কেমন যেন একটা গোঙানির মত ডাক আমার গলা দিয়ে বেরোচ্ছে। আমার এই অস্বাভাবিক আওয়াজে আবু, আদ্রামানের বৌ বাইরে বেরিয়ে এল। তারা আমাকে ওই ভাবে বসে গোঙাতে দেখে কাছে এল। কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করল। ততক্ষণে জাহানারা জামা পরে নিয়েছে। পিজলামিনও জামা-প্যান্ট পরে নিয়েছে। আমি ওদের দুজনকে দেখিয়ে হাত নেড়ে জামা ধরে যা বললাম তা আবু বুঝে ফেলল। আবু খুব বুদ্ধিমতী। ব্যাপারটা বুঝে জাহানারার চুলের মুঠি ধরে উঠোনের মাঝে নিয়ে গিয়ে কিল চড় মারতে লাগল। এই সময় পিজলামিন আমার থেকে একটু দূরে এসে দাঁড়াল। আমার দিকে তার কটাক্ষ দৃষ্টি। এবার আবু পিজলামিনকে আক্রমণ করল। সে এক বীভৎস দৃশ্য। ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছি। ঠিক ভয়ে নয়, ঘেন্না ও রাগে সমস্ত শরীরে কাঁপুনি ধরেছে জাহানারা কামনা লালসা চরিতার্থ করেছে বলে ঘেন্না নয়। কারণ কামনা সবার মধ্যেই থাকতে পারে। আর তা মেটাবার স্বাধীনতা সবার আছে। খিদে পেলে তখন কেউই ভেবে দেখে না খাদ্যটা শুদ্ধ কী অশুদ্ধ। বাসী না টাটকা। খিদের সময় খাদ্যটা আসল নয়। খাওয়াটাই উদ্দেশ্য। এবং সেই খিদে মেটাবার জন্যে কারা ওপর ঘেন্না হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। প্রশ্ন একটাই, এরা কেন সবার কাছে নিজেদের সাতী বলে জাহির করে? কেন বলে, আমাদের রীর অন্য পুরুষ যাতে দেখতে না পায় তাই বোরখা পরি? এই কি মুসলিম জাতের বোরখা? এবং লজ্জা নিবারণ? আমার ঘেন্না এই ভণ্ডামির ওপর। হাঁড়ির সব ভাত টিপে দেখার প্রয়োজন পড়ে না। একটাই যথেষ্ট। কিন্তু একটা নয় আমি একাধিক দেখলাম।
জাহানারার কিন্তু কোন তাপ, উত্তাপ নেই। সে তার ঘরে চলে গেল। একটু পরে সবাই দেখল সে হাত মুখ ধুয়ে রুটি আর মাখন তোলা জল নিয়ে খেতে বসল। যেন কিছুই হয়নি। তারপর রাতে যখন সবাই বাড়িতে ফিরল, জাহানারার স্বামীও ফিরল। তখন সবার সামনে কোরান শরীফের ওপর হাত রেখে জাহানারা কসম খেল যে, সে এমন কাজ করেনি। সাহেব-কামাল মিথ্যে বলছে। চমৎকার! মিথ্যে? সাহেব কামাল মিথ্যে বলেছে? স্বামীর কাছে সমস্ত সুখ পাওয়ার পরেও এমন ঘৃণ্যতম কাজ যদি আমি করতাম, আর তা কেউ দেখে ফেলত, তবে কসম খাওয়া পর্যন্ত নিশ্চয়ই এগুতাম না। সঙ্গে সঙ্গে গলায় দড়ি। কিন্তু জাহানারা? দিব্যি ঘুরে বেড়ায়। স্বামীর পাশে বসে গল্প করে, হাসে, স্বামীর প্রতি ভালবাসা দেখায়। ঝগড়া করে। আমার সামনেও বসে কথা বলে, আমার চোখের ওপর সেও চোখ মেলায়। নির্লজ্জেরও তো একটা সীমা-পরিসীমা আছে? আর একজন এই রকম নোংরা মহিলাকে দেখলাম। সে হচ্ছে সবাই চাচার বিবি ময়না। সবাই তখন হিন্দুস্থানে। হঠাৎ পাড়াময় রটে গেল যে ময়না অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু কী করে সম্ভব? সবাই আজ তিন বছর হলো কলকাতায় আছে। তার বিবির বাচ্চা হবে? খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সওবাইয়ের বড় ভাই ময়নাকে ধরে মারধোর শুরু করল। কিন্তু ময়না কিছুতেই কারো নাম বলতে চাইলো না। কুন্তীর যুগ তো আর নেই যে সূর্যের বরে সন্তান হবে। একজন উপলক্ষ তো চাই। সন্তানের জন্মদাতা হবে। কে সেই লোক? প্রতিটি মানুষ যখন এই চিন্তায় বিভোর তখন ময়না বজ্রপাতের মতোই ঘোষণা করল যে আমার এই সন্তানের পিতা হচ্ছে ইব্রাহিম আকা। ধরিত্রীর মাটি কেঁপে উঠল। আকাশ যেন আকাশের থেকে অনেক নিচে নেমে এল। সমুদ্রের জল ফুলে উঠে প্রচণ্ড শব্দে পাড়ে এসে আছাড় খেল। একটা ঘূর্ণি ঝড় বেগে ধেয়ে এসে আমার মন, হৃদয় ভেঙে চুড়মার করে দিল।
ইব্রাহিম আকা? সে তো……? উচ্চারণ করতেও আমার বুকের ভিতরটা বেঁকে কেমন যেন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। একটা বমির মতো কী যেন পেটের ভিতর থেকে ঠেলে উঠে আসছে গলা পর্যন্ত। এত নোংরা? এত ঘৃণ্য? এমন জঘন্যতম রিপুর তাড়না? আর এরাই নাকি গোঁড়া? এতো দেখছি গোঁড়ামির চরম পর্যায় বিচরণ করছে? যতই হোক ময়নাকে বেশি ঘেন্না হতে লাগলো। ময়নাই বা কী করে পারলো এমন একটা নোংরা প্রস্তাবের সঙ্গে হাত মেলাতে? লজ্জা করল না? ইব্রাহিম ছাড়া কি আর কেউ ছিল না? নিজের স্বামীর কথাটা একবারো ভাবলো না? কী মুখ দেখাবে সে তার অতি আপন মানুষটার কাছে? কী করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? একমাত্র স্বামী ছাড়া যা কারো নয়। কাউকে দেবার নয়। সেই গোপনীয়তা কেমন করে ময়না অন্য আর একজনের হাতে সমর্পণ করলো? এইটুকু চরিত্রের দৃঢ়তা নেই ময়নার মধ্যে। বয়স তো কম নয়? আর শেষে কিনা–ইব্রাহিম? পারলো? ময়না আত্মহত্যা করতে পারলো না? বসুমতী দুভাগ হলো না?
সওবাই হচ্ছে ইব্রাহিমের মেজো ছেলে। ময়নার নিজের একেবারে নিজের শ্বশুর। শেষ পর্যন্ত শ্বশুড়ের সঙ্গে ময়না কলঙ্কিত হল? কলঙ্কের এও একটা দিক। আমার কাছে ছিল একেবারে অজানা। অচেনা। এমন নিকৃষ্টতম কলঙ্কের নাম এর আগে কখনো শুনিনি। এই সব শুনে দেখে আমি যেন কেমন হয়ে যেতে লাগলাম। এ তো পাওয়া নয়, এ যে বিকৃত পাওয়া। যা আমার অন্তত কাম্য নয়। আমার কেন শুধু, কোনও, সুস্থ, ভদ্র, মার্জিত রুচির মানুষই এসব পথ ধরে এগোয় না। পরে অনেক ভেবে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, এইখানকার মেয়েরা বিয়ের পরে যখন রক্তের উন্মাদনার স্বাদ পায়, জীবনকে চিনতে শেখে, স্বামীর উষ্ণতার মধ্যে নিজের আনন্দকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করে তার আস্বাদন সমস্ত মনে প্রাণে, শরীরে নিয়ে বসে থাকে। ঠিক সেই সময় স্বামী তাকে একা ফেলে রেখে বিদেশে পাড়ি দেয়। তারপর বছরের পর বছর সেই বিবিকে অপেক্ষা করে থাকতে হয়, কবে তার স্বামী ফিরে এসে আরার তাকে পরিপূর্ণ সুখের মুহূর্ত ফিরিয়ে দেবে? কিন্তু স্বামীরা তো পাঁচ-ছয় সাত বছরের আগে ফিরে আসার নয়। তখন হয়তো কেউ তার ইচ্ছাকে দমন করতে পারে, কেউ পারে না। আর এই পারে না-র দলে ময়না-জাহানারা। আরো এরকম অনেক আছে যাদের খবর আমি জানি না। আর জানতে চাইও না। জানলে কষ্ট বাড়ে। ঘৃণা হয়। লজ্জা করে।
ভোর পাঁচটা বাজে। হাজি নামাজ পড়ছে! মামো নামাজ পড়ে না। পড়ে কিনা জানি না। আমি দেখিনি। আমি উঠে বাথরুমের দিকে গেলাম। একেবারে স্নানটাও সেরে নেবো। এমব্যাসিতে যেতে হবে। মামোই নিয়ে যাবে আমাকে। এখনো মনের মধ্যে একটা চিন্তা আছে। যদি এমব্যাসির লোকটা বুঝতে পারে যে পাসপোর্টে যা লেখা আছে তা মিথ্যে। আমি আফগানিস্তানের মেয়ে নই। আমাকে দেখলে কি বুঝতে পারবে? কি জানি। তবুও মনের ওপর জোর রেখে মামোকে নিয়ে গেলাম এমব্যাসিতে। ইন্ডিয়ার এমব্যাসি। আবার মনের মধ্যে সেই আনন্দ। নিজের দেশের কিছু বিদেশে দেখলে কার না আনন্দ হয়?
একটা ছেলেদের ও একটা মেয়েদের লাইন আছে। মেয়েদের লাইনে আমি সর্ব প্রথম। আমার পরে মাত্র দুজনের অস্তিত্ব আছে। অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পরে একটা দরজা খুলে ভিতরে ঢোকালো সবাইকার পাসপোর্ট দেখে। ভিতরেও খানিকক্ষণ বসলাম। একটা চঞ্চলতা মনের মধ্যে আছে অফিসারের ঘরে একজন করে যাচ্ছে। এবার ডাক পড়ল আমার। শবনম খান। মুহূর্তের জন্যে আমি ভুলে গিয়েছিলাম আমিই শবনম খান। আচমকা মনে পড়তেই উঠে দাঁড়ালাম। তারপর ভিতরে অফিসারের ঘরে আমাকে নিয়ে গেল। পাঞ্জাবি অফিসার। দরজায় নেম প্লেটে লেখা আছে অবতার সিং। আমি ভিতরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবতার সিং বললেন-বলুন ম্যাডাম, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি? কথাগুলো তিনি ইংরিজিতেই বললেন। আমিও তাকে ইংরেজিতেই উত্তর দিলাম। ভুলেই গিয়েছি আমি আফগান মেয়ের পরিচয় দিয়েছি, আমি তাকে একটা ভিসা দিতে বললাম। হিন্দুস্থানে যাওয়ার জন্যে।
তিনি বললেন-আপ-ডাউন টিকিট নিয়ে আসুন, তবেই ভিসা পাবেন।
-স্যার- সে তো অনেক টাকার ব্যাপার? আমার কাছে তো অত টাকা নেই।
-আমি কী করতে পারি বলুন? আমাদের নিয়ম এটাই। আর হ্যাঁ আপনি কি আফগানিস্তানের মেয়ে? উনি সোজা প্রশ্ন করলেন।
-হ্যাঁ।
-আপনার কথা শুনে বা আপনাকে দেখে তাতে মনে হচ্ছে না?
-আমি জন্মের পর থেকেই ইন্ডিয়াতে ছিলাম। তাই আপনার এমন মনে হচ্ছে। কথাটা বলেই কেমন বিচলিত হয়ে পড়লাম। এ কি বলে ফেললাম? আফগানের মেয়েরা তো ইন্ডিয়াতে থাকে না? সর্বনাশ। সঙ্গে সঙ্গে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম,–আমার বাবা পাঠান। মা ইন্ডিয়ান বাঙালি। আমার মামার বাড়ি কলকাতায়। সেই সূত্রে ইণ্ডিয়াতে থাকার সুযোগ পেয়েছি।
-কবে এসেছেন, এদেশে?
-বারো বছর হবে।
-সেই সময়কার পাসপোর্ট বা ভিসা দিন।
আর পাবো না ভিসা। আমি যেন কেঁদে ফেলব এখুনি। তবু মনের জোর এনে বললাম-স্যার। আজ কত বছর ধরে এদেশে যুদ্ধ হচ্ছে আপনি তো জানেন। কোথায় কার বাড়ি ঘর তার ঠিক নেই; আর আপনি পাসপোর্ট ভিসা চাইছেন? সত্যিই অবাক করলেন। উনি আমার দিকে দেখে একটু হাসলেন তারপর বললেন,
– যাক এসব কথা। আমি সবই বুঝতে পারছি। আপনি সময় নষ্ট না করে টিকিট কেটে আনুন। ভিসা নিয়ে যান।
-কিন্তু স্যার। আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন-যাওয়ার টিকিটটা তো আনবেন নাকি তাও আনবেন না? বলে তিনি হাসতে লাগলেন।
অফিসারের ঘর থেকে বাইরে এসে মামোকে নিয়ে দৌড়লাম টিকিট নিতে। কিন্তু এখানেও সমস্যা দেখা দিল। পাসপোর্ট না হলে টিকিট দেবে না। আবার দৌড়ালাম ট্যাক্সি নিয়ে ভিসা অফিসে। সেখানের লোক পাসপোর্ট দিলো না। একটা নাম্বার লিখে দিলো। সেই নাম্বার নিয়ে আবার এলাম টিকিট অফিসে। আবার এখানে বলল পাসপোর্ট চাই নাম্বারে হবে না। আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেলো। পুস্তুতে একটা লোককে আমি বললাম,-একবার আপনারা পাঠাচ্ছেন পাসপোর্ট আনতে। পাসপোর্ট আনলে তবেই টিকিট দেবেন। আর এমব্যাসি পাঠাচ্ছে টিকিট আনতে। টিকিট আনলে তবেই পাসপোর্ট ও ভিসা দেবে। আপনিই বলুন তো আমি কী করি?
হঠাৎ ওদেরই মধ্যে একজন রোগা লম্বা লোক বলল-কী হয়েছে? আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন?
লোকটাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বললাম। তিনি সব শুনে আমাকে বললেন–আপনি কোথা থেকে আসছেন?
-আমি সারানা থেকে আসছি। ওখানে আমার বাড়ি।
লোকটা তখন একজনকে বলল–আরে টিকিট দিয়ে দাও। ইনি আমার গাঁয়ের মেয়ে।
এবার টিকিট পেলাম। টিকিট নিয়ে আবার দৌড়ে গেলাম ভিসা নিতে। এমব্যাসি তখন বন্ধ হবে। একটা ঘরে বসে সবাই চা খাচ্ছে। দ্বিতীয় গেটের ছোট্ট একটা জানালা দিয়ে একজনকে ডাকলাম। তিনি হিন্দুস্থানি। তাকে ভিসার কথা বলতে তিনি বললেন অ্যামব্যাসি তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তখন আমি তাকে অনুরোধ করলাম একবার দরজাটা খোলার জন্যে। কী জানি লোকটার বোধহয় দয়া হলো আমার প্রতি। দরজা খুলে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। তাকে আমি বললাম-প্লিজ। স্যারকে বলুন আমার ভিসাটা আজই দিতে। এই দেখুন কালকের টিকিট এনেছি। নইলে টিকিটটা আবার ফেরত দিতে হবে। আমি ভীষণ হাঁপিয়ে উঠেছি এই দৌড়োদৌড়িতে। আর পারছি না। লোকটা একটু বসতে বলে, আমার কাছ থেকে টিকিটটা নিয়ে চলে গেলো। প্রায় কুড়ি মিনিট পর এলো। পাসপোর্ট ভিসা, টিকিট আমার হাতে দিয়ে বলল,–ম্যাডাম। আমি জানি, আপনি ইন্ডিয়ান। আপনার চেহারা, কথা, সব কিছুই বাঙালির মতো। তাই আপনাকে কষ্ট না দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে স্যারকে বলে করে নিয়ে এলাম ভিসা। স্যারও বুঝতে পেরেছেন সব। তাই দিয়ে দিলেন। অন্তত একজন মেয়ে নিজের দেশে ফিরে যাক।
আমি লোকটাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে এলাম।
আজ আট তারিখ। সকাল নটায় আমি সমস্ত কিছুর অবসান ঘটিয়ে সব কিছু পিছনে ফেলে, সবাইকে উপেক্ষা করে, তালিবানদের গোঁড়ামি, চূড়ান্ত শরীয়তি, মৌলবাদীর ভাঁড়ামি, এবং কোরানের দোহাই দিয়ে সাধারণ জনগণের ওপর অত্যাচার–সমস্ত কিছু পদদলিত করে এয়ারপোর্টে গিয়ে পৌঁছালাম। চেকিং শেষ করে ময়দান। একবার পিছন ফিরে দেখলাম। কাবুল। পশ্চিম এশিয়া। কাবুল। কাবুল দেশটা কি সত্যিই খারাপ ছিল? আজ শেষ বিদায়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এই কথাটাই আমার মনে বার বার প্রশ্নের ঢেউ তুলে যাচ্ছে। দেশটার মধ্যে কি সবই খারাপ? স্বৈরতন্ত্র, নাকি মানুষের নষ্টামি দেশটাকে খারাপ করে দিল? এত সুন্দর হাওয়া, ভালো জল, ভালো খাদ্য, সবই তো ভালো। তবে কেন বিকৃত রুচির এবং অনুদার মানসিকতার হল। কেন এমন মানুষ এখানে বাস করার অধিকার পেল যারা দেশের বৈশিষ্ট্য একের পর এক নষ্ট করে দিচ্ছে? সেলফিস জায়েন্টের দৈত্যর হিংস্রতাই এদের আছে, উদারতা নেই অথচ কেউ কোনও প্রতিকার করতে পারছে না। পারবে কী করে? কে বা কারা যে এই তালিবানকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করছে তা এখনো পর্দার পেছনে। তবে সাহায্য কেউ করছে সে বিষয়ে নিশ্চিত। কারো মদত না পেলে আধুনিক সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারত না। কিন্তু যারা তালিবানদের সাহায্য করছে তাদের অবগত থাকা উচিত, বাঘ একবার যদি মাংসের স্বাদ পায় তবে মাংস ছাড়া কিছুই সে খায় না। সে মাংস মানুষের হোক আর জানোয়ারের হোক। সবাই এগিয়ে চলেছে প্লেনের দিকে। তাদের সঙ্গে আমিও এগিয়ে যেতে লাগলাম। প্লেনে ওঠার সিঁড়ির কাছে দুজন সিকিউরিটি গার্ড দাঁড়িয়ে। সবার পাসপোর্ট ও ভিসা দেখে তবেই উপরে উঠতে দিচ্ছে। আমিও পাসপোর্ট ও ভিসা দেখালাম। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি। অন্য কোনও বিপর্যয় না হলে আমি ঠিক ইন্ডিয়াতে পৌঁছাবো। আর আমাকে কোনও শক্তিই রুখতে পারবে না। তালিবানরা এখনও এখানে এসে পৌঁছায়নি। এখানে রাব্বানি সরকারের হুকুম চলছে। প্লেনের ভিতরে গিয়ে একটা জানালার ধার দেখে বসলাম। এরিয়ানা আফগান প্লেনে সিট নাম্বার দেয় না। যে যেখানে জায়গা পায় গিয়ে বসে পড়ে।
প্লেন প্রথমে জালালাবাদে যাবে। সেখানে এক ঘণ্টা দাঁড়াবে। তারপর যাবে দিল্লি। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্লেন স্টার্ট দিল। আর তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই আমি পৌঁছে যাবো আমার দেশে। এত সময় লাগে না। কিন্তু জালালাবাদ হয়ে প্লেন যাবে বলেই এত সময় লাগবে। এমনিতে মাত্র এক ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে। কাবুল শহরের বিশেষ কিছুই দেখতে পারিনি, সময় পাইনি। তার মধ্যেই মামো, মাসুদ আহমেদ শাহর কার্যালয়ে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। সমস্ত কমান্ডোরা সেখানে আছে। সেখানে একজন হেলথ ডিপার্টমেন্টের, হেড অব দা ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। যখন শুনলেন আমি গ্রামে ডাক্তারি করতাম তখন তিনি বললেন– আপনি যাবেন না। কাবুল শহরে থাকুন। আপনার মতো একজনকে আমাদের দরকার।
-আপনি কি জানেন আমি কত কাঠখড় পুড়িয়ে সব তালিবানের শরীয়তি শাসনকে, চোখ রাঙানিকে প্রত্যাখান করে তবেই আজ এখানে এসে পৌঁছেছি। আমি এখানে আর থাকতে চাই না। নিজের দেশেই ফিরে যেতে চাই।
তিনি আর আমাকে থাকার জন্যে অনুরোধ করেন নি। কিন্তু তিনি আরো যা বললেন শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তিনি বলেছিলেন,–জানেন, এখানে স্পেশালিস্ট বলে কেউ নেই। একজন গাইনোকোলজিস্ট নেই। আসলে ভালো ডাক্তারই নেই।
একটা মৃদু ঝটকা। প্লেন জালালাবাদে ল্যান্ড করল। প্লেন থেকে হিন্দুস্থানে যাওয়ার কেউ নামতে পারবে না। যারা কেবল এখানকার জন্যে এসেছে তারা নেমে যেতে লাগল। কাবুল ছাড়ার পর মনটা এবার ইন্ডিয়াতে চলে গেল। দিল্লিতে নেমে আমি কোথায় গিয়ে থাকবো? আমার এক বান্ধবির বাড়ি আছে সফদজং ইনক্লাব রোডে। সেখানেই যাবো বলে ঠিক করলাম। জালালাবাদের লোক প্লেন থেকে নেমে যাওয়ার পর এয়ারহোস্টেসরা সবাই যাত্রীদের লাঞ্চ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সময় আর কাটছে না। প্রায় দুঘণ্টা পরে আবার প্লেন স্পিড় নিয়ে সামনের মুখটা আকাশের দিকে তুলল।
বিদায়। আমার জীবনের অনেকটা সময় যে দেশে অতিবাহিত করলাম। যাদের সুখে, দুঃখে অঙ্গাঙ্গিভাবে ভাগিদার ছিলাম, সেই পশ্চিম এশিয়ার একটা চরম মৌলবাদীর দেশকে আমি বিদায় সম্ভাষণ জানালাম।
বিদায় কাবুল। বিদায় পশ্চিম এশিয়া আফগানিস্তান।
সালাম–তোমায়–সালাম।